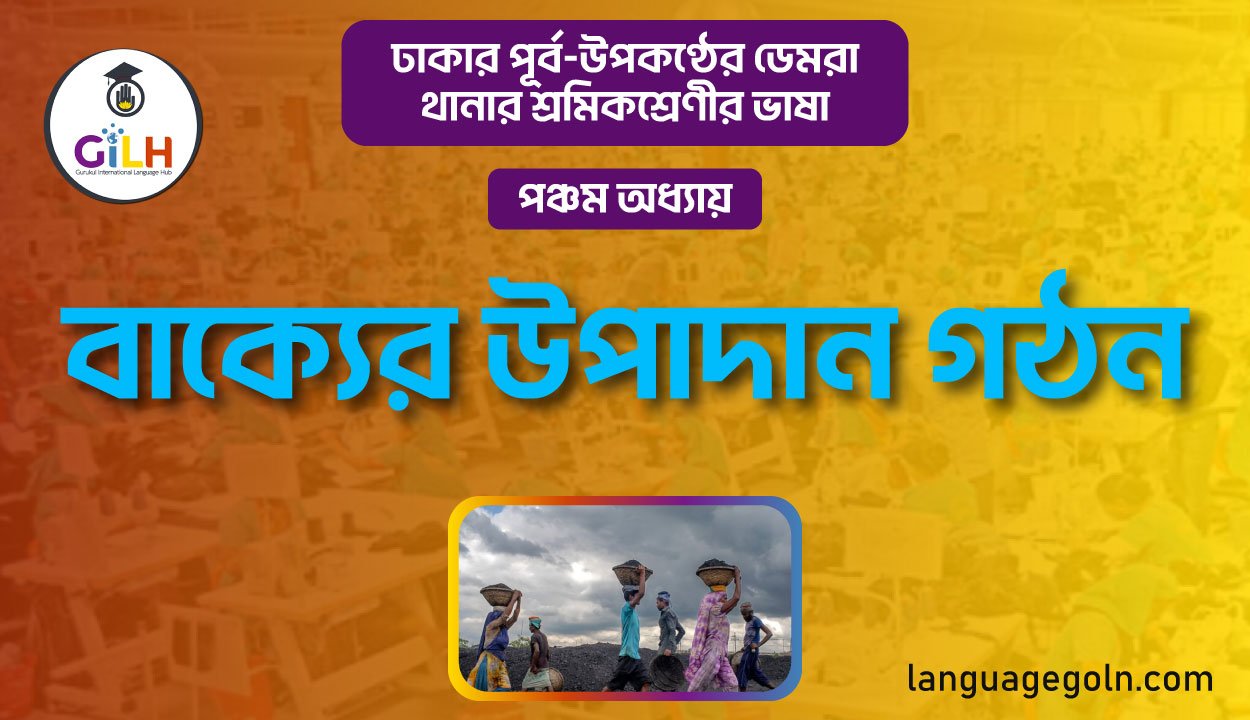আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-বাক্যের উপাদান গঠন
বাক্যের উপাদান গঠন
ক্ষুদ্রতম উপাদানের সমন্বয়ে বৃহত্তর উপাদান দ্বারা বাক্য গঠিত হয়। অর্থবোধক বাক্য তৈরি করতে হলে বাক্যাস্থিত রূপমূলকে সঠিক পদক্রমে সাজিয়ে নিতে হয়। পদক্রম যখন বিভিন্ন গঠনে অংশ নেয়, তখন ব্যাকরণগত গঠন, বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য অথবা বাক্যরূপে চিহ্নিত হয়।
গঠন (Construction) : পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যেকোন উল্লেখযোগ্য শব্দ বা রূপমূল সমষ্টি হল গঠন বা construction, যেমন রমজানের পোলায় নাও বায় (রমজানের ছেলে নৌকা চালায়) উদাহরণে ‘রমজানের পোলায়’ ও ‘নাও বায়’ রূপমূল যুগল দুটি অর্থপূর্ণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তাই এগুলো
গঠন। কিন্তু পোলায় নাও’ রূপমূল জোড়টি পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয় এবং এটি কোন অর্থ প্রকাশ করে না, তাই এটি গঠন নয়, আর ‘পোলায়’ বা ‘নাও’ এগুলো শুধু একেকটি রূপমূল ।
বাক্যাংশ
যখন শব্দদল একটা দলরূপে একক শব্দের মতো ক্রিয়া করে, এই শ্রেণির শব্দব্দল বাক্যাংশ নামে পরিচিত।
বাক্যাংশের প্রকারভেদ
বিশেষ্য বাক্যাংশ -নির্দেশক + বিশেষ্য
একটি-নির্দেশক
ছেলে-বিশেষ্য
বইটি-নিয়েছে
সর্বনাম + বিশেষ্য
সে-সর্বনাম
ভাত-বিশেষ্য
খায়-ক্রিয়া
বাংলায় বিশেষ্য বাক্যাংশের গঠন জটিল থেকে আরও জটিল হতে পারে। ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় ছোট ছোট সরল বাক্যের প্রয়োগ লক্ষণীয়।
ক্রিয়াবাচক বাক্যাংশ বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন- ক্রিয়াবাচক বিশেষণীয় বাক্যাংশ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বাক্যাংশ, ক্রিয়াবাচক অব্যয় বাক্যাংশ ও সমভাবে অন্বিত বাক্যাংশ।
ক্রিয়া বাক্যাংশ-ক্রিয়া + ক্রিয়া বিশেষ্য বাক্যাংশ
কইলামতো-ক্রিয়া
ৰাত-বিশেষ্য
খামু না-ক্রিয়া
ক্রিয়া + বিশেষ্য অংশ + ক্রিয়া + সংযোজক অব্যয় + জিয়া
রও -তুমি
যাইবা-নাকি শুমাইবা
বাক্য
বাক্য কতগুলো শব্দসহযোগে গঠিত, যার সাহায্যে সম্পূর্ণ একটা ভাব প্রকাশিত, যার উদ্দেশ্য ও বিধেয় বর্তমান, যার সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়-গঠনভূত সেই অংশ বাক্যরূপে পরিচিত।
উদ্দেশ্যগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণি বিভাগ
- বিবৃতিমূলক বাক্য
- আদেশমূলক বাক্য
- প্রশ্নবোধক বাকা
- আশ্চর্যবোধক বাকা
গঠনগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণি বিভাগ
- সরল বাক্য
- যৌগিক বাক্য
- জটিল বাক্য
উপাদান (Constituent) উপাদান বা Constituent হল, যা বৃহত্তর গঠনের অংশ। যেমন-‘রমজানের পোলায় নাও বায়’। উদাহরণে চারটি রূপমূল ও চারটি উপাদান আছে। আবার ‘রমজানের পোলায় এবং ‘নাও বায়’ দুটি উপাদান। কিন্তু ‘পোলায় নাও’ কোন উপাদান নয়।
অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent )
সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বাক্য-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে “অব্যবহিত
‘উপাদান’ বা সংগঠনের যেসব উপাদান অব্যবহিতরূপে একত্রিত হয়ে বৃহত্তর অর্থপূর্ণ একক গঠন করে
সেসব উপাদানই হল অব্যবহিত উপাদান।
বাক্য বিশ্লেষণ করতে গেলে বাক্যকে তার অব্যবহিত
উপাদানসমূহে ভাগ করতে হবে এবং এই বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত বাক্যাংশের ন্যূনতম একক বা শব্দ পর্যন্ত
প্রসারিত হবে। অব্যবহিত উপাদান হল দুই বা কয়েকটি গঠনের একটি যার থেকে একটি গঠন
প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন-
“আকাতরের ছেরি নিত্যি স্কুলত যায় (আকতরের মেয়ে রোজ স্কুলে যায়) এই বাক্যে ‘আকস্তরের ছেরি এবং ‘নিত্যি স্কুলত যায় পরস্পরের অব্যবহিত উপাদান। বাক্যটিতে ‘আকতরের ছেরি-উদ্দেশ্যের অব্যবহিত উপাদান ‘নিত্যি স্কুলত যায়’- বিশেষের অব্যবহিত উপাদান।
(আকতরের + ছেরি) + (নিভিন্ন স্কুলত + যাই)
রূপমূলগুলোর মধ্যে নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে বাক্যকে অব্যবহিত উপাদানে বিভক্ত করা হয়। বাকা বিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অব্যবহিত উপাদান। কারণ বিভিন্ন শ্রেণির উপাদানগুলোই অব্যবহিতরূপে একত্রিত হয়ে বাক্য সংগঠনে অংশগ্রহণকারী বৃহত্তর অর্থপূর্ণ একক গঠন করে। সে কারণে অব্যবহিত উপাদানের সাহায্যে প্রত্যেক পর্যায়ের গঠনকে বিভক্ত করে দেখানো যায়।
বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে বাক্যগঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয় গঠন, উপাদান, অব্যবহিত উপাদান, স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গি ইত্যাদি দিকের সমন্বয়ে।
উপাদান গঠন পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয় কিভাবে ক্ষুদ্রতম উপাদান একত্রিত হয়ে বৃহত্তর উপাদান সৃষ্টির মাধ্যমে বাক্য গঠন করে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্য গঠনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য বোঝা যায়। যেমন-
১. বাউল মেলাততে মাইটা পাতিল কিনতে অয় (বাউল মেলা থেকে মাটির পাতিল কিনতে হয়)।
২. জেরায় মাইয়ারে ঢুক দিছে (ছেলেটি মেয়েটিকে মার দিয়েছে)।
এই বাক্য দুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রথম বাক্যে শাব্দিক উপাদান ছয়টি, দ্বিতীয় বাক্যে শাব্দিক উপাদান চারটি।
প্রথম বাক্যে রূপমূল বা ন্যূনতম উপাদানের সংখ্যা আটটি।
বাউল+মেলা+ততে+মাইটা পাতিল+কিনতে+জয় বাউল, মেলাতে (মেলা+ততে), মাইটা, পাতিল, কিনতে (কিন+তে), অন্ত
এখানে বাউল, মেলাত, মাইটা, পাতিল এই চারটি রূপমূল সমশ্রেণির উপাদান বিশেষ্যবাচক পদ। ‘কিনতে’ ‘অ’ ভিন্ন
শ্রেণির উপাদান ক্রিয়াবাচক পদ। আবার ‘তে’ বিশেষ্য ও ক্রিয়া উত্তর উপাদান, যা
উল্লেখিত দুই শ্রেণি থেকে ভিন্ন।
দ্বিতীয় বাক্যে রূপমূল বা ন্যূনতম উপাদানের সংখ্যা ছয়টি।
ছেরা++মাইয়া+রে+দু+দিছে।
ছেরার (ছেরা+য়), মাইয়ারে (মাইয়া+রে), দুক, দিছে।
এখানে ‘ছেরায়’ ও ‘মাইয়ারে সমশ্রেণির উপাদান বিশেষ্য বাচক, আর ‘দুক (মার) দিছে’ ক্রিয়াপদ স্বতন্ত্র উপাদান
এবং ‘য, ‘রে’ বিশেষ্য ও ক্রিয়া উত্তর উপাদান, যা এই দুই শ্রেণির উপাদান থেকে আলাদা ।
প্রথম বাক্য
- বাউল মেলাততে
- বিশেষ্য বাক্যাংশ
মাইটা (মাটির) পাতিল
জিয়া বাক্যাংশ
কিনতে অয় (হয়)
দ্বিতীয় বাকা
বিশেষ্য বাক্যাংশ
১ ছেরায়
২. মাইয়া
ক্রিয়া বাক্যাংশ ১. লুক (মার) দিছে
উল্লেখিত বাক্যটিকে দুটি শক্তবাক্যে বিভক্ত করা যায়-
- বাউল মেলাততে
- মাইটা পাতিল কিনতে হয়।
বাক্যের উপাদান গঠন বন্ধনী ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দেশ করা যায়, যেমন-জিয়ায় পান-সুবারি খায় (বড় চাচি পান সুপারি খায়)
বাক্যটি সামগ্রিকভাবে একটি একক বাক্যের প্রতিটি রূপমূল একটি করে উপাদান।
{{(জিয়া)(য) | {(পান) (সুবারি)} {(খায়)}}
প্রথম বন্ধনী (()) দ্বারা মুক্তরূপমূল ও বদ্ধরূপমূল নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বন্ধনী ({}) দ্বারা বাক্যকে উপাদানসমূহে বিভক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় বন্ধনী (II) দ্বারা সম্পূর্ণ বাক্যটিকে বোঝানো হয়েছে।
‘মাইয়াডা মাছড়ি কুটছে’
মাইয়াডা) (মাছড়ি কুটছে উদ্দেশ্য/বিধেয়
(মাইয়াডা)} {(মাছড়ি) (কুটছে)} কর্তা/কর্ম/ক্রিয়া
{{ (মাইয়া) (ডা)} {(মাছ) (ডি) (কুটছে)}। নির্দেশক/বিশেষ্য
নিচে প্রদত্ত বাক্যের উপাদান সমশ্রেণিতে বিভক্ত করা হল-
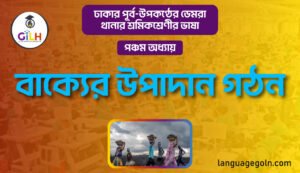
বন্ধনীর সাহায্যে বাক্যের অব্যবহিত উপাদান নির্দেশ করা যায়, কিন্তু বাক্য উপাদানের প্রকৃতিগত ধারণার স্পষ্টতার জন্য প্রয়োজন বৃক্ষ চিত্রের। বাক্যের উপাদান গঠন নিম্নোক্তরূপে চিহ্নিত করা হল :

বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কিভাবে বাক্য গঠিত হয় এবং এসব উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বা পার্থক্যই বা কি তা উক্ত বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিকদের ভাষায় এ ধরনের অসংখ্য বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। বাক্যের রূপমূল পারস্পরিক প্রতিস্থাপন সম্ভব যেমন-
১. ছেরায় বউ পিডায় (ছেলেটা বউ মারে)
২.বেজিডা মুরগি খায় (বেজিটা মুরগি খায়)
৩.বাজানে নাও বায় (বাজান (বাবা) নৌকা চালায়)
উল্লেখিত বাক্যগুলোর উপাদান সমশ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন-

রূপমূলের বিভাজন
বিভাজন অর্থে যে পরিবেশে রূপমূল ব্যবহৃত হয়, তা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- হাপাড়া মাছভারে খায়া হালাইলো (সাপটা মাছটাকে খেয়ে ফেলল)।
আলোচ্য বাক্যে ‘খায়া হালাইলো’ ক্রিয়ার বিভাজন হচ্ছে বিশেষ্য বাক্যাংশ বিশেষ্যবাক্যাংশ- যেমন-“হাপড়া মাছভারে’ (ড্যাম) চিহ্ন দ্বারা বাক্যস্থিত ক্রিয়ার পরিবেশ বা বিভাজন নির্দেশ করা হয়। একইভাবে ‘ডা’-র বিভাজন নিম্নলিখিতভাবে দেখান যায়।
হাপ-মাছ-রে খারা হইল।
ক্রিয়াভেদে ক্রিয়ার পরিবেশও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন- ছেরিডা বাত খায়। এ বাক্যের ক্রিয়া সকর্মক ক্রিয়া
সকর্মক ক্রিয়ার পরিবেশ হল
বিশেষ্য বাক্যাংশ
বিশেষ্য বাক্যাংশ
ছেরিভা
অকর্মক ক্রিয়ার পরিবেশ হল
বিশেষা বাক্যাংশ
বাক্যের উপাদান বিশ্লেষণে নির্বাচনের বিধিনিষেধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যের কোনো একটি উপাদান অন্য
যেকোনো উপাদানের সাথে ব্যবহৃত হয় না। বাক্যতত্ত্বের এই দিকটি নির্বাচনের বিধিনিষেধ নামে পরিচিত। অকর্মক ক্রিয়া বিশেষ্য বাক্যাংশের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, সকর্মক ক্রিয়ার আগে বিশেষ্য বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। বিশেষা বাক্যাংশের সঙ্গে বিশেষ্যউত্তর পদ যুক্ত হয়েছে, কিন্তু ক্রিয়ার শেষে উত্তরপদ যুক্ত হয়নি।
ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে বসেনি, বিশেষ্য বাক্যাংশের পরে বসেছে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল :
ক. রহিমার পোলায় বিলাইডাৱে খেদাইতাছে
(রহিমার ছেলে বিড়ালটাকে তাড়াচ্ছে)
খ।বিলাইডা রহিমার পোলারে খেলাইতেছে।
(বিড়ালটি রহিমার ছেলেকে তাড়াচ্ছে)
গ।জ্য়ক বিলাইডার সুনাম করলে।
(ছেলেটি বিড়ালটার সুনাম করলো)
ঘ।বিলাইডা ছেরার সুনাম করলো।
(বিড়ালটা ছেলের সুনাম করলো)
হাপ-মাছ-রে খায়া হালাইলো।
বিধিনিষেধের দিক-নির্দেশিত। এদিক থেকে বিশেষ্যকে ‘মনুষ্যবাচক’ ও ‘অমনুষ্যবাচক’ উপশাখায় বিভক্ত করা যায়। এ পর্যায়ে বিশেষ্যের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করে, বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মাধ্যমে বাক্যের নির্বাচনী বিধিনিষেধের কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হল-
মানু (মানুষ) রূপমূল (+মনুষ্যবাচক) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
বিলাই (বিড়াল) রূপমূল (+ অমনুষ্যবাচক প্রাণী বিশেষ্য) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বই (বই) রূপমূলে (+অমনুষ্যবাচক বস্তু বিশিষ্ট) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশেষ্য রূপমূলের সঙ্গে ‘খেদানো’ (তাড়ানো) এবং ‘সুনাম’ করা রূপমূলের
নির্বাচনীয় বিধিনিষেধ নিম্নরূপ :
(খেদানো) তাড়ানো
( বিশেষ্য ( + মনুষ্যবাচক / প্রাণ বিশিষ্ট অমনুষ্যবাচক) } বিশেষ্য বাক্যাংশ
( বিশেষ্য (+অমনুষ্যবাচক / প্রাণ বিশিষ্ট অমনুষ্যবাচক)। বিশেষ্য বাক্যাংশ ‘খেদানো’ ক্রিয়ার ফ্রেমের নির্বাচনীয় বিধিনিষেধ নির্দেশ করে যে, এই ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্ম উভয়ই নির্বস্তুক মনুষ্যবাচক বা প্রাণ বিশিষ্ট অমনুষ্যবাচক (অনুভূতিসম্পন্ন চলাচলে সক্ষম) হওয়া দরকার। এ ক্রিয়া কখনো কোন বস্তুবাচক কর্তা বা কর্ম গ্রহণ করে না।
সুনাম করা
( বিশেষ্য (+মনুষ্য বাচক)। বিশেষ্য বাক্যাংশ-বিশেষ্য বাক্যাংশ
‘সুনাম করা’ ত্রিয়ার ফ্রেমের নির্বাচনীয় বিধিনিষেধ নির্দেশ করে যে, এই ক্রিয়ার প্রাণীবাচক কর্তা প্রয়োজন, কিন্তু যে কোন কর্ম ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ কর্ম মনুষ্যবাচক প্রাণবিশিষ্ট অমনুষ্যবাচক কিংবা বস্তুবাচক যে কোনটা হতে পারে। বিশেষ্যের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-
[+ মনুষ্যবাচক], [+ পুরুষ], [+ মূর্ত], [+ গণনাবাচক], [+ সাধারণ] ও [+ বস্তুবাচক
[+ মনুষ্যবাচক] বৈশিষ্ট্য মনুষ্যবাচক ও অমনুষ্যবাচক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈশাদৃশ্য নির্দেশ করে।
উদাহরণ-‘লেহাপাড়া’ করে (লেখা পড়া করে) কেবল মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে । [+ পুরুষ] পুরুষ ও স্ত্রীবাচক প্রাণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন-‘পোয়াতি’ (গর্ভবতী) স্ত্রীবাচক প্রাণ বিশিষ্ট বিশেষ্যকে নির্দেশ করে পুরুষবাচক বিশেষ্যকে নয় ।
[+ মূর্তী মূর্ত বিমূর্ত বিষয়ে বৈশাদৃশ্য নির্দেশ করে। যেমন- কিচ্ছা’ (রূপকথার গল্প)-বিমূর্ত বিশেষ্য নির্দেশ-মূর্ত নয় ।
[+ বস্তুবাচক বস্তুবাচক ও নির্বস্তুক বিশেষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। যেমন- ‘শইল মাজতাছে’ (গোসল করা) এই ক্রিয়ার জন্য বস্তুবাচক কর্তা বিশেষ্যের প্রয়োজন।
+ গণনাবাচক] অগণনীয় ও গণনীয় বিশেষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে । একড়া মাছ (একটা মাছ) গণনাবাচক
ত্যাল (তেল) অগণনীয় অপৃথক বস্তুবাচক নির্দেশে ব্যবহৃত হয়।
[+ সাধারণ] ‘কামাল’ ছবি নামবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে বানদোর (বাঁদর), পাহি (পাখি) ইত্যাদি সাধারণ বিশেষ্যের বৈশাদৃশ্য নির্দেশে ব্যবহৃত হয়। একটি ‘বিশেষ্য’ যতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে তার সবগুলো দেখিয়ে
নিচে উদাহরণে (+)চিহ্ন দ্বারা সাদৃশ্য (—) চিহ্নের দ্বারা বৈসাদৃশ্যকে নির্দেশ করা হল : ছেরা (বালক) বিশেষ্য
(+মনুষ্যবাচক) (+প্রাণ বিশিষ্ট) (+বস্তুবাচক) (+পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (+সাধারণ) ছেরি (বালিকা) বিশেষ্য (+
মনুষ্যবাচক) (+প্ৰাণ বিশিষ্ট) (+বস্তুবাচক) (পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (+সাধারণ) ভাব (প্রেম/বন্ধুত্ব) বিশেষ্য
(মনুষ্যবাচক) (-প্রাণ বিশিষ্ট) (-বস্তুবাচক) (পুরুষ) (-মূর্ত) (গণনাবাচক) (+সাধারণ) কামাল বিশেষ্য (+মনুষ্যবাচক)
(+প্রাণ বিশিষ্ট) (+বস্তুবাচক) (+পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (সাধারণ) সুন্দর (সৌন্দর্য্য) বিশেষ্য (মনুষ্যবাচক) (-
প্রাণ বিশিষ্ট (বস্তুবাচক) (গণনাবাচক) (+সাধারণ) উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোতে বিশেষ্যের অর্থতত্ত্বীয় দিক প্রাধান্য পেয়েছে।
যেমন- ছেরি (মেয়ে) রূপমূলের বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে-এটি (+বস্তুবাচক), (+মনুষ্যবাচক) এবং (পুরুষ) ইত্যাদি ভাব। বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত সর্বনামের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ্যের মত কাঠামোতে নির্দেশ করা হলে এভাবে নির্দেশ করা যায়-
তুই—সর্বনাম (+মনুষ্যবাচক) (+প্ৰাণ বিশিষ্ট) (বস্তুবাচক) (+পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (সাধারণ)
উইটা (সেটা) সর্বনাম (মনুষ্যবাচক) (+প্রাণ বিশিষ্ট) (+বস্তুবাচক) (+পুরুষ) (+মূর্ত) (+গণনাবাচক) (+সাধারণ) ‘তুই’ সর্বনাম মনুষ্যবাচক প্রাণ বিশিষ্ট, মূর্ত ও গণনাবাচক এটি পুরুষ বা স্ত্রী উভয়ই হতে পারে। ‘উইটা’ রূপমূল দ্বারা প্রাণহীন বা প্ৰাণ বিশিষ্ট যেকোন বস্তুকে নির্দেশ করা যায়। তাই (+) ও (-) উভয় চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।
আভিধানিক ও গঠনগত অর্থ
বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ‘রূপমূল’ প্রধান উপাদান হিসেবে গৃহীত। রূপমূলের অর্থগতদিক এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়। একক রূপমূল স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে যে অর্থ প্রাপ্তি হয় তাকে রূপমূলের আভিধানিক অর্থ বলে। এ অর্থ সর্বক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট। বক্তার বক্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক রূপমূলের সমন্বয়ে যখন বাক্য গঠিত হয় তখন রূপমূলগুলোর আভিধানিক অর্থ পরিবর্তিত হয়ে নতুন অর্থ প্রকাশ করে। নতুন প্রকাশিত এ অর্থকে বলা হয় গঠনগত অর্থ।
আভিধানিক অর্থ
কাডল (কাঁঠাল) জিয়া (চাচি), ছেরা (ছেলে) আনছে (এনেছে) লাগি (জন্য)
উল্লেখিত রূপমূলগুলোর প্রতিটির আলাদা আলাদা আভিধানিক অর্থ সম্পন্ন। উল্লেখিত রূপমূলগুলোকে যদি দুই একটা আলাদাভাবে যুক্ত করে সাজিয়ে নেয়া হয় তাহলে এর আভিধানিক অর্থের সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং ভিন্ন এক অর্থ প্রাপ্তি ঘটে।
‘কাডল আনছে’। ‘ছেরা আনছে’
ছেরা আনছে = ছেলে এনেছে এবং
কাডল আনছে = কাঁঠাল এনেছে।
নতুন অর্থ গঠনগত অর্থ প্রকাশ করছে।
উল্লেখিত সব মুক্তরূপমূলগুলোকে বদ্ধরূপমূলের সাহায্যে একত্রিত করে একটি বৃহত্তর ভাষাতাত্ত্বিক
উপাদান গঠন করা যায়-
ছেরায় জিয়ার লাগি কাডল আনছে। এখানে বদ্ধরূপমূল য় র ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে বাক্যের অর্থগতদিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।
বাক্যের ব্যবহৃত রূপমূলের আভিধানিক অর্থ, গঠনগত অর্থ ছাড়াও অব্যয়মূলক অর্থ বিদ্যমান।
মুক্ত ও বদ্ধরূপমূল ছাড়াও কিছু অব্যয়সূচক শব্দের সাহায্যে বাক্যের অর্থগত দিক স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা যায়।
ঐ ছেরায় আলা জিয়ার লাগি কাডল আনছে।
উল্লেখিত বাক্যে ঐ, ‘আলা’ এই অব্যয়সূচক শব্দগুলো মুক্ত ও বদ্ধরূপমূলের সঙ্গে পাশাপাশি সন্নিবেশিত হয়ে জটিল গঠনরূপ নির্মাণে সহায়তা করেছে। এই অব্যয়মূলক শব্দ রূপমূলের গঠনগত অর্থ পরিবর্তনে সহায়তা করে। অব্যয় সংযুক্তির পর প্রকাশিত অর্থকেই বলা হয় অব্যয়মূলক অর্থ ।
ডেমরার শ্রমিকশ্রেণির ভাষায় অব্যয়সূচক শব্দের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বাক্যে ব্যবহৃত রূপমূলের গঠন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান, সেগুলো হল-
১. সম্প্রসারিত রূপ বৈশিষ্ট্য
২. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য
৩. শব্দের অবস্থান
৪. স্বরভঙ্গিরীতি
৫. অব্যয়মূলক শব্দ
আরও দেখুন: