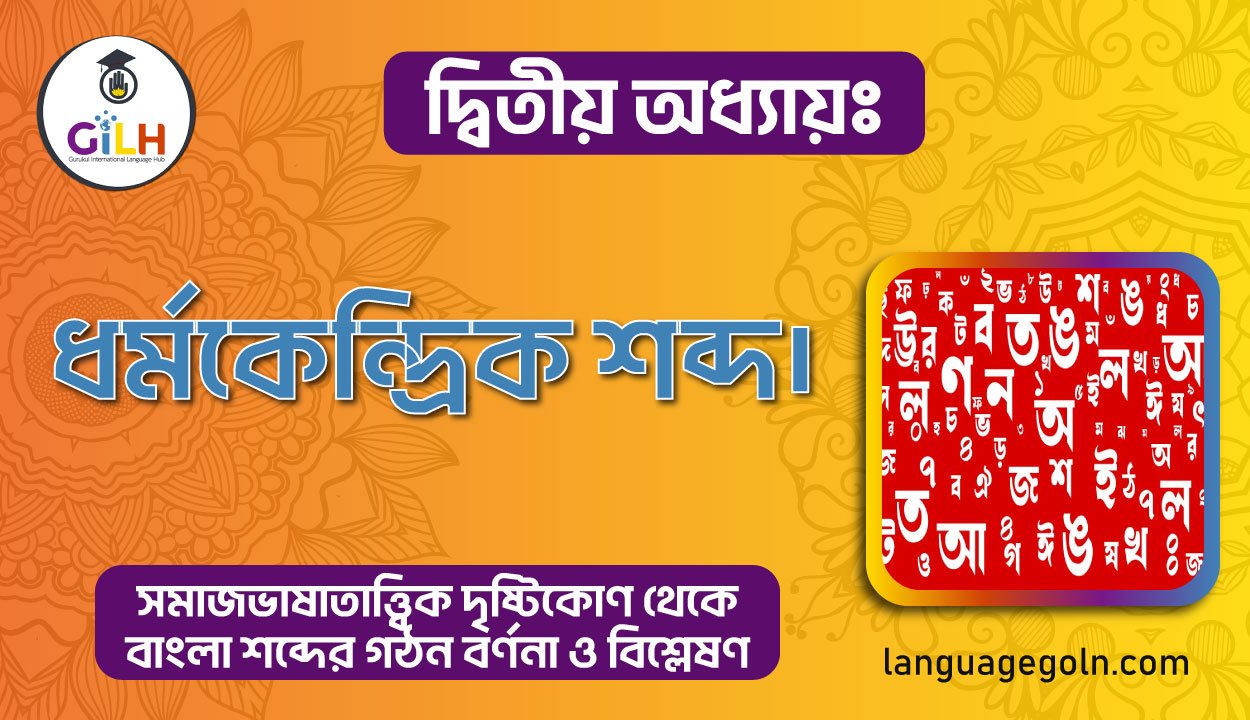আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় -ধর্মকেন্দ্রিক শব্দ
ধর্মকেন্দ্রিক শব্দ
ক. ভূমিকা
পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মানুষ তাঁর জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, স্রষ্টা, ইহলোক পরলোক ইত্যাদি নিয়ে কমবেশি চিন্তা করেন। এই চিন্তার ফসল ধর্ম। পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ধর্মসমূহ হলো ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম, হিন্দু – ধর্ম ইত্যাদি। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম প্রবর্তক দাবী করেন তিনি স্রষ্টার প্রতিনিধি এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টাকর্তৃক প্রেরিত।
প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন স্রষ্টা ছাড়াও মানুষ সূর্য, দেব-দেবী, গাছপালা, ইত্যাদি উপাসনা করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম, ধর্মচিন্তা এবং ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান জন্ম দিয়েছে অসংখ্য শব্দ।
বাংলাদেশে প্রধান চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায় আমরা লক্ষ করে থাকি। যেমন- হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে সুস্পষ্ট কিছু পার্থক্য দেখা যায়।
প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মকেন্দ্রিক মৌলিক শব্দ ছাড়াও রয়েছে ঋণকৃত অনেক শব্দ। ইসলাম ধর্মের কারণে সৃষ্ট হয়েছে কোরআন ও হাদিসকেন্দ্রিক প্রচুর শব্দ। মুসলমানগণ ধর্মকেন্দ্রিক যেসব শব্দ ব্যবহার করে তার প্রায় সব শব্দ আরবি বা কোরআনকেন্দ্রিক নয়।
উর্দু, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা থেকে এসেছে ধর্মকেন্দ্রিক অনেক শব্দ। নিচে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কেন্দ্রিক শব্দ ও প্রাসঙ্গিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হলো।

খ. ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক শব্দ
১. ইসলামী শব্দের সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে ইসলাম, আল্লাহ, খোলা, কোরআন, নামায, রোখা, হজ্জ, যাকাত, কালেমা, হযরত মোহাম্মদ (সঃ), হাদিস, শিয়া, সুন্নী, পয়গম্বর,
রসুল, ঈদুল ফিত্র ঈদুল আয্হা, মক্কাশরীফ, কাবাশরীফ ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ। এসব শব্দের সরাসরি অর্থ অনেক সময় অভিধানের সুলভ। কিন্তু ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক এমনকি ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে (Etymological) সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা যথেষ্ট হয়নি।
ইসলাম ধর্ম মানে শান্তির ধর্ম। একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ইসলাম শব্দ কীভাবে গঠিত হয়েছে তা অনেকরেই অজানা। ইসলাম শব্দের মূলে রয়েছে sim ও তিনটি discontinuous morph আরবি ভাষার শব্দগঠনের নিয়ামানুসারে sim এর সাথে infix যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে সালাম।
সালাম একটি ক্রিয়াপদ। মূল অর্থ বিরোধ বিবাদ এড়িয়ে শান্তি স্থাপন করা। সালাম থেকে গঠিত হয়েছে ইসলাম। আরবি ভাষায় মূল রূপমূল অথবা একটি রূপমূলের আগে ‘মিম’ যুক্ত হয়ে সাধারণত গঠিত হয়- যে করে ধরণের শব্দ। এই হিসেবে সালাম অথবা ইসলামের আগে বদ্ধরূপমূল ‘মিম’ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে মুসলিম।
মাঝে infix সমূহের মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তাহলে মুসলিম শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যিনি শান্তিতে বিশ্বাস করেন। এখানে ইসলামে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর নামের মোহাম্মদ অংশের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। হে, মিম, দাল দিয়ে গঠিত হয়েছে হামদ শব্দ।
হামদ মুক্তরূপমূলের আগে মিম বন্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে মোহাম্মদ মুহম্মদ শব্দটি। হামদ শব্দের অর্থ প্রশংসা। মুহম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়/ প্রসংসিত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ যথাক্রমে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত। ঈমান থেকে গঠিত হয়েছে বাংলায় ঈমানদার, বেঈমান ইত্যাদি বহু শব্দ। ঈমানদার শব্দটি গঠিত হয়েছে আরবি ঈমানের সঙ্গে ফারসি ‘দার’ বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে। অনেকটা এইরকমভাবে ‘বেঈমান’ শব্দটি গঠিত হয়েছে ঈমান রূপমূলের আগে ফারসি ‘বে’
বন্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে। বেঈমান শব্দটির মূল অর্থ হওয়া উচিত ঈমানহীন অথবা ইসলামধর্মে অবিশ্বাসী। কিন্তু বাংলায় এই শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বল যায় বেঈমানের জি’ স্বরধ্বনিটি অর্ধস্বর ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।
নামায শব্দটির ইতিহাস বিস্ময়কর না হলেও চমকপ্রদ। বাঙালি মুসলমানগণ সুদীর্ঘকাল ধরে পরম বিশ্বাসের সঙ্গে নামায পড়ে আসছেন। কিন্তু নামায শব্দটি আরবি ভাষায় নেই। আরবি ভাষায় নামাযের প্রতিশব্দ সালাত। একই কথা রোযা শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
রোযা শব্দটি ফারসি। রোযার মূল শব্দ সাওম বা সিয়াম। সাওম শব্দের বহুবচন হচ্ছে সিয়াম। সাওম মাসের আক্ষরিক অর্থ restraint, abstinence from all improper or unlawful acts. (গোলাম মাকসুদ হিলালী; ১৯৬৭: ২৮৪)। রোযার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দসমূহের মধ্যে উল্লেযোগ্য হচ্ছে রমজান/রমযান, ঈদুল ফিত্র আরো অনেকশব্দ।
বাহার উদ্দিন লিখেছেন- ‘রমজান’ শব্দটি আরবি ‘রমজ’ ধাতু থেকে আগত। ‘রমজ’ মানে দাহ, তাপ, পোড়ানো। আরবি শব্দতাত্ত্বিকদের ধারণা, চান্দ্র মাস চালু হওয়ার চান্দ্র বর্ষই নিয়ন্ত্রিত করে মুসলমানদের উৎসব] অনেক আগে প্রাচীনকালে গরমের মৌসুমে এই মাস পড়ত বলে এর নাম হয় রমজান।
রমজানের সঙ্গে উপবাসের আরবি প্রতিশব্দের ধ্বনিগত কোনো মিল নেই। উপবাসের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে ‘সওম’। এর অর্থের সঙ্গেও উপবাস ব্রতের কোনো মিল নেই। এর অর্থ হলো আরাম বা বিশ্রামে থাকা।
“এবং হিযরতের পরেই সম্ভবত ইহুদি বা সিরিয়ার সূত্র থেকে উপবাসের প্রতিশব্দ হিসাবে সপ্তম শব্দটি গ্রহন করেন মুহম্মদ।
কোরআনের ১৯ নং সূরা মরিয়মের ২৭ নং আয়াতে সওম শব্দটির উল্লেখ আছে” (মুনতাসীর মামুন ২০০০:১৪)। বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত শব্দ রমজান এবং রমযান ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ফারসি ভাষার প্রভাবে রমযান এবং বাংলার ধ্বনি বৈশিষ্টানুসারে রমজান
শব্দটি প্রচলিত। অতি সম্প্রতি ব্যবহৃত হচ্ছে ‘রমাদান’। রমাদানের ‘দ’ আসলে জোয়ান এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিভাষায় interdental ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, ইরানিরা আরবের ধর্ম নিয়ে ছিল, ভাষা ও সংস্কৃতি নেয়নি। নামায, রোযা, ইসলামের মূল স্তম্ভের পরিচয়বাহী এ শব্দ দুটি একথাই সত্যতা প্রমাণ করেন ।
বাহার উদ্দিনের আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে ইতি টানা যায়। “ঈদ, সত্তম এবং রমজানের মূল অর্থ এবং তাদের উৎসভূমির ভিত্তিতেই অনুমান হয়. রোজার উপবাস জন্ম নিয়েছে কৃষিনির্ভর সমাজে হয়ত বা প্রাচীন সিরিয়ায়”। মুনতাসীর মামুন: ২০০০: ১৩) ।
ঈদুল ফিতর বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। ঈদুল ফিতরকে কেউ কেউ ভুলক্রমে ফেতরার ঈদ বলে থাকেন (বিশেষ করে গ্রামে শব্দটি প্রচলিত)। ‘ঈদ’ আরবি শব্দ। এর দুটি আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়। এক, পুনর্গমন বা বার বার ফিরে আসা দুই, আনন্দ।
অন্যদিকে ফিতর শব্দের অর্থ ভেঙ্গে দেওয়া, অন্য অর্থ বিজয়। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখা বা উপবাস করার পর যে উৎসব পালন করা হয়, তাই ঈদুল ফিতরের উৎসব। ‘বিজয়’ অর্থটি ব্যঞ্জনাময় পুরো রমজান মাস রোজা রেখে মানুষ তার কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে এক ধরনের বিজয় অর্জন করে এ অর্থে তা বিজয় উৎসবও বটে। ( শিশু বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, 287 )
সাধারণ জনগণের কাছে ঈদুল ফিত্র ঈদ অথবা ছোট ঈদ হিসেবে পরিচিত। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলেন ঈদুল ফিত্র। এখানে দুটি ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা সন্ধির নিয়মানুসারে ঈদ-উল হয়েছে ঈদুল / ইদুল আর অন্যদিকে যেহেতু বাংলা শব্দের শেষে যুগ্ম ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয় না সেহেতু ফির হয়েছে ফিতর।
ঈদ-উল- আয্হা শব্দটি বাংলায় ‘ইদুল আযহা’ অথবা ‘ঈদ-উজ-জোহা’ হিসাবে পরিচিত। সাধারণ জনগণসহ অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান ঈদ-উল-আযহার বদলে কোরবানীর ঈদ, বকরি ঈদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। কোরবানী শব্দটির মূলে রয়েছে আরবি
শব্দ গঠনের নিয়মানুসারে discontinuous কাফ, রে, বে। কাফ, রে, বে এর সঙ্গে prefix, suffix, infix যুক্ত হয়ে কোরবান এবং কোরবানী শব্দ দুটো গঠিত হয়েছে। মূল অর্থ নৈকট্য লাভ করা অথবা উৎসর্গ করা। “কুরবানী- একটা প্রথা যা বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। ‘কুরবানী’ শব্দটি ক্রিয়াপদ এসেছে ‘কুরবান’ থেকে অর্থ উৎসর্গ করা।
হিব্রুতে বলা হয় কোরবান (Kurban) কু-র-র ধাতু থেকে উৎপন্ন। ধাতুগত অর্থে এর মানে হয় নৈকট্য। দেবতা ঈশ্বর বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ যারা হয় তাও কুরবান নামে পরিচিত। এই প্রথা আদিকাল থেকে চলছে। আদমের দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল ঈশ্বরকে সম্রষ্ট করার জন্য কুরবান করল।
যেমন কোরআনে আছে “এবং তাহাদের নিকট সত্যভাবে অসমের দুই পুত্রের কথা বর্ণনা করা হয়। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের উৎসর্গ কবুল হয়েছিল” (কোরআন, ৫ ও ২৭)। তাছাড়া আরও আছে দুই স্থানে (৩১৮৩ এবং ৪৬:২৮)। যেখানে বলা হয়েছে “যাহারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদিগকে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো রসুলের ওপর ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের জন্য এমন কুরবানী (করার আদেশ) লইয়া আসে যাহা অগ্নি গ্রাস করে” (৩ঃ ১৮৩)।
অতএব তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে (তাহারা) নৈকট্য লাভের জন্য যাহাদিগকে মাবুদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল উহারা কেন তাহাদের সাহায্যে আসিল না (৪৬:২৮)। প্রথমোক্ত স্থানে ‘কুরবান’ উৎসর্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী স্থানে নৈকট্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (সাদউল্লাহ, দৈনিক জনকণ্ঠ ঈদ-উল-আযহা সংখ্যাঃ ১৭)।
বকরি ঈদ শব্দের সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন- “কোরবানীর ঈদ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু বকরী ঈদঃ অনেকের ধারণা সুরা বাকারা থেকে ‘বকরী’ শব্দটি চালু হয়েছে। বাকারা সুরায় গাভী সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তা অন্য প্রসঙ্গে। ঈদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া বকরী মানে আমরা
নির্দিষ্টভাবে একটি পশু ছাগল (খাসী) কেই বুঝি। একশো বা দেড়শো বছর আগে বাংলাদেশে গরু কোরবাণী দেয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে হিন্দু জমিদারের অঞ্চলে যেখানে গরু কোরবাণী সম্পর্কে তারা বৈরি মনোভাব পোষণ করতেন। কোরবাণী যদি কেউ দিতেন তাহলে খাসী বা ছাগলই দিতেন।
‘বকরা মানে গাভী। আরবি এই শব্দটির বিকৃত রূপ হয়েছে ‘বকরি’। কিন্তু গরু যেহেতু কোরবাণী দেওয়া সম্ভব নয়, কোরবাণী দেওয়া হচ্ছে ছাগল, ভাই বকরী মানে দাঁড়িয়ে গেল ছাগল ” । (পূর্বোক্ত; ২০০০: ২৭)।
সম্মানসূচক রূপমূল, বন্ধরূপমূল ও সংক্ষিপ্ত রূপ প্রসঙ্গঃ ইসলামকেন্দ্রিক, কয়েকটি মুক্তরূপমূলের সঙ্গে শরীফ রূপমূল যুক্ত করে সম্মান দেখানোর একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। যেমন- কোরআন শরীফ, দুরুদ শরীফ, হাদীস শরীফ, বোখারী শরিফ, মক্কাশরীফ, কাবাশরীফ ইত্যাদি।
ইরানের কবি রুমি রচিত মসনবী গ্রন্থকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় বলে কেউ কেউ গ্রন্থটিকে মসনবী শরীফ বলেন। ইসলামে মহানবী হযরত মোহাম্মদের নামের পাশে বন্ধনীতে লিখিত হয় সং অথবা দঃ। সঃ এর পূর্ণরূপ হলো সল্লল্লাহু আলাহিস সালাম।
দঃ এর পূর্ণরূপ দরুদ। অর্থাৎ পাঠককে হযরত মোহাম্মদের নাম উচ্চরণের সঙ্গে দরুদ অর্থাৎ (সঃ) পড়তে বলা হচ্ছে। দরুদ শব্দটি এসেছে ফারসি দুরুদ থেকে যার অর্থ দোয়া, দয়া ইত্যাদি। স পঃ এর মতো বিভিন্ন নবী ও খলিফাদের নামের পাশে বন্ধনীতে আঃ, রাঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন হযরত নূহ (আঃ), হয়রাত ওমর (রাঃ) ইত্যাদি। আঃ এর পূর্ণরূপ আলাহিস সালাম (রাঃ) এর পূর্ণরূপ রাদিয়াতাল্লাহ / রাজিয়াল্লাহ আনহু। নবী কন্যা ও পত্নীর ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় রাদিআল্লাহ আনহা।
রাদিআল্লা রাজিআরা এর মধ্যে ‘দ’ এবং ‘জ’ এর উচ্চারণ কোনটিই সঠিক নয়। ন জ এর বদলে হবে জোয়াদ এর উচ্চারণ। IPA এর ভাষায় interdental প্র সম্মানিত নবী এবং ইসলামী শাস্ত্র উচ্চশিক্ষা লাভকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কয়েকটি
উপাধি ব্যবহৃত হয়। যেমন- হযরত আল্লামা মাওলানা, মৌলভী, মুন্সী ইত্যাদি। ১৯৯০ দশকের পূর্বে শুধুমাত্র নবীদের নামের আগে হযরত শব্দ ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো কোনো ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির নামের আগেও হযরত উপাধি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।
আল্লামা শব্দটি অতি উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের নামের আগে ব্যবহৃত হতো ১৯৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত। যেমন- আল্লামা ইকবাল। এখন ইসলাম ধর্মে উচ্চশিক্ষিত কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আল্লামা ব্যবহৃত হয়।
মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী নামের আগে মাওলানা, ফাজেল পাশ ব্যক্তিদের নামের আগে মৌলভী এবং মাদ্রাসায় সামান্য কিছু লেখাপড়া করেছেন এমন ব্যক্তিদের নামের আগে মুন্সী ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।
পুরুষদের নামের আগে মোহাম্মদ ও মেয়েদের নামের আগে মোসাম্মৎ এবং নামের পরে বেগম, খাতুন, খানম ইত্যাদি শব্দও সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশ আসল (মূল) নাম আরবি-ফারসি প্রভাবিত (রাজীব হুমায়ুন: ২০০১:৭১)।
মুসলমান পুরুষদের নামের আগে শতকরা নব্বই ভাগের অধিক ক্ষেত্রে মুহম্মদ ব্যবহৃত হয়। যেমন- মুহম্মদ আবুল হুসেন, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ইত্যাদি। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় নামের আগে স্বধর্মের রসুলের নাম সংযোজিত হয়েছে। অথবা এও হতে পারে মুহম্মদ শব্দের মাধ্যমে মুহম্মদী ধর্ম, বোঝানো হয়েছে।
১৯৬০-৭০ দশক পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলমান মহিলাদের নামের আগে মোসাম্মৎ শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মোসাম্মৎ শব্দের মূল অর্থ ভদ্রমহিলা। ধর্মীয় অনুষঙ্গবাহী অন্য দুটি পদবি হচ্ছে সৈয়দ, কোরায়শী। এ দুটি পদবিধারীগণ নিজেদেরকে হযরত মোহাম্মদ এবং কোরাইশ বংশের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেন, এ দাবীর পেছনে সত্যতা থাক বা না থাক। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন বাঙালি মুসলমানের অনেকেই তাদের আরবি-ফারসি নামের অর্থ জানেন না।
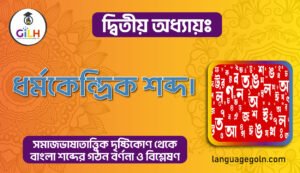
২. শব্দের গঠন এবং রূপমূল সম্পর্কে অসচেতনতা
আরবি-ফারসিজাত শব্দসমূহের গঠন এবং রূপমূল সম্পর্কে স্বাভাবিক অসচেতনতা রয়েছে। এটি দোষের কিছু নয়। ভবিষ্যতের সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ভাষাতাত্ত্বিকগণ সব শব্দের গঠন সম্পর্কে সচেতন হলে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটবে।
যেমন বাংলায় ‘বিসমিল্লাহ’ শব্দটি মুসলমান পরিবারে ‘বিসমিল্লা’ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। খাওয়ার শুরুতে এবং অনেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। মাঝে মাঝে ‘বিসমিল্লায় গলদ’ ও হয় এবং হিন্দু পরিবারেও মাঝে মাঝে বিসমিল্লায় গলদ হতে শোনা যায়।
বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ধারণায় বিসমিল্লাহ একটি শব্দ। এ শব্দটির মধ্যে মুক্তরূপমূলসহ যে চারটি রূপমূল আছে তা বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায়। আরবিতে বিসমিল্লাহ শব্দটি গঠিত হয়েছে বে+ইসম+এ+ আল্লাহ এ চারটি রূপমূল দ্বারা। একই কথা পয়গম্বর শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
বাংলা ভাষাভাষীর ধারণায় (Concept) এ পয়গম্বর শব্দটি একটি মাত্র রূপমূল দিয়ে গঠিত। পয়গম্বর শব্দে কমপক্ষে দুটি রূপমূল (পঞ্চগম+বর) রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ‘বাংলায় ব্যবহৃত আরবি ফারসিজাত ধর্মীয় অনেক শব্দেই ‘হ’ লোপ পায়। যেমন- আল্লাহ> আল্লা, ঈদগাহ> ঈদগা, বিসমিল্লাহ> বিসমিল্লা ইত্যাদি ( সৌরভ সিকদার ২০০২: 230)
৩. ইসলামী শব্দ ও শব্দসমষ্টির ভুল প্রয়োগ
আরবি ফারসির প্রভাবে বাংলায় আশেক, আশেকান, মুরিদ, মুরিদান, শহীদ, শহীদান, আসামি, আসিমিয়ান এ জাতীয় কিছু শব্দ এসেছে। মুক্তরণমূলের সঙ্গে বহুবচনসূচক ‘আন’ যুক্ত হয়ে আশেকান, মুরিদান, শহীদান, আসামিয়ান ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়েছে।
আসামিয়ান শব্দটি আজকাল অপ্রচলিত। শহীদান শব্দটি ধর্মযুদ্ধে বিশেষ করে ইসলামের জন্যে শাহাদাৎ বরণকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার কথা। কিন্তু আজকাল শহীদ শব্দটি ভাষাশহীদ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ এমনকি
পশ্চিমবঙ্গের কোনো ন্যায় সংগ্রামে প্রাণদানকারী হিন্দু ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আশেকান, মুরিদান, শহীদান প্রত্যেকটি শব্দই বহুবচন। বহুবচনসূচক ‘আন’ সম্পর্কে সচেতন নন বলে অনেকেই ব্যবহার করেন মুরিদানদের, শহীদানদের ইত্যাদি শব্দ। বাংলায় জান্নাতবাসী, আব্বাজান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাংলা ভাষাভাষী হিন্দুরাও ব্যবহার করেন স্বর্গীয় পিতা, স্বর্গীয় মাতা ইত্যাদি শব্দ। এ শব্দসমষ্টির প্রয়োগে ভুল রয়েছে।
ইসলামী শাস্ত্রানুসারে মৃত্যুর বহুবছর পরে কিয়ামত হবে, তারপর হাশরের ময়দানে বিচার হবে। বিচারের পর কেউ জান্নাতবাসী, কেউবা জান্নাতবাসিনী হবেন। যেহেতু শেষ বিচারের আগে কে জান্নাতবাসী হবেন অথবা হবেন না তা বলা সম্ভব নয়, তাই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়া ভুল।
হৃদয়ের আকো, মনের আকো, সন্তানের আবেগকে প্রশ্রয় দিলে এ ধরণের ভুল প্রয়োগকে মেনে নেয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত বিধর্মী ও সহধর্মীনি নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। বাঙালি মুসলমানের ধারণায় (Concept) বিধর্মী বলতে যার ধর্ম নেই অথবা নাস্তিককে বোঝায়। একজন হিন্দু অথবা খ্রিস্টানকে বিধর্মী না বলে ভিন্নধর্মী বা ভিন্নধর্মাবলম্বী বলাই শ্রেয়। সহধর্মী, সহধর্মীনি স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দ। স্বামীর সঙ্গে একই ধর্মে বিশ্বাসী স্ত্রী হলেন সহধর্মীনি।
সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দম্পতির ক্ষেত্রে এখন এ শব্দটি প্রযোজ্য নয়। তাই প্রশ্ন করা যেতে পারে “প্রমিলা সেনগুপ্ত কি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সহধর্মীনি ছিলেন?” বাংলাদেশের অনেকের নাম আব্দুল খালেক, আব্দুল মালেক, আব্দুল মাবুদ, আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি।
আব্দুল খালেক মানে স্রষ্টার বান্দা (নাস), আব্দুল মালেক মানে প্রভুর বান্দা, আব্দুল মা’বুদ মানে স্রষ্টার বান্দা, আব্দুর রাজ্জাক মানে রিযিকদাতার বান্দা। কোনো মানুষ খালেক (স্রষ্টা), মালেক (প্রভু), মাবুদ (স্রষ্টা), রাজ্জাক (রিযিক প্রদানকারী) হতে পারেন না। অথচ মালেক, মালেক সাহেব সার, খালেক, খালেক
সাহেব / সাব, মাবুদ, মারুন সাহেব /সাব, নামে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে ডাকা হয়। উপভাষায় এ পরিস্থিতি আরো করুণ। উপভাষাসমূহে খালেইক্কা, মালেইক্কা, রাজ্জাইকা ভাষা শোনা যায় প্রতিনিয়ত। শব্দের অর্থের বিষয়ে উদাসীন বা অসচেতন বলে এ ধরনের শব্দ নির্বাচন করা হয় নামের ক্ষেত্রে।
৪. ইসলামী শব্দের ধ্বনি ও রূপমূলগত ধ্বনি পরিবর্তন (Morphophonemic change)
ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত এ্যাডাম, মেরি, জ্যাকব, আব্রাহাম আরবি ও বাংলায় পরিবর্তিত হয়েছে যথাক্রমে আদম, মরিয়ম, ইয়াকুব এবং ইব্রাহীম হিসেবে। রমযান, রমাদান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কারি শব্দের প্রথমে রয়েছে আরবি ‘কাফ’ এবং কারি শব্দটির জন্ম হয়েছে কোরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণকারীর জন্য।
বাংলায় কারি শব্দের বদলে কারি শব্দ শোনা যায় প্রায় সময়ে। আরবি, ফারসি প্রভাবিত শের-এ-বাংলা, মান-এ-জান্নাত, কোরআন-এ হাফেজ, কায়েদ-ই-আজম ইত্যাদি শব্দ সমষ্টি বাংলায় আনায়াসে পরিবর্তন হয়ে যায় শেরে বাংলা, খাতুনে জান্নাত, কোরানে হাফেজ, কায়েদে আজম ইত্যাদিতে।
শের-এ-বাংলা এবং কায়দ-ই-আজম এ দুটি শব্দসমষ্টি যে উপাধি বিশেষ এ তথ্য অনেক বাঙালি পাঠকেরই অজানা।
৫. ইসলামী শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা
(অ) কোরআন হাদিসকেন্দ্রিক শব্দঃ আল্লাহ, ইসলাম, মোহাম্মদ, কোরআন, কোরআন মজিদ, কোরআন শরীফ, আদম হাওয়া, হাদিস, নামায, হজ্জ, যাকাত, মোহাদ্দেস, শিয়া, সুন্নি, হানাফি, আহলে হাদিস, আহলে সুন্নত, আহমদিয়া, ইবাদত, ইফতার, সালাত, ইসলামিয়া, কিবলা, কিবলারোখ, যুতবা, খলিফা, খিলাফত, তাওহিদ, আযান, মোয়াজ্জেম, পয়গম্বর, রসুল ও আরো অসংখ্য শব্দ
আ) ইসলামী আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক শব্দঃ ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আয্হা, মোহররম, আসুরা, তাজিয়া, ফতেহা-ইয়াজ দহম, মিলাদ-উন-নবী, মিলাদ শরীফ, শব-ই-কদর, শব-ই-মেরাজ, শব-ই-বরাত, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ ।
(ই) ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কিত শব্দঃ মাদ্রাসা, মোদারেস, মক্তব, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, জামাতে উলা, আলেম, ফাজেল, কারি, কোরআনে হাফেজ, তালেবে আলেম, তালেবান ইত্যাদি।
(ঈ) ইসলামী শব্দ বিবিধঃ আবে জমজম, আবে হায়াত, জেহাদ, মুজাহিদ, দজ্জাল, সরাব, সুফি, বাউল, ফকির, মাইজভান্ডারি, রাজাকার, মৌলবাদী, আল-বদর, আল- শামস, জিয়ারত, হারাম, হালাল, শিরক, হেরা গুহা, ইন্তেকাল, ওফাত, গায়েবানা জানাজা, কুলখানি, চেহলাম, চল্লিশা, কারবালা কান্ড, হাতেম দিল, হাতেম তাই, শয়তান, ইবলিশ, ওমরা হজ্জ, ইফতার পার্টি ও আরো অসংখ্য শব্দ।
বাংলায় আসার পর বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কিছু কিছু শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে।
ফারসির প্রভাবে সালাতের বদলে নামায বহুল প্রচলিত হয়েছে। শয়তান এবং ইবলিশের অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে। আল-বদর, আল-শামস, রাজাকার শব্দসমূহে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর পরিবর্তিত অর্থে বহুল প্রচলিত হয়েছে।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে আঁতাত করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার জন্য ঐতিহাসিক-সামাজিক কারণে বাংলায় মূল রাজাকার শব্দের অর্থেরই বদল ঘটেছে। এটি এখন বিশ্বাসঘাতক অর্থে প্রয়োগ হয়। এ প্রসঙ্গে “মীরজাফর” শব্দটির কথাও উল্লেখ করা যায়। বর্তমান গবেষণায় পরিসরের সংক্ষিপ্ততার কারণে অধিকাংশ শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বাংলায় বহুল প্রচলিত কয়েকটি শব্দের গঠন নিচে বর্ণিত হলোঃ-
(১) জালেম, জুলুম, মজলুম এ শব্দগুলো বাংলায় প্রচলিত। আরবি ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে ও শব্দ সমূহের গঠন সম্পর্কিত একটি ছক নিচে উপস্থাপিত
হলো।
(২) শহীদ, শাহাদাত শব্দ দুটি বাংলায় বহুল প্রচলিত। এ শব্দের গঠন নিম্নরূপ।
শহীদ আরবি শব্দ। ফারসি বদ্ধরূপমূল ‘দান’ মিলে পরবর্তীকালে শহীদান শব্দটি
গঠিত হয়েছে।
গ. হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক শব্দ
বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা সর্বাধিক। ফলে বাংলা ভাষায় হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক অসংখ্য শব্দ রয়েছে। শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপঃ
(অ) মূল শাস্ত্রকেন্দ্রিক শব্দঃ ঈশ্বর, ঐশ্বরিক, বেদ, বৈদিক, বেদান্ত, বৈদান্তিক, বিষ্ণু, বৈষ্ণব, শক্তি, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সহ আরো অসংখ্য শব্দ ।
(আ) আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক শব্দঃ অগ্নিপূজা, অগ্নিসাক্ষী, আগমনী, আদশোদ্ধ, আল্পনা, কীর্তন, নামসংকীর্তন, অষ্টপ্রহর কীর্তন, গঙ্গাযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দীপাবলী
দেওয়ালী), ধর্মঘট, কুশপুত্তলিকা, ব্রত, অন্নপ্রাসন, নবপত্রিকাস্নান, কলাবউ, ভাইফোঁটা প্রভৃতি শব্দ।
(ই) হিন্দু দেবদেবী ও অবতার কেন্দ্রিক শব্দঃ শিব, পার্বতী, অনুপূর্ণা, উর্বশী, দূর্গা, চণ্ডী, কালি, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, পাণ্ডব, কৌরব, অর্জুন, দ্রৌপদী, নটরাজ ও আরো অসংখ্য শব্দ।
(ঈ) শিক্ষাকেন্দ্রিক শব্দঃ আশ্রম, তপোবন, তপস্বী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চর্তুবেদী, শাস্ত্রী ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ।
বিবিধ শব্দঃ কুরুক্ষেত্র, লঙ্কাকাণ্ড, তিলক, তিলোত্তমা, দক্ষিণা, দেবদাসী, দেবোত্তর, দত্ত, দৈব, সতীদাহ, গৌরীদান, কুমারীপূজা, পূজনীয়, কাঁসার ঘন্টা, সাঁখ, পতিদেব, পতিপরমেশ্বর, কুলীন, কৌলিন্য, কৌলিন্য প্রথা, বৈষ্ণব, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, ভাবসম্মিলন, অভিসার, অভিসারিকা, খণ্ডিতা ইত্যাদি শব্দ ।
২. শব্দের গঠনঃ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। এই হিসেবে পণ্ডিতগণ এসব শব্দের প্রসঙ্গে তৎসম ও তদ্ভব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের অর্থ তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের মত।
যে সব শব্দ সংস্কৃতের অবিকৃত রূপে প্রাকৃত ব্যবহৃত হোত, প্রাকৃতে বৈয়াকরণিকেরা তার নামকরণ করেছিলেন তৎসম শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, ‘তৎ’ বা তার অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ‘ সম’ রূপে ব্যবহৃত বা উচ্চার্য শব্দগুলিই তৎসম শব্দ। বাংলা ভাষায় অজস্র তৎসম শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে অবিকৃত রূপেই গৃহীত হয়েছে। তবে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে স্বাচ্ছন্দে দেখানো চলে যে, সংস্কৃত ধ্বনিসামা বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ রীতিতে পরিত্যক্ত।
যেমন- পদ্ম, শ্মশান, লক্ষ্মী, ও, জিহ্বা ইত্যাদি অসংখ্য তৎসম শব্দ বাংলায় ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় (তরুণ ঘোষ, ১৯৯৬; ৭৩)।
পদ্ম ও লক্ষ্মী শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ম ও লক্ষ্মী। কিন্তু শব্দ দুটি বাংলায় উচ্চারিত হয় যথাক্রমে পদ ও লখি।
এধরনের ধ্বনি পরিবর্তন দেখানো যার অনেক সংস্কৃত শব্দে। যেমন- ঈশ্বর শব্দটির কথা ধরা যাক। ঈশ্বর শব্দ সংস্কৃত, হিন্দি উচ্চারণ ইশওয়ার (Iswar) বাংলা উচ্চারণ ইশশর।
অর্থাৎ ” ‘ই’-তে পরিণত হয়েছে। অন্তস্থ ব বানানে আছে, উচ্চারণে নেই। ব-ফলা যুক্ত অধিকাংশ শব্দে বাংলায় দ্বিত্ব হয়। যেমন- শ্ব’ হয়েছে ঈশ্বরের পর স্বয়ং বিদ্যাদেবীর উপরেও কম অবিচার হয়নি। সরস্বতী শব্দের মূল সংস্কৃত উচ্চারণ সরসওয়াতি (Soroswati )। বাংলা উচ্চারণ ‘শরণশতি’।
দন্ত্য-স এর ব্যবহার বাংলায় কম বলে সব দন্ত্য স তালব্য শ তে পরিণত হয়েছে। মুহম্মদ আবুল হাই এর ভাষায় পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ‘শ’ তে পরিণত হয়েছে (মুহম্মদ আব্দুল হাই; ১৯৬৪, ১২৮ )। সরস্বতীর দণ্ডা-স ব-ফলা যথারীতি দ্বিত্ব হয়েছে শশ। হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক অধিকাংশ শব্দের গঠন বিশ্লেষণে দুতিনটি সূত্রের প্রাধান্য রয়েছে।
এবং এ সূত্রসমূহ গুণবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। গুণবৃদ্ধি অনুসারে কোনো মুক্তরূপমূলের শেষে – ইক/ষ্ণিক য-ফলা ইত্যাদি যুক্ত হলে বাংলা প্রারম্ভিক ধ্বনিগুলোর গুণবৃদ্ধি
অর্থাৎ অ আ ই ঈ ঐ ঔ ই এ ঐ ও ঔ । এ সূত্রসমূহ মনে রাখলে ঐশ্বরিক শব্দের মধ্যে ঈশ্বরকে এবং বৈদিক শব্দের মধ্যে বেদকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।
গঠন বিশ্লেষণ ও ঐশ্বরিক, ই> ঐ। ইক এর প্রভাবে ই পরিণত হলো ঐ কার এ। ফলে ঈশ্বর হলো ঐশ্বর। এরপর হলো ঐশ্বরিক। একই সূত্র বৈদিক শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বেদ+ইক বৈদিক। ইক এর প্রভাবে বেদের ‘এ’ হলো ‘ঐ’। তাহলে বেদ হয়ে গেল বৈদ। বৈদ+ইক = বৈদিক।
তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা, অসংখ্য পৌরাণিক চরিত্র এবং বারো মাসের তের পার্বন এবং পার্বন সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠান বিষয়ক শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান সুকঠিন। কাজেই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বিশ্লেষণ সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হলোঃ
(অ) দেবতা
“দেবতা এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ যাঁরা আপন ক্রীড়া বা দীপ্তি দ্বারা বিশ্ব ব্যপ্ত করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে এই শব্দ ও তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতিতে দেবস, লাতিন ভাষায় দেব দেইভাস, লিথুয়ানিয়ায় দেবস্ ফরাসিতে দেইতি, ইংরেজিতে ডেইটি, ইতালিতে দেইতা, স্পেনীয় দেইদাদ, ক্রোশিয়ায় নেইতাত, ফারসিতে দার, জার্মানিতে দেইদাদি । ঋদ্বেগে অদিতি, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুন, প্রজাপতি, বিষ্ণু, সবিতা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম আছে (শিশু ১৯৯৭: ১৩৬: তৃতীয় খন্ড)।
দেব-দেবতা, দেব-দেবী, দৈবচক্র, দৈবিক ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক শব্দ বাংলায় বহুল ব্যবহৃত। দেবী শব্দটি দেবের স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যেমন- দূর্গাদেবী, মনসাদেবী, দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।
গবেষক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের মতে- “কিছুদিন আগেও বাংলাদেশে কেবল ব্রাহ্মণ জাতীয় স্ত্রীলোকগণই নামের শেষে দেবী লিখিতেন। এখন ‘দেবী’ শব্দের ব্যবহার
জাতি বিশেষ নিবন্ধ নহে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের রমনীরাই আজকাল নামের শেষে ‘দেবী’ লিখিতেছেন। তখন থিয়েটারে বায়স্কোপে অভিনেত্রীরাও দেবী। বিদেশী মহিলারাও মধ্যে মধ্যে শখের ভারতীয় নাম লইয়া প্রাণে একটি ‘দেবী’ সংলগ্ন করেন। ইংরেজীতে নামের শেষে যে Esq. লেখা হয় তাহাও প্রথমে আমাদের দেবীর মতই সমাজের একটা বিশেষ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে প্রযুক্ত হইত। এখন Esq. এর ব্যবহার বিরল” (বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ১৯৫০: ৩২)।
দৈবচক্র আর ঘটনাচক্র কথার অর্থ এক। ডক্টর রাজীব হুমায়ুনের মতে- যিনি দৈবে অথবা দেব-দেবতা বিশ্বাস করেন না তিনি দৈবচক্র ব্যবহার না করে সচেতনভাবে) ব্যবহার করেন ঘটনাচক্র।
(আ) দুর্গাপূজা প্রসঙ্গেঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাকেন্দ্রিক দুর্গাপূজা এবং সম্পর্কিত শব্দসমূহ হচ্ছে দুর্গা, দুর্গাপ্রতিমা, দশভুজা, তৃনয়নী, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী, কলাবউ, নবপত্রিকা স্নান, বাসন্তী পূজা, শারদীয়া পূজা ইত্যাদি। দুর্গাপূজার ভাষাতাত্ত্বিক গঠন নিয়ে একাধিক মত প্রচলিত।
(১) দুর্গ নামের এক অসুরকে বধ করেছিলেন বলে নাম হয়েছে দুর্গা। অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক গঠন দুর্গ+আ = দুর্গ।
(২) দুর্গা নামের আসল অর্থ ছিল দূর্গম স্থানের অধিষ্ঠাত্রী। পরে অর্থ হয়েছে দুর্গে অর্থাৎ সঙ্কটে ত্রানকর্তী। (শিশু বিশ্বকোষ, ২৫৭; তৃতীয় খণ্ড)
(৩) দুর্গতিনাশিনী বলে দুর্গা। অর্থাৎ দুর্গতি বা কষ্ট থেকে যিনি মানুষকে মুক্তি দেন।
(৪) দুর্গার এক নাম দশভুজা। ভাষাতাত্ত্বিক গঠন দশ+ভুজ (হাত)+আ।
(৫) দুর্গার তিনটি চোখ বলে তিনি ত্রিনয়নী । অর্থাৎ গঠনঃ ত্রি+নয়ন+ঈ।
৬) দুর্গার বাহন সিংহ। এজন্য তিনি সিংহবাহিনী। গঠনঃ সিংহ + বাহন (বহন থেকে বাহন) + ঈ ।
(৭) দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। এজন্য তার নাম মহিষমর্দিনী। গঠনঃ মহিষ+মৰ্দন+ঈ। মহিষমর্দিনী শব্দের অসুর বর্জিত হয়েছে।
(৮) দুর্গার আরেক নাম পার্বতী। পর্বত কন্যা বলে তিনি পার্বতী। গঠনঃ পর্বত+ঈ= পার্বতী। গুণবৃদ্ধির সূত্রানুসারে পর্বতের প হয়েছে পা (পা))।
(৯) শরৎকালে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে দুর্গাপূজার নাম শারদীয়া পূজা। শারদীয়া শব্দের গঠনঃ শরৎ+ঈয়+আ = শারদীয়া। প্রথম অক্ষরের ‘শ’ গুণবৃদ্ধির ফলে ‘শা’ হয়েছে (শশা)। ঈ বদ্ধরূপমূলের ঈ এর প্রভাব শরৎ এর ‘হু’ ‘দ’ এ পরিণত হয়েছে।
(১০) দুর্গাপূজা কেন্দ্রিক একটি শব্দ নবপত্রিকা স্নান। অধিকাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ধারণা নবপত্রিকায় স্নান মানে নতুন ফল পাতার স্নান। আসলে এটি নয়টি ফল পাতার স্নান। এ নয়টি ফলপাতা হচ্ছে- কলা, ডালিম, ধান, হলুদ, মানকচু, কচু, বেল ইত্যাদি। কদলী দাড়িমী ধানাং হরিদ্রা মানকং, কচুঃ বিন্ধা শোকে জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নরপত্রিকাঃ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৬, ১১৭৭; ১ম খণ্ড ) ।
কালী ও প্রাসঙ্গিক শব্দঃ কালী, কালীদেবী, দশমহাবিদ্যা, সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, শশ্মানকালী, মহাকালী এবং আরেকটি জনপ্রিয় নাম শ্যামা। শ্যামা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। বাঙালি প্রিয় সঙ্গীত শ্যামাসঙ্গীত। আবার শ্যামাসঙ্গীতের অন্যতম স্রষ্টা রাম প্রসাদের নামানুসারে আরেকটি জনপ্রিয় বাংলা শব্দ সৃষ্টি হয়েছে রামপ্রসাদী।
শ্যামাসঙ্গীত আর রামপ্রসাদী এখন প্রায় সমার্থক। কালীর চার হাতে চারটি অস্ত্র। এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে চারটি শব্দ। কালীর গলায় নরমুণ্ডের মালা সেজন্য হয়তো কালীর আরেকটি
নাম নৃমুণ্ডমালিনী। কালীর সাথে সম্পর্কিত অন্য শব্দসমূহ হচেছ কালীমন্দির, কালী বাড়ি, কালীতলা, কালীঘাট, কালীগাছ প্রভৃতি। বাংলাদেশের সন্দ্বীপসহ বিভিন্ন স্থানে যে বটগাছের তলায় কালীপূজা হয় সে বটগাছকে বলা হয় কালীগাছ।
(ই) সরস্বতী ও প্রাসঙ্গিক শব্দঃ সরস্বতী বিদ্যাদেবী। এজন্য সরস্বতী এক নাম বাগদেবী। বাগদেবীর শব্দের গঠন নিম্নরূপঃ বাক্ + দেবী বাগদেবী। বাক্ শব্দের ‘ক’ দেবী শব্দের ‘দ’ এর প্রভাবে ‘গ’ তে পরিণত হয়েছে। সরস্বতীর হাতে আছে বীণা তাই তিনি বীণাপাণি। শব্দের গঠনঃ বীণাপাণি (হাত) = মিশ্রশব্দ। সরস্বতী শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আগেই প্রদান করা হয়েছে।
(ঈ) লক্ষ্মী সম্পর্কিত শব্দঃ লক্ষ্মী সম্পদের দেবী। প্রাসঙ্গিক শব্দাবলী নিম্নরূপঃ লক্ষ্মীপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, ভাদুই লক্ষ্মীপূজা, পৌষ লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি। দেবীলক্ষ্মীর অনেক নাম কমলা, কমলালয়া, পদ্মা, পদ্মাসেনা, পদ্মালয়া ইত্যাদি। বাংলায় দুটি ঘরোয়া শব্দ অলক্ষ্মী, লক্ষী ছাড়া। যার সাথে লক্ষ্মী নেই সে অলক্ষ্মী এবং যাকে লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে সে লক্ষ্মীছাড়া। আর এ শব্দ দুটির সোজা অর্থ সম্পদহীন দরিদ্র ব্যক্তি।

৩. হিন্দু ধর্ম ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা
হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে ও আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক অসংখ্য শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীপাবলী বা দেওয়ালি, জন্মাষ্টমী, রামায়ণ, মনসা, মনসামঙ্গল, কুরুক্ষেত্র, অন্নদামঙ্গল, অন্নপূর্ণা, দেবদাসী, লঙ্কাকাণ্ড, উল্টোরথ গঙ্গাযাত্রা, কুশপুত্তলিকা, আদ্যশ্রাদ্ধ, কৌলিন্য প্রথা, বৈষ্ণবধর্ম, গৌরচন্দ্রিকা ও আরো অসংখ্য শব্দ।
অভিসন্দর্ভের কথা বিবেচনা করে এখানে সীমিত পরিসরে শব্দগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি শব্দ, শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষিত হচ্ছে। এখানে বলা প্রয়োজন হিন্দু দেব দেবীদের আচার অনুষ্ঠানের জন্ম বাঙালির জীবন আচার তথ্য সংস্কৃতি চিন্তার সাথে সম্পর্কিত।
দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছে সকল প্রকারের দূর্গতি থেকে মুক্তিলাভের আশায়। লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মী পূজার মূলে রয়েছে সম্পদের আকাঙ্খা। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর জন্ম হয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে। চাঁদ সওদাগরের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও জন্ম হয়েছে সর্পদেবী মনসার সাপের দংশন থেকে মুক্তি লাভের আশায় বাঙালি মানস জন্ম দিয়েছে মনসাদেবীর।
দিল্লীর কাছাকাছি গিয়ে বাঙালি উচ্চারণে কেউ যদি কুরুক্ষেত্র দেখতে চান তাহলে তাকে কেউ দেখিয়ে দিতে পারবেন না। কুরুক্ষেত্র শব্দটির সঠিক ও মূল উচ্চারণ কুরুখষেরা। ‘ক্ষ’ যেহেতু বাঙালি উচ্চারণে ক ষ এর বদলে ক
খ উচ্চারিত হয়। সেজন্য কুরুখষেরা হয়েছে কুরুক্ষেত্র ।
বাংলাদেশে মাঝে মাঝেই কুশপুত্তলিকা দাহ করতে দেখা যায়। ‘কুশ’ শব্দের মূল অর্থ এক জাতীয় ঘাস। পুরলিকা শব্দের পরিবর্তিত রূপ পুতুল। আগের দিনে কারো মৃতদেহ না পাওয়া গেলে বার বছর পর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হতো। আজকালে জীবন্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হাতের নাগালে না পাওয়া গেলে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।
এ প্রসঙ্গে আরেকটি শব্দ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শব্দটি হচ্ছে অতিশ্রুত ‘সতী দাহ প্রথা = সতীদাহ প্রথা। সতী নারীকে দাহ করার কথা বললে ভবিষ্যতের পাঠক হয়তো এ শব্দের মূল অর্থ বুঝতে পারবেন না। সতীদাহের পেছনে লুকিয়ে আছে হিন্দু শাস্ত্র মতে স্বামীর মৃত্যুর পর এক বা একাধিক স্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারবার ইতিহাস।
ঘ. বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মকেন্দ্রিক শব্দ
(১) বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্রিক শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধদেব, সিদ্ধার্থ, বোধিবৃক্ষ, বৌদ্ধধর্ম, ত্রিপিটক, নির্বান, মহাথেরো, ভিক্ষু, ভান্ডে, প্যাগোডা, চৈতা,
বিহার, শালবন বিহার, বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, বৌদ্ধপূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, প্রবারণা, জাতক, অপালি ইত্যাদি।
(২) খ্রিস্টধর্মকেন্দ্রিক শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ গড়, যিশু, যিশুখ্রিস্ট, ফানার, পাদ্রী, নান, গির্জা, চার্চ, ক্রিসমাসড়ে, বড়দিন, মরিয়ম, মেরি, ক্যাথলিক, প্রটেস্টান, ওল্ড টেষ্টামেন্ট, নিউ টেষ্টামেন্ট, খ্রিস্টান, বাইবেল, ফিরিঙ্গি ইত্যাদি।
ঙ. ধর্মকেন্দ্রিক জোড়া শব্দ
বিভিন্ন ধর্ম সহাবস্থানের কারণে ধর্মকেন্দ্রিক জোড়া শব্দ বা একই ধারণার
(Concept) জন্য বাংলায় একাধিক শব্দের প্রচলন রয়েছে।
(১) ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত জোড়া শব্দ
ধারণা
প্রার্থনা
ধর্মীয় উপবাস
আরবি প্রভাবিত
আল্লাহ
সালাত
সিয়াম / সিয়াম সাধনা
ফারসি প্রভাবিত
খোদা
নামায়
রোয়া
২) ইসলাম ও হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক জোড়া শব্দ। ধারণা মুসলিম ব্যবহৃত আরবি ফারসি প্রভাবিত আল্লাহ/ খোলা বেহেশত
পরকালের সুখের আবাস
হিন্দু ব্যবহৃত সংস্কৃত প্রভাবিত
স্রষ্টা
ঈশ্বর/ভগবান
পরকালের শাস্তিপ্রাপ্তদের স্থান জাহান্নাম / দোজখ
স্বর্গ
নরক
এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সমাজভাষাবিজ্ঞানের গবেষক রাজীব হুমায়ুন (সমাজভাষাবিজ্ঞান;
চ. হিন্দুয়ানি বাংলা বনাম মুসলমানি বাংলা
সৈয়দ সুলতান, মোজাম্মিল এবং আব্দুল হাকিম প্রমুখের আমল থেকে অর্থাৎ পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতক থেকে মুসলমানি বাংলা, হিন্দুয়ানি বাংলা, দোভাষী বাংলা, বিদ্যাসাগরী বাংলা, আলালী বাংলা নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক ও গবেষণা হয়েছে। এ বিতর্কের অসারতা প্রমানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেকেই লিখেছেন।
বাংলা ধর্মকেন্দ্রিক মিশ্র শব্দের ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখিয়েছেন ডক্টর রাজীব হুমায়ুন। তাঁর মতে জলোচ্ছ্বাস শব্দের জল সম্পর্কে সচেতন নন অনেক মুসলমান। অন্যদিকে পানসে বা পাস্তা শব্দের পানি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন নন অনেক হিন্দু। (রাজীব হুমায়ুন: ২০০১: ৭৭)। Climate প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বেতার, টেলিভিশনে আবহাওয়া শব্দের ব্যবহারে অনিচ্ছার কারণে মাঝে মাঝে ‘জলহাওয়া’ ব্যবহার করতে শোনা যায়।
জল শব্দটি বাংলায় প্রচলিত হলেও হাওয়া শব্দটির আরবি ফারসির উৎস সম্পর্কে অনেকেই অসচেতন। বাংলাদেশেও এরকম প্রবণতা মাঝে মাঝে লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের অনেকেই আচার্য, উপাচার্য ব্যবহার করতে চান না।
কিন্তু তারা অনায়াসে ব্যবহার করেন বহু দূরের বিদেশি ইংরেজদের ব্যবহৃত চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর শব্দ দুটি। গরিব এবং খুন শব্দকে তাড়াবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক লেখক-সাংবাদিক চেষ্টা চালিয়েছেন বহুবার। কিন্তু কিছুতেই বাংলার গরিবদের সংখ্যা এবং সন্ত্রাসীদের খুনাখুনি কমছে না।