বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের জগতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এক অনন্য নাম। তাঁর রচনা শুধু সময়ের দিক থেকে নয়, বরং চিন্তার গভীরতা, চরিত্রচিত্রণের সূক্ষ্মতা এবং সমাজ-দর্শনের স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা দিয়ে পাঠককে মুগ্ধ করে। ‘নয়নচারা’ গল্পগ্রন্থের একই নামের গল্পটি সেই কাহিনীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মহান বঙ্গদুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত। এই গল্পে শৈল্পিক কল্পনাশক্তি এবং বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতার মিলনে মানুষের অভ্যন্তরীণ মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিন্যাস ফুটে উঠেছে। শহরের কঠোর বাস্তবতা এবং গ্রামের স্বপ্নময় স্মৃতির মধ্য দিয়ে ভাসমান কেন্দ্রীয় চরিত্র আমুর দৃষ্টিকোণ পাঠককে এক গভীর অভিজ্ঞতায় নিমগ্ন করে। গল্পের ভৌতিক ও রূপকথার সমন্বয়, শহরের দুঃখী জীবন এবং গ্রামের মধুর স্মৃতির প্রতিসম্প্রতিক চিত্রায়ণ এই কাহিনীর মূল আকর্ষণ।
নয়নচারা ছোটগল্প
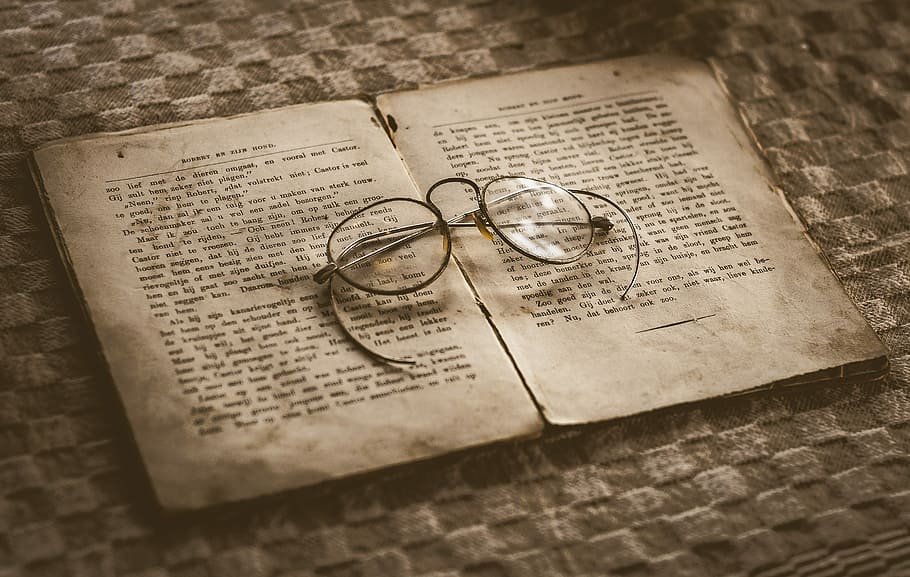
নয়নচারা ছোটগল্প
লেখক-পরিচিতি
১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্, মাতা নাসিম আরা খাতুন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সহায়ক পারিবারিক পরিএগুলে অতিবাহিত হয় বাংলা সাহিত্যের এই অসামান্য শিল্পীর শৈশব-জীবন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পিতৃ ও মাতৃ উভয় পরিবারই ছিলো ধনে-মানে-জ্ঞানে-রুচিতে সম্ভ্রান্ত। পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির এম.এ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা।
মাতামহ মৌলবী আবদুল খালেক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে স্নাতক হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন বলে ওয়ালীউল্লাহ্র সমগ্র স্কুলজীবন কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যায়তনে কেন্দ্ৰীভূত থাকেনি। ১৯৩৯ সনে তিনি কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পূর্বে পিতার চাকুরি-সূত্রে তিনি মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফেনি, চিনসুরা, হুগলি ও সাতক্ষীরা স্কুলে পড়াশুনা করেছেন।
ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দেই ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্। ঐ কলেজের ম্যাগাজিনেই লেখক ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম আবির্ভাব। আই.এ পাশ করে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য তিনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন এবং ঐ কলেজ থেকে ১৯৪৩ সনে ডিসটিংশনসহ বি.এ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে এম.এ শ্রেণীতে ভর্তি হন।
১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পিতার জীবনাবসানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত থাকলেও এ-সময় ওয়ালীউল্লাহ্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে, পেশাজীবনে প্রবেশের কারণে। পেশাগত দায়িত্বপালনের পাশাপাশি এ-পর্যায় থেকেই মূলত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৫ সনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে যোগদান করেন।
ঐ বছরই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস বিষয়ক ত্রিমাসিক ইংরেজি পত্রিকা ‘কনটেমপোরারি’। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের পর ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকার চাকুরি পরিত্যাগ করে ‘রেডিও পাকিস্তান’ ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা- সম্পাদক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পদোন্নতি পেয়ে ‘রেডিও পাকিস্তান’ করাচি কেন্দ্রে বার্তা-সম্পাদক পদে যোগ দেন।
১৯৫১ সনে পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় ‘প্রেস অ্যাটাশে’ পদে নিয়োগ দেয়া হয় তাঁকে। ১৯৫২ সনে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে তাঁকে বদলি করা হয়। ১৯৫৪ সনের অক্টোবরে সিডনি থেকে তাঁকে ঢাকায় আঞ্চলিক তথ্য-অফিসে তথ্য অফিসার পদে বদলি করা হয়। ১৯৫৬ সনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জাকার্তায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য-পরিচালক পদে স্থানান্তরিত হন।
কিন্তু তথ্য-পরিচালকের পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাঁর এ চাকুরি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ফলে ১৯৫৭ সনে জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-অ্যাটাশে পদে নিয়োগ দেয়া হয় তাঁকে। ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসনামলে তাঁকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে এনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করে রাখা হয়। আবার ১৯৫৯ সনে প্রথমে লন্ডনে এবং পরে বন্-এ প্রেস-অ্যাটাশে পদে কিছুকাল কাজ করেন ওয়ালীউল্লাহ্।
১৯৬০ সনে ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন তিনি। ১৯৬১ সনে পাশ্চাত্যের শিল্প-সাহিত্য- সংস্কৃতির তীর্থ-নগরী প্যারিসে বদলি করা হয় তাঁকে। প্যারিসে দীর্ঘবাস কালে ১৯৬৭ সনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পি-৫ গ্রেডে ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট পদে প্যারিস- অফিসেই যোগদান করেন। ১৯৭০ সনের ৩১ ডিসেম্বর ইউনেস্কোর সঙ্গে তাঁর চুক্তি ভিত্তিক চাকুরির মেয়াদ শেষ হলে ইসলামাবাদ বদলির সরকারি সিদ্ধান্ত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রত্যাখান করেন।
অতঃপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থসংগ্রহে আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন তিনি। ১৯৫৩ সনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ফরাসি বংশোদ্ভূত অ্যান-মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবো-র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পূর্বেই মাদাম অ্যান-তিবো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন ও আজিজা মোসাম্মাৎ নাসরিন নাম গ্রহণ করেন।
বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিক শিল্পরীতির প্রবক্তা, রাজনীতি ও সময় সচেতন কথাশিল্পী ও নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যিক-জীবনের স্ফূর্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ‘৪৩-এর দুর্ভিক্ষপীড়িত কলকাতায়। তবে তাঁর প্রথম রচনা ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ প্রকাশিত হয় Dacca Intermediate College Annual – এ।
বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রবক্তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কথাসাহিত্যের দুই শাখা উপন্যাস ও গল্প এবং নাট্য রচনায় সমান দক্ষ।
তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস-নাটক বাংলাদেশের সাহিত্যকে উন্নীত করেছে বিশ্বমানে। দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড ঔপন্যাসিক দস্তয়ে ভস্কি এবং দার্শনিক-ঔপন্যাসিক জাঁ পল সাত্রে প্রচারিত অস্তিত্ববাদী দর্শন এবং আধুনিক প্রকাশবাদী-প্রতীতিবাদী ও পরবাস্তববাদী শিল্পপ্রকরণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সমগ্র সাহিত্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। জীবনের একটি বৃহৎ সময় প্রবাসে কাটালেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সকল রচনারই পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে বাংলাদেশের দেশ-কাল- সমাজ-জীবন।
১৯৭১ সনের ১০ অক্টোবর মধ্যরাতে ফ্রান্সের প্যারিস নগরের উপকণ্ঠে নিজের ফ্ল্যাটবাড়িতে পাঠরত অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে সৈয়দ ওয়ালীউলা জীবনাবসান ঘটে।
রচনা-পরিচিতি
নয়নচারা গল্পগ্রন্থের নাম-গল্প ‘নয়নচারা’। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম গ্রন্থ ‘নয়নচারা’ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৫১) কলকাতার পূৰ্ব্বাশা লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে সংকলিত আটটি গল্পের প্রথম গল্প ‘নয়নচারা’। গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বে ‘নয়নচারা’ সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূৰ্ব্বাশ মাসিক পত্রে মুদ্রিত হয়।
‘নয়নচারা’ গল্পটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দের (১৯৪৩ খ্রি:) ‘The Great Bengal Famine’ বা মহামন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। গল্পকারের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ এবং কেন্দ্রিয় চরিত্র আমুর অবচেতন মনের কথকতার সংমিশ্রণ ‘নয়নচারা’র গঠনশৈলীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রান্ত। সর্বজ্ঞ লেখকের বহির্বাস্তব এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র আমুর অন্তর্বাস্তবতানিষ্ঠ বর্ণনা ও অনুভূতিপুঞ্জ এক স্বকীয় গদ্যকলায় বিন্যস্ত হয়েছে গল্পটিতে।
দুর্ভিক্ষপীড়িত অন্নহারা শহরমুখী মানুষের এই কাহিনীর ভিত্তি দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধশাসিত দেশকালের মৃত্তিকায় প্রোথিত। গল্পটির স্থানিকপট কলকাতা মহানগরীকে উপলক্ষ করে নির্মিত হলেও, আমুর অবচেতন মনের অনুষঙ্গে ময়ুরাক্ষী নদীর তীরবর্তী গ্রামীণ জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।
‘নয়নচারা’ গল্পে সর্বজ্ঞ লেখকের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমুর চেতন-অবচেতন মনোলোকই মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। তার চেতনা-শাসিত মনোলোক উন্মোচনে গল্পকার ব্যবহার করেছেন পরাবাস্তববাদী শিল্পরীতি। আমুর চেতনার অনুষঙ্গে স্বপ্নময় উলম্ফনধর্মী চিত্র সমাহার যোজনায় ব্যবহৃত প্রাতিস্বিক গদ্য ‘নয়নচারা’ ও তার সৃজয়িতার গৌরব।
মূলপাঠ
ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী : রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলে ডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মত মৃদু-মৃদু জ্বলে।
তবে, ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে : ময়ুরাক্ষী। কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া। যে হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে?
ফুটপাথে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেরেছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে – – মৃত্যুর মত নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নামে তন্দ্রার, এবং যদিবা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয় দেহে : মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কল্পনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনচে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলেডিঙিগুলোর পানে চেয়ে ভাবচে।
ভাবচে যে এরই মধ্যে হয়তো বা ডিঙির খোদল ভরে উঠেচে বড় বড় চকচকে মাছে — যে চকচকে মাছ আগামী কাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারী করে তুলবে জেলেদের ট্যাক। আর হয়তো বা – – কী হয়তো বা ?
কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ খ খ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামচে না। তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়। কাশে, কখনো বা ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, অথচ ঘুম লেগে থাকে জোঁকের মত। ভুতনির ভাই ভুতো কাশে না বটে তবে তার গলায় কেমন ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় একটানা, যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলেচে যে চলেচে-ই।
তাছাড়া সব শান্ত, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, আর জমাট বাঁধা ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মত দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লঙ্খ ।
ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠলো বলে আমুর মনের কুয়াশা কাটলো। সে ভরা চোখে তাকালো। ওপারের পানে – তারার পানে এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবলো, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখতো? কিন্তু সে তারাগুলোর নিচে ছিলো ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য, আর ময়ূরাক্ষী।
আর এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েচে শুধু হিংসাবিদ্বেষ-নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা। কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কি যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে – । কিন্তু যা এসেছিলো, মুহূর্তে তা সব শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেলো। কিছু নেই …। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করচে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ-ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার।
ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহুদূরে কোথায় গো? যেখানে শাস্তি – সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কী বিস্তৃত বালুচরের শাস্তি? তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। নয়নচারা ছোটগল্প মন্থরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসচে গলি দিয়ে, এবং নদীর মত প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন এলো তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখলো যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলচে, আর সে চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতায় ও ক্রোধে রক্তবর্ণ।
হয়তোবা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয় তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলচে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই : ভয় করে না একটু-ও : বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমান।
তাছাড়া, রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটি বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলো-রেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েচে, সে- আলো রেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুলচে না তো যেন হাসচে: আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায় – তখন পথ চলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোন অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসচে।
কিন্তু কেন হাসবে? দীর্ঘ-উজ্জ্বল সে-রেখাকে তার ভয় নেই? জানেনা সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি – – অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে – কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক আলাদা দুনিয়ায় হাসুক কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ দুনিয়ায় – যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, সে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না – দেবে না।
তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসচে, শূন্যে ভাসতে ভাসতে যেন এগিয়ে আচে ক্রমশ, এসে, কী আশ্চর্য, আলোরেখাটাও পেরিয়ে গেলো নির্ভয়ে, এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে-রেখা বাধা দিলো না তাকে। মৃতগতির-পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নামলো কুয়াশা আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নামলো। পরাজয় মেনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি । রোদদগ্ধ দিন খরখর করে।
আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা : শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। (এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা।) তবু ভালো।
ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কেমলতা, সে চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। নয়নচারা ছোটগল্প এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভংঙ্কর চোখ ধক্কক্ করে জ্বলচে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাড়ি কলা ঝুলচে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়।
ওগুলো কলা নয় তো, যেন হলুদ রঙা স্বপ্ন ঝুলচে। ঝুলচে দেখে ভয় করে – – নিচে কাদায় ছিঁড়ে পড়বে কী হঠাৎ? তবু, শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন ঊর্ধ্বপানে মুখ করে কেঁদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারা গাঁ?
লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্চে : রক্ত ছুটচে। যেমন করিম মিয়ার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিলো রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা শাদা, এত শাদা যে মনটা হঠাৎ নহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় রাজপথে ভাসমান হয়ে পড়বার জন্যে খাঁ খাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেলো রক্ত ঝকিয়ে। কিন্তু একটা কথা : ও কী ভেবেচে যে তার মাথায় সাজানো চুল তারই? আমু কী জানে না – – আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল ।
কিন্তু পথে কতো কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অগুনতি মাথা; কোন সে অজ্ঞাত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেচে শুধু ধানখেতে, হাওয়ায় দোলানো ধানের খেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে আর এতে কত তফাত। মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর আর দেহের সাথে জমির কোন যোগাযোগ নেই, যে হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্পমান, সে হাওয়াও দিগন্ত থেকে ওঠে আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ হাওয়া নয় : এ-হাওয়াকে সে চেনে না।
অসহ্য রোদ। গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কি রকম কথা : ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসচে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরো বিরক্তিকর – এ কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোন লোক নেই। এখানে ইটের দেশে তো কেউ নেই-ই, তার দেশের যারা বা আছে তারাও মন হারিয়েচে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েচে অন্ধ চোখে চেয়ে। তবু যাক, ভুতনি আসচে দেখা গেলো।
কী রে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলে না, তার চোখ শুধু ড্যাব ড্যাব করচে, আর গরম হাওয়ায় জটা পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করচে। কিন্তু কী রে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পমান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললে ভ্যাঁ করে। নয়নচারা ছোটগল্প কেউ দিলো না বুঝি, পেট বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েচে কী জানিস, কোত্থেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে ছিটাতে এসে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে গেলো, তার মাথায় আমাদের সেই ঝিরার মাথার চুল – তেমনি ঘন, তেমনি কালো…।
আর তার গলার নিচেটা । ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মত লেগে রয়েচে। থাক সে কথা। কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি? ভুতনি, ওরে ভুতনি? কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করলো। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোন নতুন কথা নয় পুরোনো কথা শুধু আবার বলা হলো।
সে মরেচে, ও মরেচে; কে মরেচে বা মরচে সেটা কোন প্রশ্ন নয়, আর মরচে মরেচে কথা দুরঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তায় দুধারের সারি-সারি বাড়ি — যে বাড়িগুলো অদ্ভূতভাবে অচেনা, অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোচে অবশ্য রয়েচে। ভুতনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেলো। কাশি থামলে ভুতনি হঠাৎ বললে, পয়সা? তার পয়সার কথা-ই যেন শুধোচ্চে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন?
ভুতনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করচে, আর কিছু কিছু জ্বলচে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতনি আরো কাঁদলো, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে আমুর চোখ রাজপথে ভাসমান জ্বলে উঠলো। চোখ যখন জ্বলে উঠলো তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ : একটা বিদ্রোহ – অভিমান ধাঁ ধাঁ করে জ্বলে উঠলো সারা দেহময়। তাতে তবু কেমন যেন প্রতিহিংসার উচ্ছ্বলন্ত উপশম ।
একটা ক্ষুরধার সন্ধে হয়ে উঠচে। বহু অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে আমু জানলে যে ও-পথগুলো পরের জন্যে, তার জন্য নয়। রূপকথার দানবের মত শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপচে। কোন সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ-উদগ্র ব্যস্ততা? সে গুহা কী ক্ষুধার? এবং সে-গুহায় কী স্তূপীকৃত হয়ে রয়েচে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তুপ? কত বৃহৎ সে গুহা?
অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে ধীরে কথা কয়ে উঠচে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ-বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠছে তা। নয়নচারা ছোটগল্প কী কইচে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে-অস্পষ্টতা অতি উগ্র : মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হলো : রূপকথার সন্ধ্যা-ও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেচো?
কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটবো, চেটে চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে আকাশ দিয়ে। – কে তুমি, তুমি কে? আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মত। সে ক্ষমা চায় : শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে-ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করেচে, এবং তাই সে ক্ষমতা চায় : দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক।
চারধারে তো রাত্রির ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ, শুনবে না কেউ। ওধারে কুকুরে-কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেচে। মনের এ পবিত্র সান্ত্বনায় সে কোলাহলের তীক্ষ্ম আওয়াজ অসহনীয় মনে হলো বলে হঠাৎ আমু দূর দূর বলে চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর জানলো যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়। অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়। কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে-বাইরে মানুষ।
সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠে পড়লো, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধানে যেন তাকালো রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দুপাশের স্বপ্নালোকিত জানালাগুলোর পানে। একতলা দোতলা তেতলা – আরো উঁচুতে স্বল্পালোকিত জানালা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে! তুমি কী ওখানে থাক? তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগলো। এবং কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বার্স্ট হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ।
আমু শুনতে পারচে বেশ যে, কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে আচে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেলো তখন তার আঘাতে অন্ধকারে ঢেউ জাগলো, রাজপথে ভাসমান ঢেউগুলো দু-ধারের খোলা-চোখে ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো তার কানে। – মা গো, চাট্টি খেতে দাও – এই পথ, ওই পথ : এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌঁছানো যায় না।
ঘর দেখা গেলে-ও কিছুতেই পৌঁছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা ঝনঝন করে : কিন্তু এধারে কাচ, কাচের এপাশে মাছি আর পথ আর আমু। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটিলোক বাজের মত খাঁইখাই করে তেড়ে এলো। আরে, লোকটি অন্ধ নাকি? মনে মনে আমু হঠাৎ হাসলো একচোট, অন্ধ না হলে অমন করবে কেন? দেখতে পেতো না যে সে মানুষ?

পথে নেমে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিলো শহরের লোকেরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্যে নকল চোখ পরে। দোকানের লোকটি অন্ধ-ই, আর তার চোখে সে নকল চোখ। কিছু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেচে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিলো অমন করে। কিন্তু সে কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কান্ড দেখে, নকল চোখে আর আসল চোখে তফাত নেই কিছু। তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগলো। ময়ূরাক্ষীর তীরে কুয়াশা নেমেচে।
স্তব্ধ দুপুর : শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতাল ঝন ঝন করচে, আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়চে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেচে, আর রাজপথে ভাসমান অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েচে ৷ কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগচে। কী কোলাহল। লোকেরা আসচে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে, তবে নকল চোখ পরা কোন অন্ধ তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না তো খাই খাই করে?
কিন্তু গন্ধটা চমৎকার। তারপর বোশেখ মাসে শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি দেখতে না দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভেতরটা করাল হয়ে উঠলো, আর কাঁপতে থাকলো সে থরথর করে : সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইলো দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে চেঁচিয়ে উঠলো, আরেকজন দ্রুত পায়ে এলো এগিয়ে, এসে হীন ভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগাল দিয়ে উঠলো। এই জন্যেই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিলো।
হঠাৎ সে ক্ষিপ্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর, এবং তারপর চকিতে-ঘটিত বহু ঝড়-ঝাপটার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে পথ ধরলো, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলো : যে লোকটা তাড়া করে এসেছিলো সে-ও যদি ময়রার দোকানের লোকটার মত অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সে-ও অন্ধ, তার ও চোখ নকল ; শহরে এত-এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর।
বস্তুসংক্ষেপ
মহামন্বন্তরে খাদ্যের আশায় বাস্তুত্যাগী মানুষের স্রোত ধরে নয়নচারা গ্রামের আমু শহরে এসেছে। দুর্ভিক্ষের আক্ষরিক অর্থ এই শাহরিক জীবন ও সমাজের এক রূঢ় বাস্তবতা। খাদ্যের অন্বেষণে আমু দিনভর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ক্ষুৎ পিপাসায় অবসন্ন আমু ব্যর্থ মনোরথ হয়েই ফিরে আসে অনিবার্য মৃত্যুমুখী মানুষের স্রোতে। শহর-সভ্যতার নিষ্ঠুর রূপের বিপরীতে ক্ষুধায় অবসন্ন আমুর অবচেতনায় ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী মধুময়-প্রাণময় নয়নচারা গ্রামের স্মৃতির জাগরণ ঘটে বারবার।
শহরবাসী আত্মকেন্দ্রিক মানুষের নিত্য চলাচলে মুখর থাকে রাজপথ; কিন্তু বাস্তুহারা নিরন্ন মানুষের দিকে ভ্রক্ষেপ করার অবসর নেই তাদের। শহরের ইট-কাঠ-প্রস্তরের মতই এরা সব মমতাহীন-প্রাণহীন। নয়নচারা গ্রামে কুকুরের চোখে যে বৈরিতা দেখেছে আমু শহরের মানুষের চোখে লক্ষ্য করেছে সে ঐ বৈরিতা। ময়রার দোকানে মাছি ভন ভন করে। চোখময় পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে দোকানে বিরাজ করে ময়রা। ওধারে একটি দোকানে ক-কাড়ি কলা হলুদ রঙা স্বপ্ন হয়ে ঝোলে।
লালপেড়ে শাড়ি পরা একটি মেয়ে পথচারি আমুকে দুটো পয়সা দিয়ে রক্ত ঝলকিয়ে চলে যায়। মেয়ের মাথার সাজানো চুল মেয়েটিরই কিনা ভেবে সংশয়িত হয়ে পড়ে আমু। তার মনে হয় ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে – 1 -ঝিরার মাথার ঘন চুল । আমুর প্রতিবেশী ভুতনির ভাই ভুতো অনাহারে মারা যায়। ভুতনির কাশির প্রকোপ কমে না। ক্ষুধার্ত ভুতনি শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসে শূন্য হাতে।
‘রক্ত ছিটাতে ছিটাতে দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেলো’ যে মেয়েটি, আমু তার কথা ভুতনির কাছে বলে। মেয়েটির মাথার চুল যে নয়নচারা গ্রামের ঝিদের চুলের মতন ঘন-কালো সে-কথাও নয়নচারা ছোটগল্প বলতে ভোলে না আমু। একদিকে শহরের দৃশ্যমান বাস্তব আর অন্যদিকে স্বপ্নময় অবচেতনময় অন্তর্বাস্তবতানিষ্ঠ নয়নচারা গাঁয়ের ছিন্ন ছিন্ন স্মৃতির সূত্রে আলোড়িত হয়ে ওঠে আমুর মনোলোক।
তবু দুর্ভিক্ষ-তাড়িত আমু ভিক্ষালব্ধ দুটো পয়সা ক্ষুধার্ত ভুতনি হাত পেতে চাইলেও বাস্তবিক কারণেই দিতে পারে না। একটা বিদ্রোহ আর ক্ষুরধার অভিমান ধাঁ ধাঁ করে জ্বলে ওঠে তার সমগ্র দেহে। সন্ধ্যা নামে। বহু অচেনা পথে ঘুরে-ঘুরে আমু বুঝতে পারে ও পথগুলো তার জন্য নয়। নীড়- অভিমুখী মানুষের চলাচলে চঞ্চল শহরের রাস্তাগুলো। আমুর মনে হয় কোন্ সে গুহায় ফিরে যাবার জন্য মানুষের এত উদগ্রতা।
সে গুহায় কী স্তুপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? আমুর ক্ষুধা-অবসন্ন সমস্ত মন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, অনুতপ্ত অপরাধীর মতো নুয়ে পড়ে তার সমস্ত শরীর। অন্নের ভাঁড়ার আগলে নয়নচারা ছোটগল্প আছে রাজপথে ভাসমান যে শক্তিমান, তার কাছে ক্ষমা চায় আমু। দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। ওধারে কুকুরে কুকুরে বিবাদ বেঁধেছে। প্রথমে দূর দূর বলে চেঁচিয়ে উঠলেও পরে সে বুঝতে পারে বিবাদমান কুকুরগুলো আসলে কুকুর নয়, ক্ষুধায় হিংস্র জান্তব মানুষ।
কিন্তু আমু কুকুর নয়, ভেতরে-বাইরে মানুষ। সে ক্ষমা প্রার্থী। অদূরবর্তী সারিবদ্ধ দালানের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে সম্ভাব্য অন্নদাতা শক্তিশালীর অবস্থান রয়েছে কিনা জানতে চায় সে। আমুর পথচলার বিরাম নেই। কাছে পিঠেই ঘরের সমাহার, কিন্তু অনিকেত আমুর পক্ষে ঘরে পৌঁছানো যাবে না কখনো। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে। কাচের ওধার থেকে দেখা যায় মানুষের আনাগোনা খানাপিনা।
কিন্তু কাচের ওপাশে মাছি, পথ আর ক্ষুধার্ত আমুর অবস্থান। রাস্তায় দাঁড়ানোরও উপায় নেই তার। বাজখাঁই গলায় তেড়ে আসা লোক হটিয়ে দেয় মানুষ-আমুকে। আবার শুরু হয় পথচলা। শহরের এই রূঢ় নিষ্ঠুর রূপের বিপরীতে মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত নয়নচারা গ্রামের ছবি জেগে ওঠে আমুর ভাবনায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত নয়নচারার মৃত্যু-গহ্বর অতিক্রম করে এসেছে সে। মৃত্যুহীনতার সদর-রাস্তায় উত্তীর্ণ আমুর এখন আর মৃত্যু-ভয় নেই।
এ পথে ও পথে হাঁটতে-হাঁটতে ভোজন উৎসব-বিলাসী মানুষের তাড়া খেয়েও পথ হারা হয় না আমু। একবার ভাবে যে পথের শেষ নেই, সে পথে চলা নিরর্থক। এই ভেবেই সে পৌঁছে যায় মৃত্যুমুখী মানুষের ভিড়ে কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে আসে আমু। তার মনে হয়, মৃত্যুকে আলিঙ্গনের অপেক্ষায় যারা নিঃশব্দে ধুঁকছে, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। ফলত দ্রুত পা চালিয়ে অবসন্ন মানুষের মৃত্যুপুরী থেকে পালিয়ে আসে আমু। পুনরায় শুরু হয় তার পথ চলা।
অনেক্ষণ পর আমুর খেয়াল হয় যে, সে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে চলেছে। গলার সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠে আসা আর্তনাদ নিজের কাছেই ভয়ঙ্কর শোনালো তার। অবশেষে একটানা ভয়ঙ্কর বীভৎস আর্তনাদে প্রাণ কাঁপলো আবদ্ধ দরজার। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো কে একটা মেয়ে, অতি-আস্তে শান্ত গলায় শুধু বললে — ‘নাও’ ।
কী নেবে আমু? আমু ভাতই চায়। অস্তিত্বকে রক্ষা করে যে ক্ষুধার অন্ন, সে অন্ন ছাড়া আর কিছুর নাম জানে না আমু। ত্রস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে ভাতটুকু নেয়ার মুহূর্তগুলিতে নিস্পলক চোখে বিস্ময়াভিভূত আমু চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। চেনা-চেনা মনে হয় তার মেয়েটিকে। নতুবা চোখ ফেরাতে পারবে না কেন সে? আবিষ্কারের আনন্দে অভিভূত আমু জিজ্ঞাসা করে ‘নয়নচারা গাঁয়ে কী মায়ের বাড়ি?’
স্বভাবতই মেয়েটি কোন উত্তর দেয় না; শুধু কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়মাখা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। শহরের প্রাণহীন রুক্ষতার মাঝেও যে নারী ক্ষুধার্তের হাতে অন্ন ঢেলে দেয়, তার অবয়বে ভঙ্গিমায় আমু প্রত্যক্ষ করে মমতামাখা নয়নচারা গ্রামের মা-ঝিদের অন্নদাত্রী রূপিণী নারী-রূপ !
পাঠোত্তর মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন
১. দেহের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েও জাগ্রত মন নিয়ে কোথায় পরিভ্রমণ করে আমু ?
২. সে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না – – দেবে না।’ কাকে হাসতে দেবে না আমু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।
৩. রাজপথে ভাসমান দুর্ভিক্ষতাড়িত নিরন্ন মানুষের অবস্থা বর্ণনা করুন।
৪. শক্তিশালী কে ? শক্তিশালীর কাছে আমুর ক্ষমা প্রার্থনার হেতু কী?
৫. শহর ও শহরের মানুষ সম্পর্কে আমুর উপলব্ধি বর্ণনা করুন।
৬. আমুর আত্মভাবনার আলোকে নয়নচারা গ্রামের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তর
দুর্ভিক্ষপীড়িত আমু ক্ষুধার অন্নের আশায় গ্রাম পরিত্যাগ করে শরণার্থী হয়েছে শহরে। বাস্তুহারা ক্ষুধার্ত আমু দুমুঠো ভাতের আশায় নির্দয় শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। লঙ্গরখানা থেকে দেয়া অপ্রতুল খাদ্যে ক্ষুধা মেটেনা আমুর। খাদ্যান্বেষণে বৃথাই শহর প্রদক্ষিণ করে অন্যদের মত ক্লান্ত অবসন্ন দেহ আমু ফুটপাতে এলিয়ে পড়ে। অন্যরা ঘুমিয়ে পড়লেও আমুর চোখে ঘুম আসে না। কখনো কখনো তন্দ্রার কুয়াশা নামে তার চোখে।
যদিবা কখনো ঘুম আসে, সে ঘুম তার মনোলোকে ভর করতে পারে না। দেহের ঘুমে আচ্ছন্ন হলেও জাগ্রত মন নিয়ে সে ফেলে আসা স্মৃতিময় নয়নচারা গ্রামে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। ঘনায়মান অন্ধকার রাতে জনশূন্য রাজপথকে প্রিয় ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে ভালো লাগে তার।
মনের চরে যখন আঘাত করে ঘুমের বন্যা তখন তার মনোলোকে কলস্বরা ময়ূরাক্ষী জীবন্ত হয়ে ওঠে, নদীর মধ্যজলে ভাসমান জেলে ডিঙিগুলোর বিন্দু বিন্দু লালচে আলো আশার প্রদীপ হয়ে মৃদু-মৃদু জ্বলে। তার অবচেতনায় ময়ূরাক্ষীর জেলে ডিঙিগুলোর খোদল বড়-বড় চকচকে মাছে পূর্ণ হয়ে যায় ।
শহরের নির্দয়তার বিপরীতে, স্মৃতিময় নিরাপদ নয়নচারা গাঁ আশা ও প্রশান্তির প্রতীক হয়ে বিরাজ করে আমুর মনোলোকে। এ জন্যেই অবসন্ন দেহে ঘুম ভর করলেও অবচেতন অবস্থায় আমুর সংবেদনা নয়নচারা গাঁ-কে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

৪ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা- উত্তর:
উদরে প্রজ্বলিত ক্ষুধার আগুন নিয়ে শহরের রাজপথে ভাসমান আমু অনুধাবন করতে পেরেছে শক্তিহীন জনারণ্যের বিপরীতে খাদ্যের ভাঁড়ার আগলে থাকা শক্তিমানের অস্তিত্ব। ময়রার দোকানে ধাতব মুদ্রার ঝনৎকারে, শোভার জন্য নকল চোখ পরা মানুষের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে শক্তিশালী। মহামন্বন্তরে কৃত্রিম খাদ্য-সংকটের হোতা শহরের বর্ণচোরা শক্তিশালী মানুষ ।
রাতের অন্ধকারে আমু দেখতে পায় শয়তানের প্রজ্বলিত চোখ। আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায় তখন শয়তানের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে হাসির প্রতিমায়। হৃদয়জ ক্রোধে-ঘৃণায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আমুর মন। কালো নদীর ধারে ধারে পড়ে রয়েছে যে-সব মানুষ ভাটির টানে মৃত্যুস্রোতে ভেসে যাবে বলে সে-দুনিয়ায় শয়তানকে কোনো অবস্থাতেই হাসতে দেবে না আমু। কিন্তু আমুর এই আপাত বিদ্রোহ ক্ষুধার পীড়নে ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ে।
সে যদিও বলে ‘কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটবো, চেটে চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে-আকাশ দিয়ে কে তুমি, তুমি কে?’ তবু শেষ অবধি ক্ষুধা অবসন্ন আমুর সমস্ত মনে স্তব্ধতা ভিড় জমায়, অনুতপ্ত অপরাধীর মত নুয়ে পড়ে সে। অসহায় নিরন্ন জনতার প্রতিনিধি আমু নগর-সভ্যতার কূটচালের রহস্য ভেদ করতে পারে না, . কৃত্রিম সংকটের মারণান্তিক রূপের শিকারই হয় কেবল।
এ জন্যেই আমু শক্তিশালীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। সে জানতে পেরেছে শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সেই গর্হিত ন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করা ক্ষমাহীন পাপ। অসহায় আমু উপলব্ধি করে যে সে পাপ করেছে। এই পাপ-মুক্তির জন্যই সে শক্তিশালীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। দুটি ক্ষুধার অন্ন দান করে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। শহরে অনেক মানুষ রয়েছে যারা বাইরের মানুষ অথচ ভেতরে কুকুর।
আমু ভেতরে বাইরে অবিমিশ্র মানুষ। সে- জানে আশেপাশের সারিবদ্ধ-ত্রিতল দ্বিতল দরদালানের স্বপ্নালোকিত জানালাগুলোর ভেতরেই খাদ্যের ভাঁড়ার আগলে থাকা শক্তিশালীর অবস্থান ।
