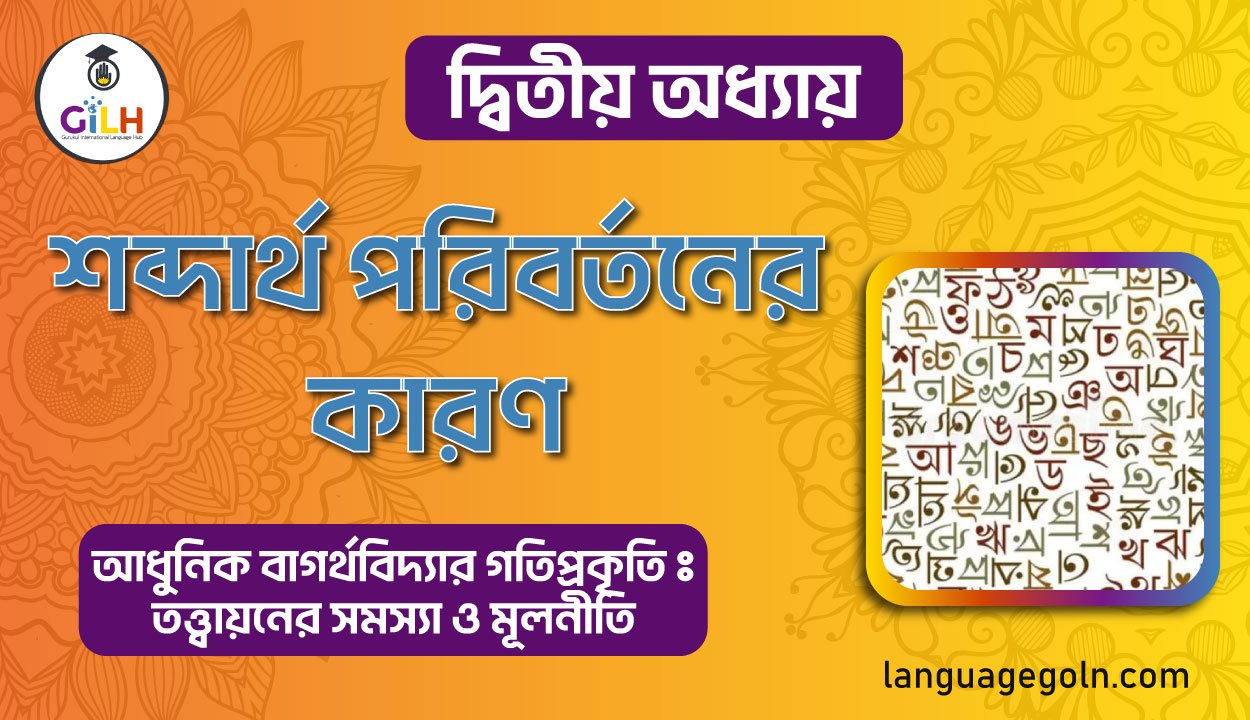আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ
শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ
শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা যেমন বিচিত্র, শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণও তেমনি বহুমুখী । আমরা শব্দার্থ পরিবর্তনের মোটামুটি নয়টি কারণ খুঁজে পাই : (১) কালপ্রভাব, (২) সামাজিক পরিবেশ, (৩) সৌজন্য ও শিষ্টাচার, (৪) অন্ধসংস্কার, (৫) ভাবাবেগ, (৬) অনবধানতা, (৭) সৃজনশীলতা, (৮) অস্পষ্টতা এবং (৯) আলংকারিক প্রয়োগ । নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ।
কালপ্রভাব : সময় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উপর তার চলার ছাপ রেখে যায়। শব্দ এবং অর্থও তার বাইরে নয়। সময় চলে যায়, সময়ের সাথে অনেক শব্দও হারিয়ে যায় অতীতের গর্ভে কিছু থেকে যায় তার চিহ্ন পথের ধুলির মতো । মমতাজ হারিয়ে যায়, তবু কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাজমহল ।
আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে পারি :
একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান, কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন গৌরব ধনমान । শুধু তব অন্তর বেদনা চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ বাসনা ।

কড়ির প্রচলন না থাকলেও এখনো আমরা বলি টাকাকড়ি, পয়সাকড়ি। আমরা সবাই নিজেদের স্বার্থ ষোল আনা চাই, কিন্তু আনা কি আর এখনো আছে ? পৃথিবীর সব শব্দের পরিবর্তনই কালে সম্পাদিত হয়। কালকে তাই আমরা অর্থ পরিবর্তনের কারণ রূপে চিহ্নিত করলেও এটি আসলে অর্থ পরিবর্তনের একটি অনুঘটক ।
সরাসরি এটি পরিবর্তন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না, তবে এর উপস্থিতিতে পরিবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ।
সামাজিক পরিবেশ : সামাজিক পরিবেশ অর্থ পরিবর্তনের কারণ হিসাবে কাজ করতে পারে। আমাদের সমাজে বিবাহিত নর-নারী বাবা-মা বলতে শুধু জনকজননীকে বোঝেন না, শ্বশুর-শ্বাশুরীকেও বোঝেন এবং অনেকে সে অনুযায়ী সম্বোধন করেন। বিদায়ের সময় আমরা কখনোই বলিনা যাও বরং বলি আসো।
অঞ্চল প্রভাবে অর্থের পরিবর্তন হয় । মান বাংলায় ঢোকানো বলতে কোনকিছু কুড়ানো বুঝায়, কিন্তু নোয়াখালী অঞ্চলে এটি কাউকে খোঁজা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সৌজন্য ও শিষ্টাচার: সৌজন্য ও শিষ্টাচারবশতঃ শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে।
কাউকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর সময় বাড়িতে পোলাও-কোর্মার আয়োজন হলেও আমরা বলি ডালভাত রান্না হয়েছে এবং একগাদা ভাতকেও আমরা চারটা ভাত বলতে কুণ্ঠাবোধ করি না। বিশাল অট্রালিকায় বাস করলেও এবং পায়ের ধুলি না থাকলেও আমরা বলি আমার কুটিরে পদধুলি দেবেন।
ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দেয়ার ইচ্ছা থাকলে আমরা সৌজন্য সহকারে বলি মাফ করো। বৈষ্ণবীয় বিনয়ের কথা আমরা অবগত আছি। বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর দাসানুদাস, গুরুর চরনামৃত তাদের কাছে পরম প্রসাদ। মুসলমানী আদবকায়দাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তাদের কাছে অন্যের বাড়ি দৌলতখানা কিন্তু নিজের বাড়ি গরীবখানা। তারা বক্তা হিসাবে আরজি করেন, কিছু শ্রোতা হিসাবে ফরমাশ করেন।
অন্ধসংস্কার : অন্ধসংস্কার হেতু অর্থের নানারূপ পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় । এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছুকে বোঝানোর জন্য প্রচলিত শব্দটি ছাড়া অন্য শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন সন্ধ্যার পর গ্রুপ বলা যাবে না, দোকানীর কাছে গিয়ে বলতে হয় ধোঁয়া । রাত্রি কালে অনেকে সাপ বলেন না, লতা বলেন।
ভয়বশতঃ সুন্দরবনের লোকেরা বাঘকে শেয়াল বলে, আবার অন্যত্র বলে দক্ষিণ রায়। বসন্ত রোগ হলে হিন্দুরা বলে মায়ের দয়া হয়েছে এবং সধবা হিন্দুনারী শাখা খুলে রাখেন না, ঠান্ডা করে রাখেন। ঘরে চাল না থাকলে কেউই বলেন না চাল নেই বলেন চাল বাড়া। ভাঁড়ে মা ভবানী কথাটি মনে হয় এই সংস্কার থেকেই এসেছে । বিশেষ অবস্থায় বিশেষ শব্দ প্রয়োগের নিষেধকে ইংরেজীতে বলা হয় taboo । সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন আমেরিকায় ট্যাবুর কারণে cock এর পরিবর্তে প্রচলিত হয়েছে rooster’

ভাবাবেগ : মানুষের আবেগ বা ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস থেকেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে। ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি ভাবের আতিশয্য থাকলে মানুষ উচ্ছ্বাসপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করে। যেমন মারাত্মক খেলোয়ার, অসম্ভব কথা, অদ্ভুত ছবি, ভীষণ মেধাবী, ভয়ংকর সমস্যা, ফাটাফাটি অবস্থা প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে শব্দের সহাবস্থান ব্যাকরণিক দৃষ্টিতে সন্দেজনক হলেও আবেগের উচ্ছ্বাসে সেগুলো উৎরে যায়।
আমরা বলি দারুন রান্না হয়েছে, দারুন খাওয়া হলো কিন্তু রান্না ও খাওয়া কিভাবে দারুন হয় তা বোধগম্য নয়। খোদার কসম; মা কালীর দিব্যি কিংবা পিটিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো প্রভৃতি কথায় আক্ষরিক অর্থের চেয়ে আবেগাত্মক অর্থটাই প্রধান হয়ে উঠে। প্রেমের বুলি যে ভাবাবেগের বিরাট উৎস্য তা কে না জানে :
তোমার আমার জীবন বীণা এক তারেতে বাঁধা তুমি আমার কৃষ্ণ ওগো, আমি তোমার রাধা ।
অনবধানতা : অসাবধানতা কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ শব্দের নানারকম অপপ্রয়োগ ঘটে এবং অনেক অপপ্রয়োগ কালক্রমে নিয়মবদ্ধ প্রয়োগে পরিণত হয় ।
বাংলা ভাষায় সুতরাং, তথাচ, হঠাৎ প্রভৃতি শব্দ এসেছে সংস্কৃত থেকে অপপ্রয়োগের পথ ধরে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না আমার তাকে নাস্তিক বলি। কিন্তু এর আসল অর্থ ছিল যে দেশাচার মানে না। আগে পাষন্ড বলতে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বোঝাত, কিন্তু এখন পাষন্ড বলতে বুঝায় নিষ্ঠুর।
লোকে বেগমফুলি, শেওড়াফুলি প্রভৃতির সাদৃশ্যে পায়রাফুলিকে এক প্রকার অপরিচিত ফুল বলে মনে করে। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। শব্দটি ইংরেজী pineapple এর অপভ্রংশ । armchair -কে বাংলায় অনেকে আরাম কেদারা বলে থাকেন। chair না হয় কেদারা হলো কিন্তু arm আরাম হবে কেন ? (চেয়ারে হাত বুলালে আরাম পাওয়া যায় সেজনা ?) ইংরেজীতে দেখা যায় অনেকে disinterested (নিরপেক্ষ) কে uninterested (অনাগ্রহী) অর্থে এবং infer (অনুমান করা)-কে imply (ইঙ্গিতে বোঝানো) অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।
অনবধানতা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে পারে। যখন কোন ব্যক্তির আচরণে অনবধানতা চরম পর্যয়ে পৌঁছায় তখন তা একটি মানসিক সমস্যারূপে চিহ্নিত হয়। এই অবস্থায় শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং তা প্রথাগত অর্থকে অবজ্ঞা করে। মেলভিন ম্যাডকস (১৯৭৭ : ২৭) এ ধরনের মানসিক সমস্যাকে বলেন অর্থবোধ লোপ ।
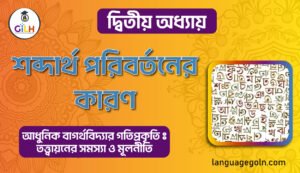
সৃজনশীলতা : অনেক সময় কবি সাহিত্যিকরা নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন অথবা শব্দের উপর নতুন অর্থ প্রযুক্ত করেন। যেমন বারুণী বলতে এক প্রকার মদ বা পশ্চিমণিককে বোঝায়, বিশ্ব শ্রুতিমধুর বলে মধুসুদন একে বরুনা দেবতা)-র স্ত্রী অর্থে প্রয়োগ করেছেন। প্রদোষ শব্দের অর্থ সন্ধ্যা কিন্তু উষাকাল অর্থেও বা ব্যবহার করেছেন
জানালা ও বাতায়নের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ জাল নির্মিত অয়ন’ এই ব্যাসবাকা যোগে জালায়ন শব্দ তৈরী করেছিলেন । সৃজনশীল স্বেচ্ছাচারিতা সবসময় নিম্ননীয় নয়। এভাবে ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হয়ে থাকে । এই প্রসঙ্গে মাইকেলী ধাতুর কথা বিশেষভাবে সারণীয় ।
অস্পষ্টতা : অস্পষ্টতাও অনেক সময় শব্দার্থ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। যেমন বিলাত শব্দের অর্থ বিদেশ । সে থেকে তা ইংল্যান্ড ও আরেকটু ব্যাপকভাবে ইউরোপকে বুঝায়। আবার বিলাতী জিনিষ কালে আমরা প্রধানত ব্রিটিশ প্রবাকে বুঝে থাকি। জাপানী জিনিস, বিলাতী নয়, কিন্তু টমেটোর নাম বিলাতী বেগুণ । বক্তৃতার সময় নেতারা বলে থাকেন ভাইসব কিন্তু সভায় অনেক বোনও উপস্থিত থাকতে পারেন।
ভদ্রলোক বলতে ঠিক কাকে বোঝায় তা স্পষ্ট নয়। ভালো পোষাক পড়লে, টাকা পয়সা থাকলে, শিক্ষিত হলে সে ভদ্রলোক আর লুঙ্গিপাড়া গরীব নিরক্ষর ব্যক্তিটি অভদ্রলোক (কোন অভদ্রোচিত কাজ না করেও)?
আলংকারিক প্রয়োগ : আলংকারিক প্রয়োগ শব্দের অর্থ পরিবর্তনের জন্য অনেকখানি দায়ী করাকে সুন্দর ও শিল্পময় করনা জন্য অলংকারের প্রয়োগ হয়ে থাকে।
অলংকার তাই সাহিত্যসৃষ্টির আবশ্যিক উপাদান । নীচে আমরা রূপক, অনুকল্প, প্রতিরূপক, অতিশয়োক্তি, সরগোতি, সুভাষণ ব্যাঙ্গোক্তি প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর অলংকার নিয়ে আলোচনা করবো ।
রূপক: কোন কিছুর অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য যখন তাকে অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনা করা হয় তখন রূপক সৃষ্টি হয়।
যেমন, আমরা কলি পাহাড়ের পাদদেশ নদীর মুখ রে মাথা এখানে পাহাড়, নদী ও গাছের বিশেষ অংশকে মানুষের প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্যে নামকরণ করেছি, যদিও কড়াকড়ি অর্থে পাহাড়ের পা নেই, নদীর মুখ নেই ও গাছের মাথা নেই। এই ধরনের অর্থের পরিবর্তনকে বৈয়াকরণরা বলেন রূপকাত প্রসারণ।
দুঃখের সমুদ্র, স্মৃতির আকাশ কপতরু প্রভৃতিও রূপকের দৃষ্টান্ত। আকংকারিক পরিভাষায় এখানে উপমেয় উপমানের মধ্যে অভেদসম্পর্ক কম্পিত (দ্রষ্টব্য নরেন বিশ্বাস ১৯৮৮৮৮৪)। নজরুলের কবিতা থেকে রূপকের উদাহরণ দেয়া একটি শুধু বেদনা মানিক আমার মনের মণিকোঠা সেইত আমার বিজন ঘরে দুঃখ রাতের আঁধার ফুটা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা থেকে রপরের আরেকটি উদাহরণ :
বুড়োর মুখটা চাষ করা রৌদ্র পড়া শীত বসন্তের কুঞ্চিত মাঠ আসল যা জীবনের তাগি গলতা ধরেছে লল ।
অনুকল্প : অভিজ্ঞতায় সান্নিধ্য অথবা সাদৃশ্যবশতঃ এক বস্তুর নামকে যখন আরেক বছর নামের স্থাে করা হয় তখন তাকে অনুকল্প বলে । রাণীন্দ্রনাথ পড়লুম নজরুল পড়লুম -এ ধরনের বাক্যে রবীন্দ্রনাথ নামটি দিয়ে বরীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং নজরুল নামটি নিয়ে নকলের সাহিত্য বোঝানো হচ্ছে। আমরা রিক্সাওয়ালাকে
বলি এই কিম্বা বাড়ির ভিতর থেকে মুরগি বিক্রেতাকে ডাক দিই এই মুরগি এখানে আসো। – অনুকল্প প্রভাবের জনাই চামড়া বা ধামাধরা কালে খোশামোদকারী ব্যক্তি, কেউটে বললে অনিকের ব্যক্তি বোঝায়। পায়ের মা দিয়ে যখন পায়ের মলের শব্দ বোঝানো হয় তখনও তাতে অনুরুপ অলংকারের প্রয়োগ ঘটে, যেমন :
কে ঐ যায় তার পারের মল শোনা যায় নিশিরাতে সে কার সাথে যে অভিসারে যায়।
প্রতিরূপক অংশ নিয়ে যখন তাকে অথবা সমগ্র দিয়ে অংশকে বোজানো হয় তখন তাকে প্রতিরূপক বলে । যেমন কালি বললে শুধু কালো কাকে না বুঝে আমরা যে কোন রঙের কালিকে বুঝে ডাকি । বাঈ বললে আমরা বিশেষ নর্তকীকে বুঝে থাকি অথচ মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে বাঈ নারীদের উপাধিমান ।
যখন আমরা ভাত নাই তখন ভারতের সাথে অন্য তরকারীও খাই। যখন চা-চক্রে সামিল হই তখন চায়ের স বিকূট, সিঙ্গারা ( এসবকেই কি টা বলে?) ইত্যাদিও চলে। একইভাবে জনপান মানে আমাদের কাছে শুধু জল বা পানি পান করা নয়, আরো কিছু ।
অতিশয়োক্তি : বর্ণনার আতিশয্যকে অতিশয়োক্তি বলে। নরেন বিশ্বাসের মতে, কবি কল্পনায় যখন বিষ বিষয়ীর দ্বারা প্রাসিত হয় অর্থাৎ উপমানের চরম প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সৃষ্টি হয় অতিশয়োক্তি। যে জলে আগুন ফলে বললে আতিশয়োক্তি হয় কারণ জলের প্রজ্জ্বলন ক্ষমতা নেই। তবু কবি মনে হয় বিশ্বাস করিয়েই ছাড়বেন
সাগরে যে অগ্নি আছে কল্পনা সে নয় চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
– সত্যেন্দ্রনাথ প
অবিশ্বাস করার যো নেই, কারণ
অন্য দেশে অসম্ভব যা পূণ্য ভারতবর্ষে দ প্রায়শ্চিত্ত কর সে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সালোজি সারলোভি হলো মনের নেতিবাচক ভাবকে ভাষার বিশেষ কৌশলে দ্বৈত নেতিবাচক শব্দযোগে প্রকাশ করা। যেমন, সে দেখতে অতটা কুৎসিত নয় বললে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোঝায় সে খুব কুৎসিত । ইংরেজী থেকে একটি উদাহরণ দিই। He’s not the brightest man in the world বললে বোঝায় He’s stupid.
সুভাষণ : রতা পরিহারের জন্য নেতিবাচক প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত কোন শব্দের পরিবর্তে যখন নতুন প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে সুভাষণ বলে। যেমন, বঙ্গ সমাজে দাসীকে আদর করে ডাকা হয় জি পাচককে ডাকা হয় ঠাকুর মারা গেছেন খারাপ শোনায় বলে একে ঘুরিয়ে বলা হয় পরলোকগমন করেছেন, দেহত্যাগ করেছেন দেহরক্ষা করেছেন ইতেকাল করেছেন বর্ণবাদী হয়েছেন, ধরাধাম বা ইহলোক ত্যাগ করেছেন ইত্যাদি । ইংরেজীতেও তেমনি die এর বদলে অনেক সময় নরম করে বলা হয় pass away
ব্যাঙ্গোক্তি শব্দের যে আক্ষরিক অর্থ থাকে কৌশলে তার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করবে বলে ব্যাপোতি যেমন বুদ্ধির ঢেঁকি করো বোঝানো হয় বুদ্ধিহীনকে, মহাবৈদ্য বলে বোঝানো হয় অকর্মণাকে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলে আমরা গালি দেই, অমুক লোকের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র বলে আমরা ব্যঙ্গ করি। যারা মুখের ধোয়া তারাও উত্তম মধ্যম খেয়ে শ্রীঘরে যেতে পারেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ব্যাজোক্তির সন্ধান মিল্লো
অদ্ভুত আঁধার এক নেমেছে এ পৃথিবীতে আজ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা যাদের হাপরো কোন প্রেম নেই প্রীতি নেই করুণার আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া ।