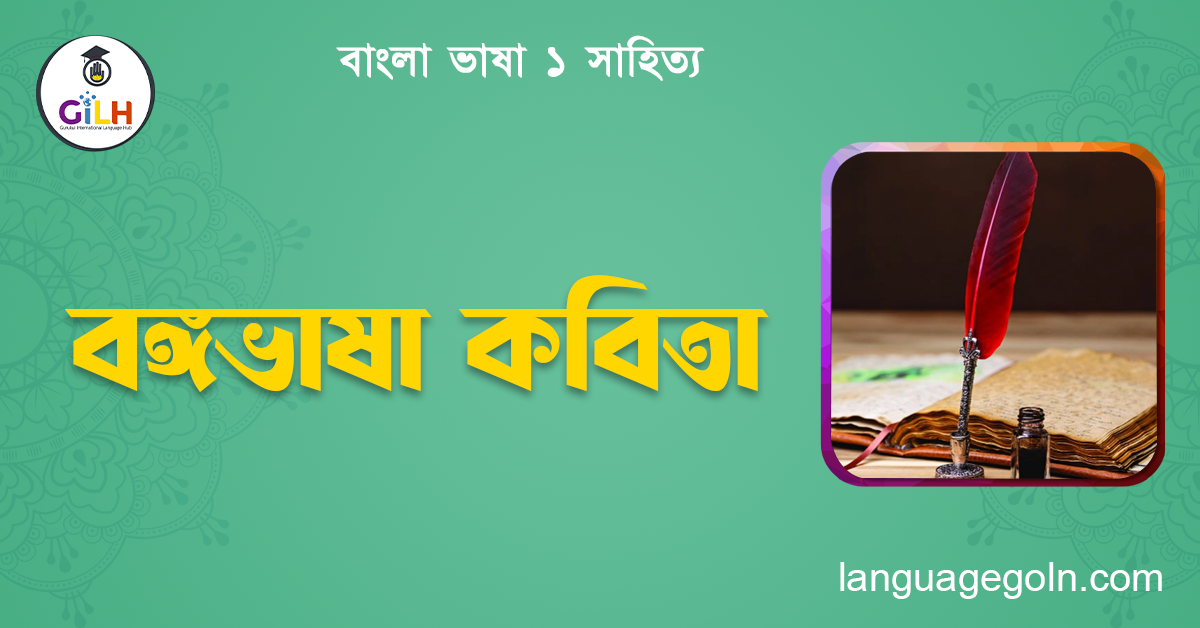বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আত্মাবিষ্কার ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর প্রেমকে কাব্যভাষায় নিবিষ্ট করে রাখেছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত সনেট ‘বঙ্গভাষা’। বিদেশি রীতি ও ভাষার আকর্ষণে নিজস্ব ভাষা অদৃষ্টে ফেলা কাব্যে–প্রবৃত্তিকে কবি এই কবিতায় তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করেছেন; তবু শেষপর্যায় মাতৃভাষার ঐশ্বর্য ও অগণিত রত্ন-সম্পদকে আবিষ্কার করে নিজে-কে ফিরে পেয়েছেন। কবিতাটির অর্থবহ অষ্টক-ষষ্টক বিন্যাস, শিল্পচয়ন ও আন্তরঙ্গ আবেগ পাঠককে মাতৃভাষার প্রতি নতুন রুচি ও গৌরববোধ জাগাতে সহায়ক। আজকের আলোচনায় আমরা কবিতাটির সাহিত্যিক রূপ, মধুসূদনের ভাষাসচেতনতা ও কবিতাটির যুগোপযোগী তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখবো—কেন এই সনেট বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় আবির্ভাব।
বঙ্গভাষা কবিতা

বঙ্গভাষা কবিতা
লেখক-পরিচিতি
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩] বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ধারার প্রবর্তক। অসাধারণ মেধা, সুগভীর পান্ডিত্য ও প্রতিভা নিয়ে তিনি কবিতার মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ রূপরীতি ভেঙে আধুনিক যুগের সূচনা করেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যেও রয়েছে তাঁর ট্র্যাজিডি ও প্রহসন রচনার অসামান্য কৃতিত্ব। তিনি যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।
পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতা জাহ্নবী দেবী। রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন সফল উকিল, উন্নতিশীল বিত্তবান মধ্যবিত্ত। বাল্যকালে মধুসূদন পারিবারিক স্নেহমমতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি মায়ের কাছে পাঠ করেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বাংলা কাব্য।
এর ফলে দেশজ সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর পরিচিতি ঘটে, পরবর্তীকালে এই পরিচয়ই তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাকে করে তোলে স্বদেশের মর্মমূলে প্রোথিত এবং ঐতিহ্যলগ্ন। তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় উপনিবেশ-কলকাতার বর্ণাঢ্য নগর প্রতিবেশে। তৎকালীন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পীঠস্থান কলকাতার চিন্তাচেতনার আলোক, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্যের সংস্পর্শ ও বিলাস-বৈভব তাঁর চিত্তকে করে প্রভাবিত।
গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি প্রায় তের চৌদ্দটি ভাষা আয়ত্ত করে মধুসূদন হয়ে ওঠেন পান্ডিত্য ও রসজ্ঞানে প্রাণবন্ত। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনার প্রয়াস ছিল, ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংরেজি ভাষার বড় কবি হওয়ার বাসনায় তিনি খ্রিষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চার নিদর্শন Captive Ladie, Visions of the Past প্রভৃতি [১৮৪৮-৪৯]।
কিন্তু ১৮৫৮-৬২ সময়পর্বে মধুসূদন বাংলা ভাষায় রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ও নাটকসমূহ। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রবাসজীবনে সৃষ্টি করেন ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য [১৮৬০], মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য [১৮৬০], বীরাঙ্গনাকাব্য [১৮৬১] ইত্যাদি এবং নাটকসমূহ শর্মিষ্ঠা [১৮৫৯], একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (প্রহসন জাতীয় রচনা ১৯৫৯],
পদ্মাবতী [১৯৬০], কৃষ্ণকুমারী [১৯৬১), মায়াকানন ইত্যাদি। মহাকাব্যের ক্ল্যাসিকরীতি, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট, ট্র্যাজেডি, প্রহসন ইত্যাদি বিচিত্র আঙ্গিক প্রবর্তনে মধুসূদন যুগন্ধর প্রতিভা, এসব ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। বিচিত্র জীবনযাপন ও বিপর্যয়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবনকাল। ধর্মান্তরের ফলে পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। মধুসূদন প্রথমে এক ইংরেজ নীলকরের কন্যা রেবেকা ম্যাকটাভিসকে বিবাহ করেন।
পরবর্তী সময়ে এমিলিয়া হেনরিএটা সোফিয়া নামের ফরাসি যুবতীকে পত্নী হিসেবে বরণ করেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই | ১৮৪৮-১৮৫৬] শিক্ষক, সাংবাদিক ও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন, কিন্তু অর্থ-উপার্জনে খুব সফল হননি। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার ফলে তিনি পরিবারসহ দুর্ভোগের সম্মুখীন হন।
জীবনের শেষ প্রান্তে রচনা করেন হেক্টরবধ কাব্য (১৮৭১); ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগাক্রান্ত মধুসূদনের শেষজীবন ছিল দুঃসহ ও দুর্ভাগ্যজনক। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ জুন তিনি পরলোক গমন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিচিত্র প্রতিভা ও প্রথম আধুনিক কবির পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত’, এবং সুরেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত ‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থে।
পাঠ- পরিচিতি
মধুসূদন দত্ত রচিত ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটি ‘চতুৰ্দ্দশপদী কবিতাবলী’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থানকালে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সনেট রচনায় ব্রতী হন, এই রচনাসমূহ ‘চতুৰ্দ্দশপদী কবিতাবলী’ গ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তবে আলোচ্য কবিতাটি প্রথমে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টম্বর-অক্টোবর মাসে ‘কবি- মাতৃভাষা’ নামে লিখিত হয়েছিল, এটি পুণর্লিখিত হয়ে ‘বঙ্গভাষা’ নামে উক্ত গ্রন্থভুক্ত হয়।
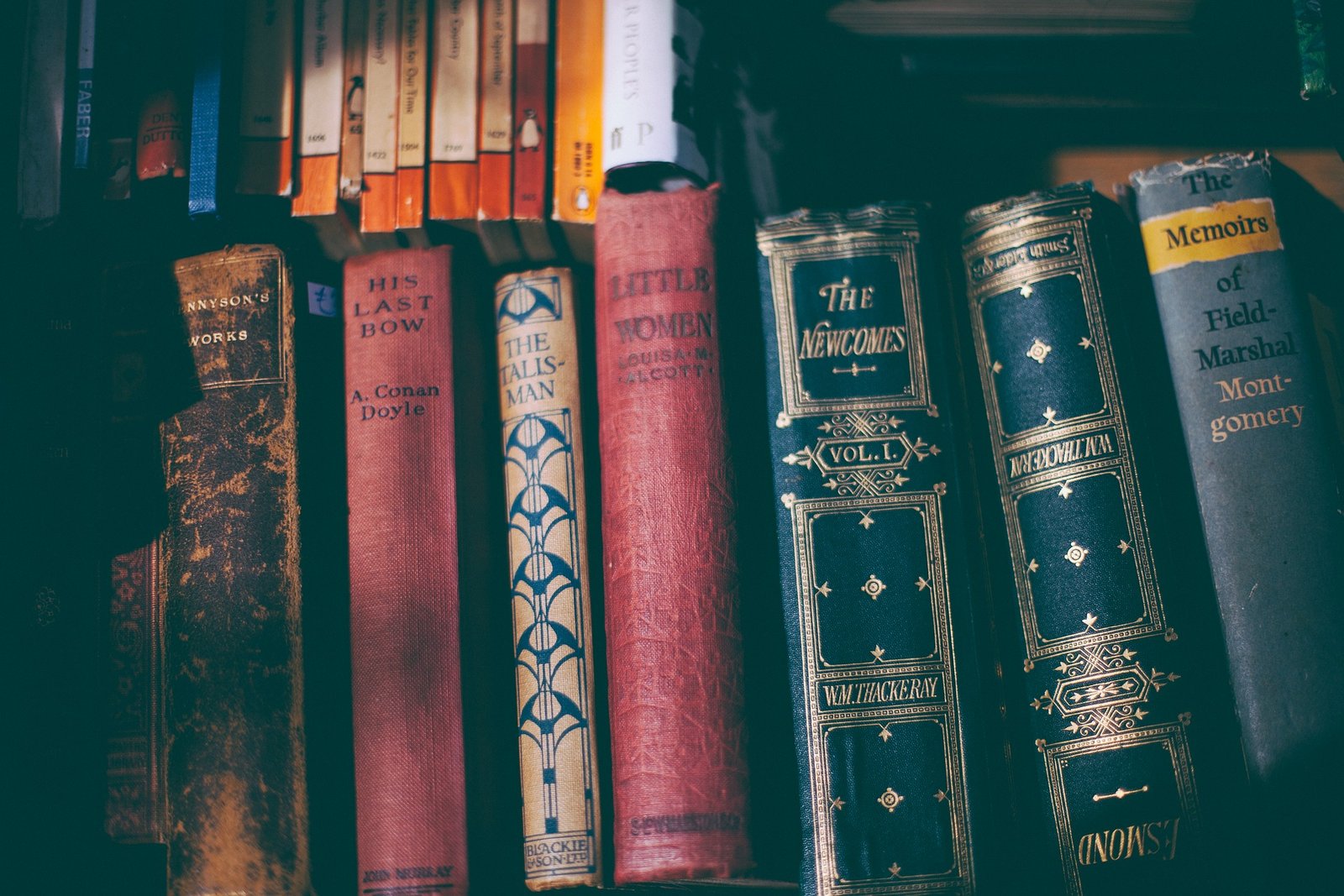
মূলপাঠ
হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি! অনিদ্রায়,
নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;-
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষী কয়ে দিলা পরে-
“ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।”
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥
বস্তুসংক্ষেপ
বাংলা ভাষার সাহিত্যভান্ডার বিচিত্র সম্পদে পরিপূর্ণ, কিন্তু কবি সেসব বৈভবকে অবহেলা করে নির্বোধের মত পরের সম্পদ আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যচর্চার জগতে পরিভ্রমণের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এ ছিল কবির জীবনের এক অনভিপ্রেত সময়, বিফল সাধনায় মগ্ন থাকার মরীচিকা মাত্র। কারণ পরভাষায় বড় কবি হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থতাই বয়ে আনে। পদ্মবনের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য পরিত্যাগ করে তিনি শ্যাওলা নিয়ে ক্রীড়ামত্ত হয়েছিলেন।
কিন্তু মাতৃভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বপ্নাদেশে কবির চেতনা জাগ্রত করেন, অর্থাৎ কাব্যচর্চার প্রেরণা অনুভব করে তিনি বাংলাভাষায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই ভাষা কবির মাতৃভাষা – অজস্র মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ, অতএব পরভাষারশারে ভিক্ষা প্রার্থনার কোন যুক্তি নেই। কাব্যলক্ষ্মীর আহ্বানে কবি সুখানুভবে ও আত্মমর্যাদায় ঋদ্ধ হয়ে মাতৃভাষায় খুঁজে পান অনন্ত রত্নসম্পদের আকর এবং বাংলা সাহিত্যকে নিজ প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ করেন।
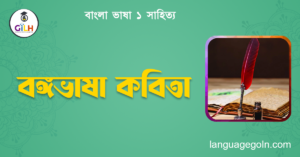
পাঠোত্তর মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. ‘পর-ধন লোভে মত্ত’ বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন?
উত্তর : ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার উদ্ধৃত বাক্যাংশে পরধন অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্য-উপাদানের কথা বলা হয়েছে। মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইংরেজি ভাষায় বড় কবি হবেন, তাঁর সাহিত্য সাধনার আরম্ভও হয় ইংরেজি ভাষাতেই। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ছিল বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণদের কাছে আরাধ্য।
কলকাতার নব্যশিক্ষিত যুবকদের চিন্তাচেতনায় ইংরেজ সভ্যতা-সংস্কৃতির যে প্রবল প্রভাব পড়েছিল তাতে তৈরি হয়েছিল এক পরানুকারী অথচ আলোকিত যুবসমাজ, ইতিহাসে যারা ইয়ং বেঙ্গল নামে অভিহিত। মাতৃভাষার প্রতি এদের ছিল অবহেলা। কবি নিজেও ইংরেজি কবিতা রচনার ভ্রান্ত পথানুসারী হয়েছিলেন।
২. ‘বঙ্গভাষা’ কোন জাতীয় কবিতা?
উত্তর : ‘বঙ্গভাষা’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট জাতীয় কবিতা। কবি মধুসূদন এর প্রবর্তক। সনেট রচিত হয় চৌদ্দ পংক্তিতে, আট ও ছয় পংক্তির বিভাজনে ভাবনাবস্তুর প্রস্তাবনা ও সম্প্রসারণ ঘটে একটি সুনির্দিষ্ট রীতিতে। আট পংক্তিকে বলা হয় অষ্টক (Octave) এবং ছয় পংক্তির নাম ষষ্টক (Sestet)। সনেটে প্রধানত দুটি রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয়। বঙ্গভাষায় গৃহীত হয়েছে উভয় রীতির মিশ্রণ।
প্রথম চার ও শেষ দুই পংক্তি শেক্সপীয়রীয় রীতিতে, পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণ পর্যন্ত অনিয়মিত শেক্সপীয়রীয় রীতিতে এবং নবম থেকে দশ চরণ পর্যন্ত পেত্রার্কীয় গঠনে বিন্যস্ত হয়েছে। আলোচ্য কবিতার অষ্টকে বর্ণিত হয়েছে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করার মনোবেদনা, ষষ্টকে ব্যক্ত হয়েছে কাব্যপ্রেরণার সঠিক নির্দেশনা লাভ, স্বভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রেরণা ও সিদ্ধিলাভের প্রসঙ্গ।
৩. ‘বঙ্গভাষা’র ছন্দ কি ?
উত্তর : ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। আপনারা নিশ্চয়ই ইউনিট- ১ এ কবিতার ছন্দ বিষয়ে পরিচিত হয়েছেন। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত— এই তিনটি ছন্দরূপের মধ্যে অক্ষরবৃত্ত প্রধান ছন্দ। গম্ভীর ভাব, ওজস্বী শব্দ ও ধীরলয় সম্বলিত এই ছন্দটির বিকাশ ও বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যজগতের বিশেষ সম্পদ। এখানে প্রতি চরণে ১৪ মাত্রার দুটি পর্ব রয়েছে, প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পর্বে ৬ মাত্রা। যেহেতু এটি সনেট, তাই এর অন্তমিল হল— কখ কখ, খক খক, গঘ ঘগ, ঙঙ
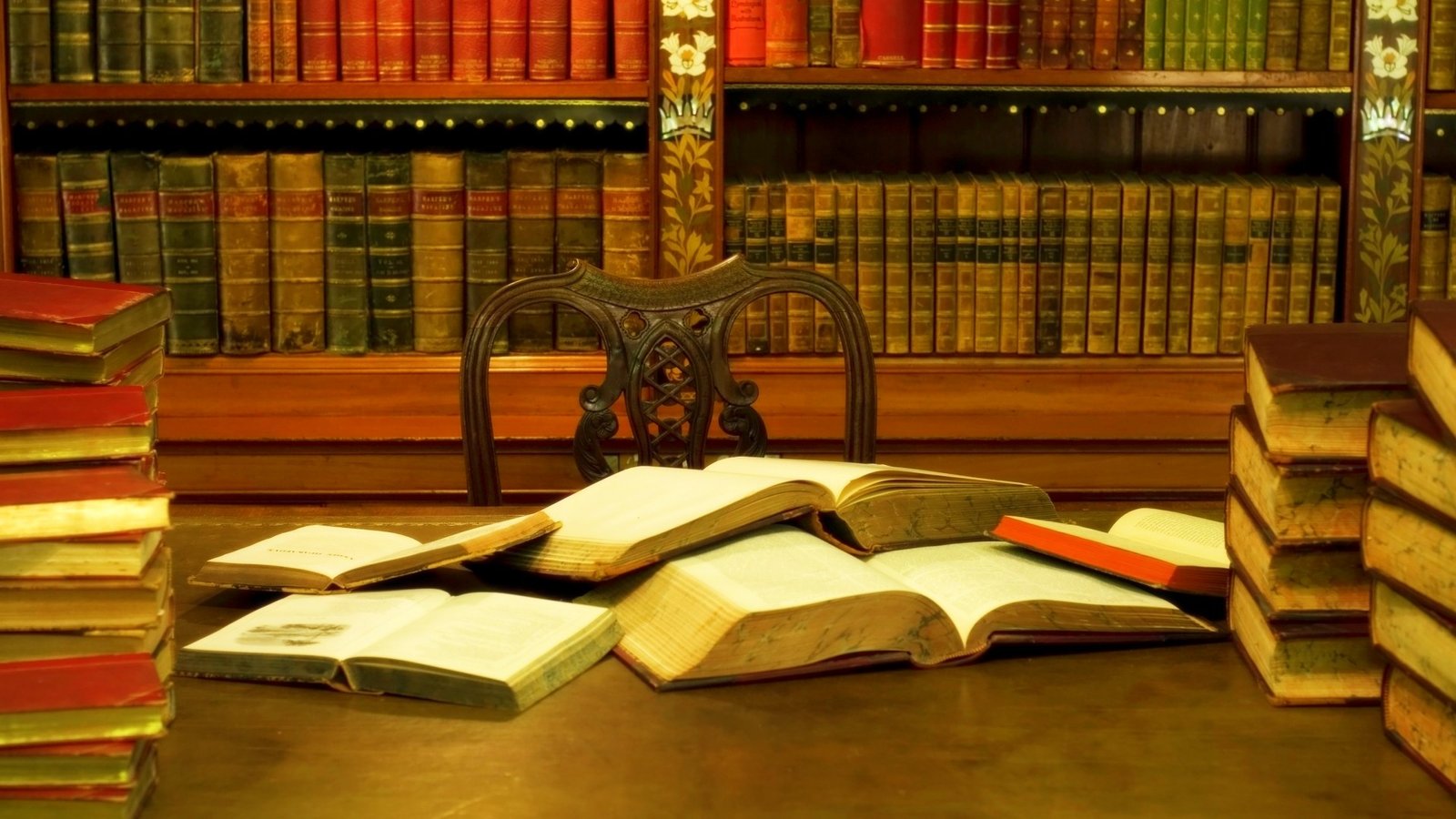
রচনামূলক প্রশ্ন
১. “বঙ্গভাষা” কবিতা কবি মধুসূদনের আত্ম আবিষ্কারের শিল্পভাষ্য মন্তব্যটি আলোচনা করুন।
২. সনেট হিসেবে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার স্বরূপ ও সার্থকতা নিরূপণ করুন।
৩. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার ভাববস্তু ও শিল্পমূল্য বিবেচনা করুন।