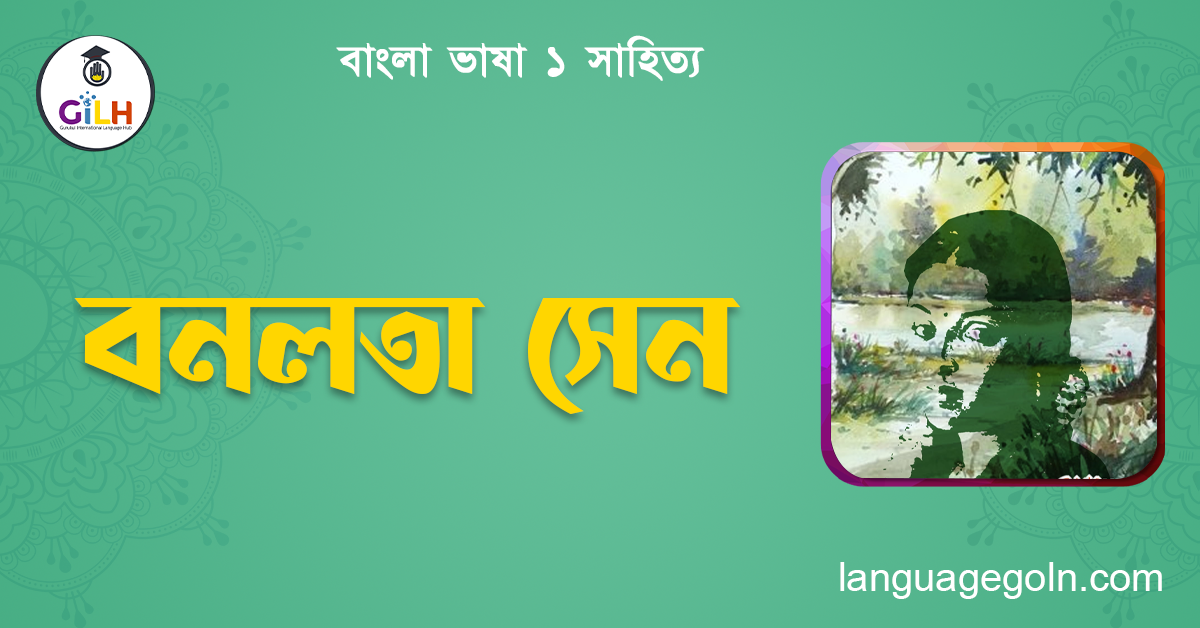আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বনলতা সেন
বনলতা সেন
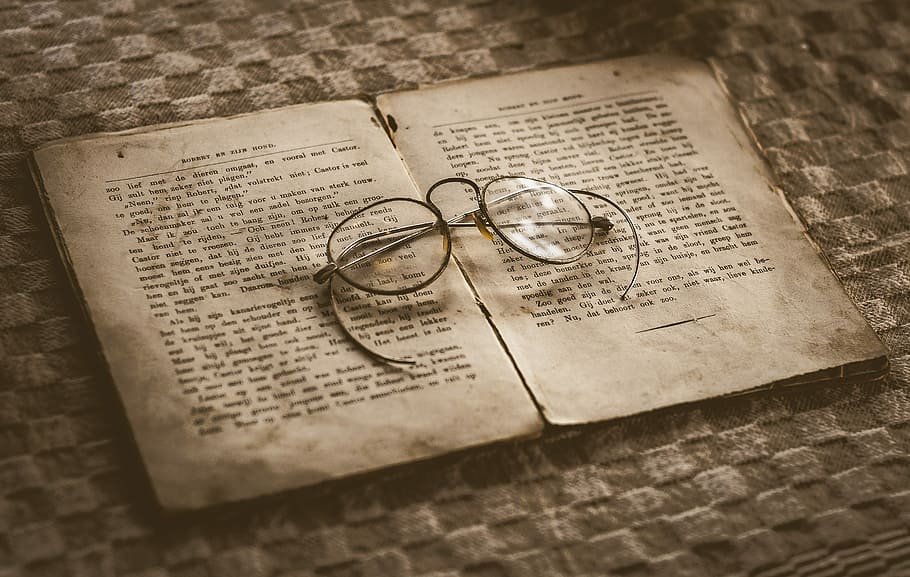
বনলতা সেন
লেখক-পরিচিতি
বিশ শতকের তিরিশের দশকে আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রগণ্য কবি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্র-পরবর্তী নতুন কবিতার ধারা প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা প্রধান। প্রকৃতি, আবহমান সময় ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক চৈতন্যের সংযোগে তিনি সৃষ্টি করেন এক অভিনব শিল্পজগৎ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলা শহরে তাঁর জন্ম, পিতা সত্যানন্দ দাশ, মাতা কবি কুসুমকুমারী দাশ। বংশগতভাবে তাঁর পূর্বপুরুষ হিন্দু হলেও পিতামহ সর্বানন্দ দাশ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন।
পরিবারটি ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চা ও আদর্শ জীবনযাপনের মধ্যে পরিশীলিত। বরিশালেই জীবনানন্দের স্কুল ও কলেজ জীবন অতিবাহিত হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৯-এ ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৯২১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। তারপর আইন পড়ার জন্য ভর্তি হলেও অসুস্থতার জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন নি।
তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। একসময় ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবেও কাজ করেছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৬-এ জীবননান্দ স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন।
কর্মজীবনে মাঝে মাঝে চাকরিচ্যুত হয়েছেন বা নিজেই পরিত্যাগ করেছেন। তবে মূলত অধ্যাপনা পেশাতেই তিনি ছিলেন নিয়োজিত ।
তাঁর সাহিত্যজীবনই ছিল প্রকৃত জীবন, এই জীবনেই তিনি সর্বতোভাবে ছিলেন নিবেদিত। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এ, ‘বর্ষ-আবাহন’ নামে। তিরিশের দশক থেকেই জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির বলিষ্ঠ ও স্বকীয় রূপটি উন্মোচিত হতে থাকে। ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগন্থ ‘ঝরাপালক’।
‘ধূসর পান্ডুলিপি’ (১৯৩৬) কাব্যে জীবনানন্দের মৌলিক কবিস্বভাব ও আধুনিক কাব্যরীতির প্রকাশ ঘটে, যাকে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেন ‘চিত্ররূপময়’ বলে। তাঁর কাব্যবিষয় প্রধানত প্রকৃতি-ভূগোল-ইতিহাস-প্রেম-নারী-মৃত্যুচেতনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসক্ষেত্রে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা- বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি খুঁজেছেন মানব-অস্তিত্বের নৈতিকতা ও হৃদয়সত্তার স্বরূপ।
এক্ষেত্রে ঐতিহ্যের বিপুল ঐশ্বর্য তাঁকে প্রাণিত করেছে, ইতিহাসজ্ঞান দিয়েছে সংশয় ও নৈরাশ্যের ক্ষেত্রে আলোর ইশারা। জীবনানন্দ চিত্রকল্পের বিস্ময়কর ভূবন রচনা করেছেন, কাব্যভাষার স্বতন্ত্র রূপ গড়েছেন এবং আধুনিক কলাকৌশলে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কবিতার আঙ্গিক।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ ঝরাপালক (১৯২৯), ধূসর পান্ডুলিপি (১৯৩৬), রূপসী বাংলা ১৯৩৩), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যাও বিপুল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে জীবনানন্দ ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।
তিনি কথাসাহিত্যেরও রচয়িতা, তদুপরি রয়েছে প্রবন্ধপুত্মক। প্রচলিত রূপরীতি বর্জন করে ছোটগল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন নতুন ধরনের আঙ্গিক। আধুনিক ব্যক্তিমানুষের উজ্জ্বল জীবনবেদ ও বেদনার রূপ উন্মোচন করেছেন জীবনানন্দ; যেখানে আশা ও নৈরাশ্য, বাস্তব ও পরাবাস্তব, অন্ধকার ও আলো আন্তরবৈপরীত্যে কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে আছে।
মায়াবী অপরূপ বিষণ্ণতা ও বেদনার গভীর তাৎপর্য তাঁর কবিস্বভাবের মূলরূপ। পরবর্তী বাংলা কবিতার অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি ।
পাঠ-পরিচিতি
‘বনলতা সেন’ কবিতাটি ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায়, পৌষ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে। কবির ব্যক্তিজীবনে বনলতা সেন নাম্মী কোন নারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছেন। তাঁর ‘কারুবাসনা’ নামক উপন্যাসে যা তাঁর আত্মজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বহন করে, বনলতা নামটির উল্লেখ রয়েছে।
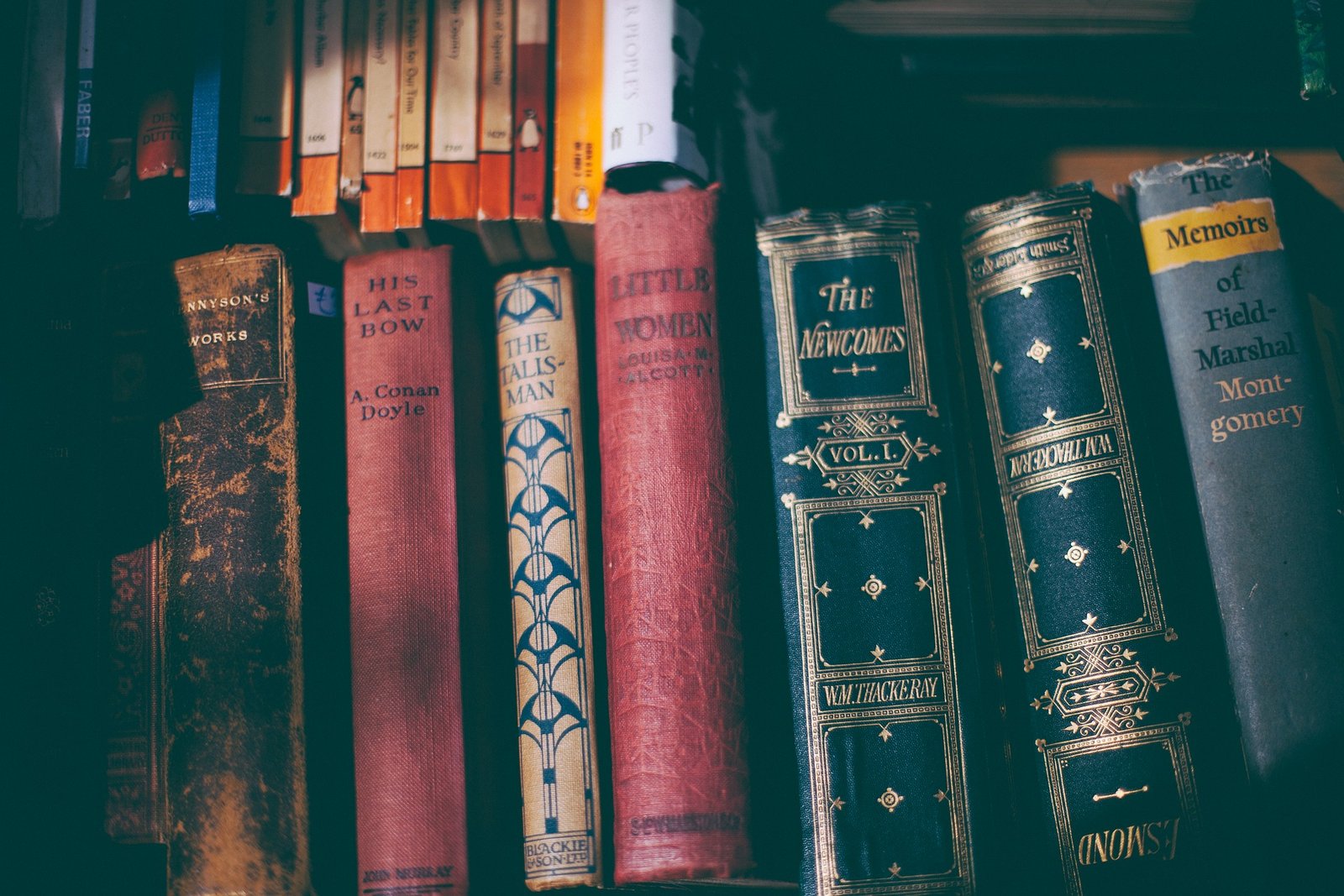
মূলপাঠ
হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে
মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি;
বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি;
আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে; আমি ক্লান্ত প্রাণ এক,
চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন ।
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;
অতিদূর সমুদ্রের ‘পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে
দিশা সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?”
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন ।
সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে;
ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে
আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে – সব নদী – ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন ।
বস্তুসংক্ষেপ
পথিক-চিত্তের অবিরত ভ্রমণ যেমন জীবনধর্ম, তেমনি প্রশান্তির আশ্রয় সন্ধানই জীবনের উদ্দেশ্য। এই পথিক হাজার বছর ধরে পথ চলছে অর্থাৎ চেতনা উন্মেষের শুরু থেকেই তাঁর এই পথচলা। সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর পর্যন্ত যেমন সে নাবিক হয়ে জলপথ ভ্রমণ করেছে সুদূর অতীত থেকে, তেমনি স্থলপথেও ঘুরেছে বিম্বিসার অশোকের ধূসর কাল থেকে।
ফলে পথিকচিত্ত ক্লান্ত, জীবনের সফেন সমুদ্রের মাঝখানে অর্থাৎ গতিতরঙ্গের ফেনায় পুঞ্জীভূত জীবনের অস্থিরতার মধ্যে পথিক পেয়েছে শান্তিদায়িনী বনলতার সংস্পর্শ। নাটোর নামক স্থানের উল্লেখ করে বনলতাকে একান্ত, নিজস্ব মানবী সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে অতীত স্থানকাল বর্তমানের স্থানের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে।
এই বনলতা সেন অন্ধকারের ঘনত্বে আবৃত, তার চুল, মুখ ও চোখের বর্ণনায় ফুটে ওঠে ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য ও রোমান্টিক রূপমাধুরী। বনলতা সেনের কেশরাশি অতীতের বিদিশা নগরীর রাত্রির মত অন্ধকার অর্থাৎ প্রগাঢ় কালো। তার মুখচ্ছবিতে শ্রাবন্তী নগরীর কারুকার্য, অতীতের ক্ল্যাসিক রূপসুষমায় সে গঠিত। কিন্তু তার চোখ পাখির নীড়ের মত নিবিড় আশ্রয়ের প্রতীক অর্থাৎ শ্রান্ত জীবনের জন্য সে বহন করে অনাবিল প্রশান্তি ও স্থিরতা।
গভীর সমুদ্রে জাহাজের নাবিক হাল ভেঙে গেলে নাবিক যখন দিশাহীন হয়ে পড়ে, তখন কোন দারুচিনি সবুজ দ্বীপ দেখতে পেলে আশ্বস্ত হয়। ব্যক্তিমানুষও তার নিরুদ্দেশ, উন্মুল জীবনের ক্লান্ত-শ্রান্ত ভ্রমণের শেষে নিজ নিজ মানবীসত্তার চোখে সন্ধান করে স্থিতি ও শান্তি। এই মানবীসত্তাও যেন ক্লান্ত পথিকের জন্য থাকে অপেক্ষমান। নিরাশ্রয়ী চিত্তের জন্য সৌন্দর্য ও প্রশান্তির জগৎ তৈরিই কবির লক্ষ্য ।
দিনশেষের চিত্র এঁকে কবি প্রাণের গতিমুখ তথা মৃত্যুর ইঙ্গিত প্রকাশ করেছেন। সন্ধ্যায় নিভে যায় পৃথিবীর রঙ-আলো, চিলের ডানায় রৌদ্রের গন্ধ থাকে না অর্থাৎ জীবনের উজ্জ্বলতা থাকে না। সবকিছু আবৃত হয় এমন এক অন্ধকারে, যেখানে আশ্রয়, মৃত্যু এবং একই সঙ্গে থাকে নতুন সৃষ্টিশীলতার আয়োজন। ছায়া-অন্ধকারের মধ্যেই কবি দেখেন তার প্রার্থিত সত্তার অস্তিত্ব। তখন এক চলার বাস্তবতা থেকে কবি প্রবেশ করেন আরেক বাস্তবতায় যাওয়ার আয়োজনে।
পান্ডুলিপি যেমন কোন লিখিত গ্রন্থ নয়, গ্রন্থের পূর্বরূপ মাত্র। পান্ডুলিপি রচনার আয়োজন হয় অন্ধকারে জোনাকীর আলোতে অর্থাৎ কোন অপার্থিব মুহূর্তে – যেখানে পাখি ও জীবননদীর সব চলা ও চাওয়াপাওয়া নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু জেগে থাকে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা – বনলতা সেন সেই সৃষ্টিসত্তারই প্রতীক।
অন্ধকার-মুহূর্তে সে সত্য হয়ে ওঠে, এই মুহূর্তটি হচ্ছে এক সত্তা থেকে আরেক সত্তায় উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী স্তর। এর পরে সব কথকতা গড়ে উঠবে অন্ধকারস্থিত বনলতা সেনের সঙ্গে, যে চিরমানবীর রহস্যে অন্ধকার তুল্য। কবিতাটিতে ইতিহাসজ্ঞান ও প্রাকৃতিক জীবনের স্থিরতর শান্তি মিশিয়ে কবি স্থাপিত করেছেন তাঁর বনলতা সেনকে তথা চিরন্তন সত্তাকে।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. ‘হাজার বছর ধরে’ কবি কোথায় পথ পরিভ্রমণ করছেন?
২. ‘নাটোরের বনলতা সেন’ কি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?
৩. ‘পাখির নীড়ের মত চোখ— কথাটির তাৎপর্য কি?
৪. কবিতাটিতে কতবার ও কি অর্থে ‘অন্ধকার’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
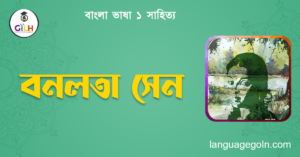
রচনামূলক প্রশ্ন
১. “ইতিহাস-ভূগোলের পটে ব্যক্তিগত প্রেমের উপস্থাপনাই ‘বনলতা সেন’ কবিতার আধেয়”। – আলোচনা করুন।
২. ‘বনলতা সেন’ কোন্ ধারার কবিতা? প্রসঙ্গত কবিতাটির শিল্পরূপ আলোচনা করুন।
৩. ‘বনলতা সেন’ কবিতার মূলভাব ব্যক্ত করুন।
৪. ‘বনলতা সেন’ কি গীতিকবিতা? কবিতাটির নামকরণ কতটুকু যথাযথ?
আরও দেখুন :