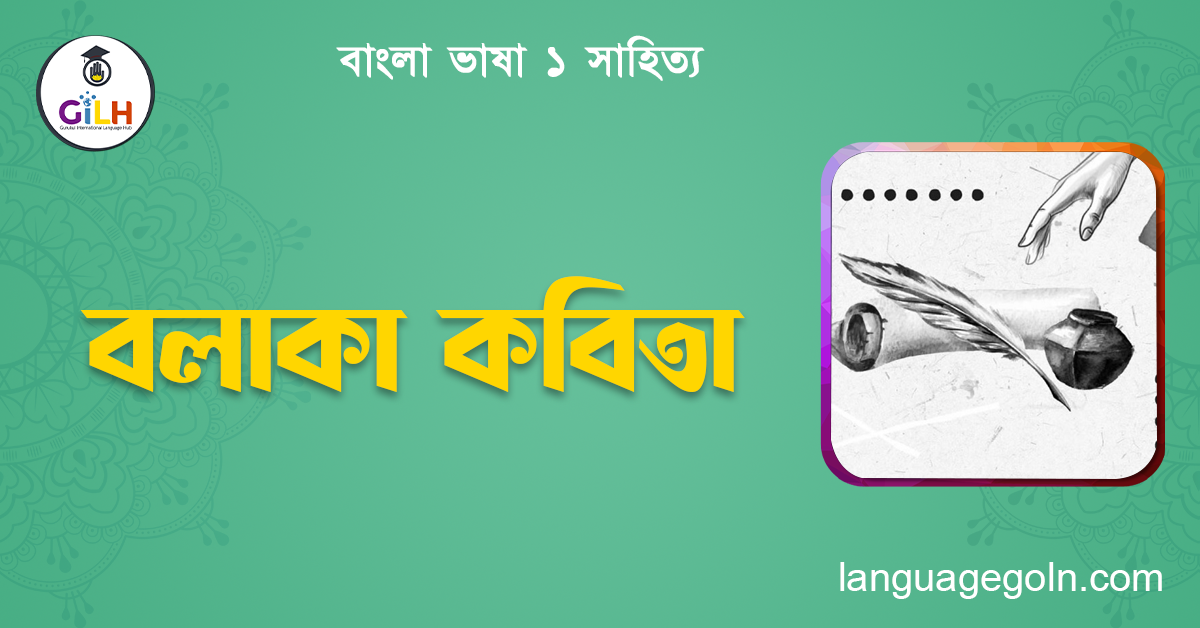আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বলাকা কবিতা
বলাকা কবিতা

বলাকা কবিতা
লেখক-পরিচিতি
১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোতে, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), জননী সারদাদেবী। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্সশারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপন্নস্নারকানাথ নিজের যোগ্যতা বলে সেকালের কলকাতায় ধনী শিল্পপতি ও সমাজের প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন।
উনিশ শতকের কলকাতায় ধর্ম-সাহিত্য-ব্যবসা-শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মকান্ডে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির অগ্রণী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ফলে শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ এক অভিজাত পরিএন্ডলের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তাঁকে প্রেরণ করা হলেও, শৈশব-কৈশোর থেকেই বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিলো না।
১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে প্রথম ইংল্যান্ড পাঠানো হয়। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নও করেন কিছুদিন। কিন্তু পিতৃ-আদেশে পাঠ-অসমাপ্ত রেখেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে ব্যারিস্টারী পড়ানোর জন্যে দ্বিতীয় বার লন্ডনে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু যাত্রারম্ভ করেও মধ্যপথে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথ।
ফলে রবীন্দ্রনাথের সনাতন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। পুঁথিগত বিদ্যার বাঁধন তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনি কখনও ।
শৈশবেই সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তি, সংবেদনশীলতা ও মননধর্মের প্রকাশ ঘটেছিলো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। আর মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি প্রকাশ করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প ‘ভিখারিণী’ (১২৮৪ বঙ্গাব্দ)। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস ‘করুণা’ (১২৮৪-৮৫ বঙ্গাব্দ)।
পরিবর্তমান সময়স্রোতে রবীন্দ্র-মানস ক্রমবিকশিত হয়েছে প্রতিনিয়ত, দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ছোটগল্প, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি শাখায় তাঁর সৃজনশীলতা জন্ম দিয়েছে এক সমৃদ্ধ ভান্ডার। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলি তাঁর অসামান্য প্রতিভার সাক্ষ্যবহ। একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ কীর্তিমান। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়’।
উত্তরকালে এই বিদ্যালয়ই ‘বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। তাঁর সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠসময় অতিবাহিত হয় বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং সাজাদপুর অঞ্চলে। পারিবারিক জমিদারির তত্ত্বাবধান-সূত্রে পূর্ববাংলার পদ্মাবিধৌত এই অঞ্চলে তাঁকে প্রেরণ করা হয়। এ সময় কৃষি উন্নয়ন ও কৃষক-কল্যাণের জন্যও রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ‘গীতাঞ্জলি’র স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ ‘Songs Offerings’ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের জন্যই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। ব্রিটিশ সরকার ‘নাইট’ উপাধি তাঁকে প্রদান করেন। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব রক্ষা না করলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবন ও রাজনীতি সতর্ক মানুষ।
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রকাশ্য গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি সরকার প্রদত্ত ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তিনি সামনে এসে দাঁড়ান। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রচিত ‘সভ্যতার সংকট” ১৯৪১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতাগবী অথচ যুদ্ধোন্মাদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে একদিন এ-দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে— রবীন্দ্রনাথ এ-আশাবাদ প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে।
কবি অভিধা-ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশধারায় তাঁর অসামান্য অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর সৃজনসামর্থ্যেই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম আত্মপ্রকাশ। সুদীর্ঘ সাহিত্যিকজীবনে ‘সে’ এবং লিপিকা’র রচনাগুলি ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন চুরানব্বইটি ছোটগল্প।
‘ভিখারিণী’ থেকে ‘মুসলমানীর গল্প’ (মুখে মুখে রচিত গল্পের খসড়া) পর্যন্ত এই বিশাল গল্পভান্ডার বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশাধারার শিল্পিত ইতিহাস। বাংলা সৃষ্টিশীল গদ্যের গতিপ্রবাহও চিহ্নিত হয়ে আছে অখন্ড ‘গল্পগুচ্ছে’র পাতায় পাতায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন – ‘আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্রমূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পারো না।
এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে।…. মোপাসাঁর মতো যেসব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বলো, , তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাদের কী দশা হত জানি নে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর উলেখযোগ্য রচনা
কবিতা: মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৩), চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১১), বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ (১৯৩২), জন্মদিনে (১৯৪১), আরোগ্য (১৯৪১), শেষ লেখা (১৯৪১)। উপন্যাস: রাজর্ষি (১৮৮৯), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯)।
গদ্য রচনা: যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (১৮৯১), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), জীবনস্মৃতি (১৯১২) ছিন্নপত্র (১৯১২),
প্রবন্ধ: কালান্তর (১৯৩৭), বিশ্ব পরিচয় (১৯৩৭)। নাটক: বিসর্জন (১৮৯০), অচলায়তন (১৯১১), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬)।
নাটক : বিসর্জন (১৮৯০), অচলায়তন (১৯১১), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬)।
গান : গীতিবিতান ।
ছোটগল্প: গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড-১৯২৬, ২য় খন্ড-১৯২৬, ৩য় খন্ড-১৯২৭), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১), গল্পসল্প (১৯৪১)।
পাঠ-পরিচিতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘বলাকা’ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘বলাকা’র (১৯২৬) অন্তর্গত ৩৬ সংখ্যক কবিতা। ১৩২২ বঙ্গাব্দে কাশশ্মীরের শ্রীনগরে অবস্থানকালে তিনি কবিতাটি রচনা করেন। কখনো-কখনো প্রকৃতির দৃশ্যাভিজ্ঞতা থেকে কবিচিত্তে জেগে ওঠে আকস্মিক কাব্যপ্রেরণা ও জীবনদর্শন। ‘বলাকা’ তেমনি প্রাকৃতিক দৃশ্যানুভূতিজাত আকস্মিক প্রেরণালব্ধ কবিতা।
শ্রীনগরের ঝিলম নদীতে বোটে অবস্থান করার সময় তিনি আসন্ন সন্ধ্যার পটে দেখেছিলেন এক ঝাঁক বুনোহাঁসের উড়ে-চলার দৃশ্য। তাদের পাখার শব্দধ্বনি কবির দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরে বিশ্বের চাঞ্চল্য ও গতিশীলতার প্রতিচ্ছবি। এই প্রতিচ্ছবিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন গতিদর্শনের শিল্পমূর্তি। ‘বলাকা’ প্রথম প্রকাশিত হয় সবুজপত্র পত্রিকায়, কার্তিক ১৩২২ বঙ্গাব্দে।

মূলপাঠ
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার !
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে দেওদার-তরু সারে সারে ;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি –
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি ॥
সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে। হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সররমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন
মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে
পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ’রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগি !
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে –
‘হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্খানে!” হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা ।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে হলে
তৃণদল মাটির আকাশ-‘পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে,
কে জানে ঠিকানা, মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল ।
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা ।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায় দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে,
অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে ॥
শুনিলাম মানবের কত বাণী
দলে দলে অলক্ষিত পথে উড়ে চলে অস্পষ্ট
অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে অসংখ্য
পাখির সাথে দিনে রাতে এই বাসাছাড়া
পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে কোন্ পার হতে কোন্ পারে ।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে
‘হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে !
বস্তুসংক্ষেপ
ঝিলম নদীর ঝিলিমিলি বঙ্কিমস্রোত যেন বাঁকা তলোয়ার। সন্ধ্যার অন্ধকার এসে যেন বাঁকা তলোয়ারটিকে খাপের মধ্যে পুরে নিল। জোয়ার-ভাঁটার পরম্পরার মতো দিনের আলোর শেষে এল রাতের এই কালো আঁধার-বন্যা। নদীর জলে প্রতিবিম্বিত তারাজ্বলা আকাশের ছবি যেন বন্যায় ভেসে আসা তারাফুল। কবি নদীর চঞ্চল স্রোতে অচঞ্চল আকাশের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।
নদীতীরের পথপারে পাহাড়ের পাদমূলে রয়েছে সারিবদ্ধ দেবদারু বৃক্ষ। তারা ঘনবদ্ধ হয়ে রচনা করে রেখেছে অন্ধকারের স্তব্ধরূপ। আমাদের সুপ্ত চেতনা যেমন অন্ধকার রাত্রে অস্পষ্ট আলোর স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তেমনি এখানে জমাটবদ্ধ দেবদারুর মধ্যেও ব্যক্ত হতে চাইছে কোন অস্পষ্ট স্বপ্নকথা। কিন্তু প্রকাশে ব্যর্থ হয়ে তারা সে কথাকে পুঞ্জীভূত কান্নায় রূপান্তরিত করে রাখে, সেই কান্নাই হলো অন্ধকার ।
এই স্তব্ধ মুহূর্তে হঠাৎ শোনা গেল এক ঝাঁক হংসের পক্ষধ্বনি। কবির মাথার উপর দিয়ে তারা শব্দের বিদ্যুৎছটা বিকীর্ণ করে দিয়ে দূরদেশে উড়ে গেল। তাদের পাখার মদমত্ত অট্টহাস যেন আকাশে সৃষ্টি করল শব্দঝড়। সুপ্ত আকাশ-নদীতে সেই শব্দতরঙ্গ জাগিয়ে তুলল বিস্ময়ের প্রতিধ্বনি। ফলে নদী ও আকাশ একই সঙ্গে হয়ে উঠল গতিচঞ্চল— চলমানতার সঙ্গে যুক্ত হলো স্তব্ধতা। স্বর্গের অপ্সরা পৃথিবীর ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করতো।
তাদের রূপ যেমন শব্দধ্বনি হয়ে সন্ন্যাসীর স্তব্ধতা ভেঙে দিত, তেমনি স্তব্ধবাক আকাশের মৌনতা ভেঙে দিল বলাকার পক্ষধ্বনি। এই শব্দে শিহরিত হলো পর্বতশ্রেণী, রোমাঞ্চিত হলো দেবদারু। তাদের জড়প্রাণে সঞ্চারিত হলো চলার আবেগ। হংসপাখার বিমানগতি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুললো গতির আকাঙ্ক্ষা । এই ধ্বনি স্পর্শে স্থানু পর্বত মেঘের মতো উড়ে চলার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হলো।
শিকড়বদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীও মাটির বন্ধন ছিন্ন করে ঐ শব্দধ্বনির পথ অনুসরণ করতে চাইলো। কারণ তারাও হতে চায় নিরুদ্দেশের যাত্রী। যাযাবর পাখিদের পাখায় রয়েছে অস্থিরতার চাঞ্চল্য, শুধুই উড়ে-চলার আকুলতা। পরিচিত বাসায় তারা চিরকাল বাস করতে চায় না। এক বাসা ভেঙে সমুদ্রপারের অন্য বাসার সন্ধানে তারা উড়ে যায়। কবি এ-অর্থে বলাকাকে বলছেন ‘পাখা বিবাগী’। তারা নিখিল- বিশ্বপ্রাণে সেই সুর বাজিয়ে দিয়ে গেল যে স্থিতি নয়, অন্য কোথাও ধাবিত হওয়ার আবেগই সৃষ্টির প্রকৃত ধর্ম।
কবির অন্তর্চক্ষুতে উদ্ভাসিত হলো সৃষ্টিলোকের গভীর সত্য, যা-কিছু স্তব্ধ হয়ে ছিল তার আবরণ যেন উন্মোচিত হয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন সর্বত্র রয়েছে গতির চাঞ্চল্য, নিশ্চল বস্তুর অন্তরে রয়েছে গতিশীলতার উদ্দীপনা ও বেগ । এই অনুভব থেকে কবি আরও দেখলেন যে তৃণদল মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে; মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বীজ মেলছে অঙ্কুর- পাখা।
ক্ষুদ্র বস্তুর এই নিভৃত-চলার সত্য থেকে কবির দৃষ্টিবিন্দু ক্রমে আবিষ্কার করতে থাকে বৃহৎ চলমানতার রূপ। পর্বত, বন, বৃক্ষরাজি, নক্ষত্র— – সবকিছুই সম্মুখ দিকে ধাবমান; সমস্ত বিশ্বজগৎ গতিস্পন্দনে ব্যাকুল ও সচল। তবে এই চলায় যেমন আছে আনন্দ, তেমনি আছে ক্রন্দনসুর। কবি তাই বলছেন, চলমান নক্ষত্র তার পাখার স্পন্দনে আলোর কান্না সৃষ্টি করে চমকে দিচ্ছে অন্ধকারকে।
সৃষ্টিজগতের স্বরূপেই রয়েছে প্রসারণ-গতি— আলোর আকাঙ্ক্ষায় এই চলা সর্বদাই স্থিতিশীল নীড়-পরিত্যাগী, তাই বেদনাপুত। প্রকৃতির মতো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন যুগ থেকে যুগান্তরে ধাবিত হচ্ছে। চেতনার উন্যেকাল থেকে – কোন এক অস্পষ্ট অতীতে মানবচিত্তে জনে ছিল এইসব আকাঙ্ক্ষা- কামনাভাবনার বাণী। চিত্তগুহা ছেড়ে ঐসব বাণী স্রোতের মতো ভেসে চলেছে মহাকাল সমুদ্রে কোথায় তাদের গন্তব্য তা জানা নেই।
অতীত থেকে উৎসারিত এই অপূর্ণ-অচরিতার্থ বাণী পূর্ণতা-সন্ধানী, তাই চলমান। কবি নিজের অন্তরের দিকেও তাকিয়ে দেখলেন যে তার মনটিও বাসা ছাড়া পাখির মতো অবিরত চলিষ্ণু। যা-কিছু গতিশীল ও সম্মুখগামী তাদের সহযাত্রী হয়ে কবির মন চলছে। অর্থাৎ সৃষ্টিলোক, মানবচিত্তের বাণী আর কবির হৃদয়— – সবকিছু একসূত্রে একটি গতির সুরে বাঁধা। কিন্তু কোথায় গন্তব্য তা জানা নেই।
কবি শুধু এটুকু জানেন যে এই বাসস্থান ছেড়ে, স্থিতির মায়া ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে । বলাকা যেমন সংসার-নীড় ছেড়ে কিসের আবেগে অকূলে পাড়ি দেয়, অনিশ্চয়তায় উড়ে চলে, তেমনি নদী-বন-পাহাড়-নক্ষত্র-মানুষ-কবিমন — সবকিছুর মধ্যে আছে ঐ সম্মুখ গতির দুর্জেয় আবেগ। এই আবেগ- রূপটিই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্ব, উপনিষদে একে বলা হয়েছে চরৈবেতি ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. হংসবলাকার উড়ে যাওয়ার কবিচিত্তে কী প্রভাব ফেলেছিল?
২. ‘পাখা বিবাগি’ বলতে কী বুঝিয়েছেন?
৩. বলাকার পক্ষধ্বনি প্রকৃতিকে কীভাবে আলোড়িত করল?