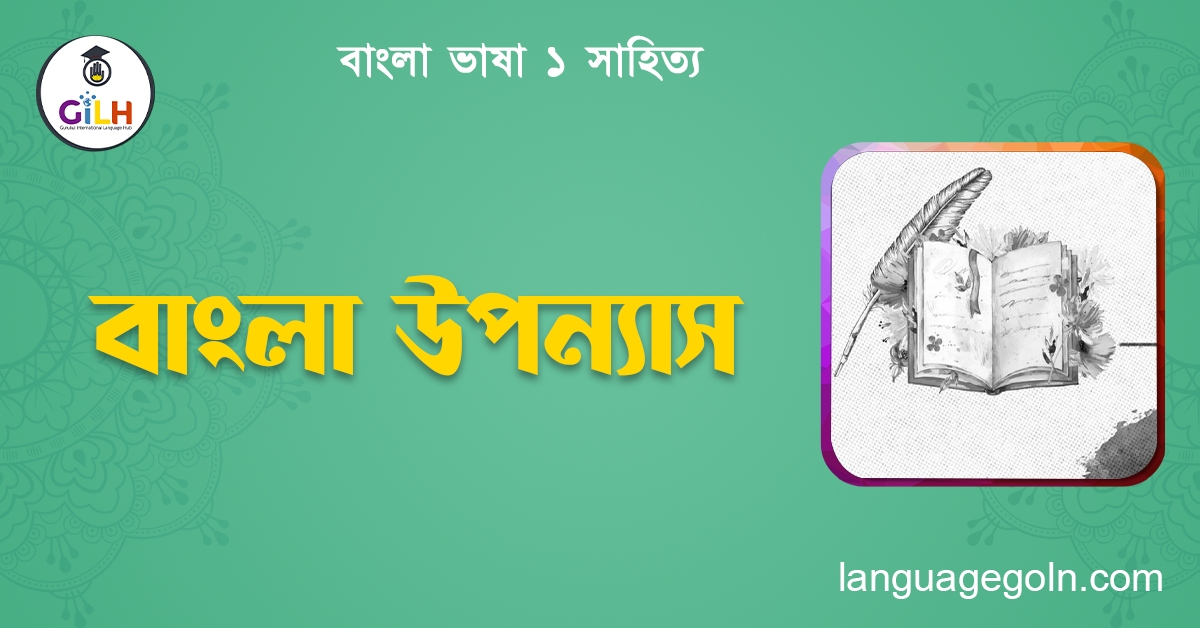আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলা উপন্যাস
বাংলা উপন্যাস
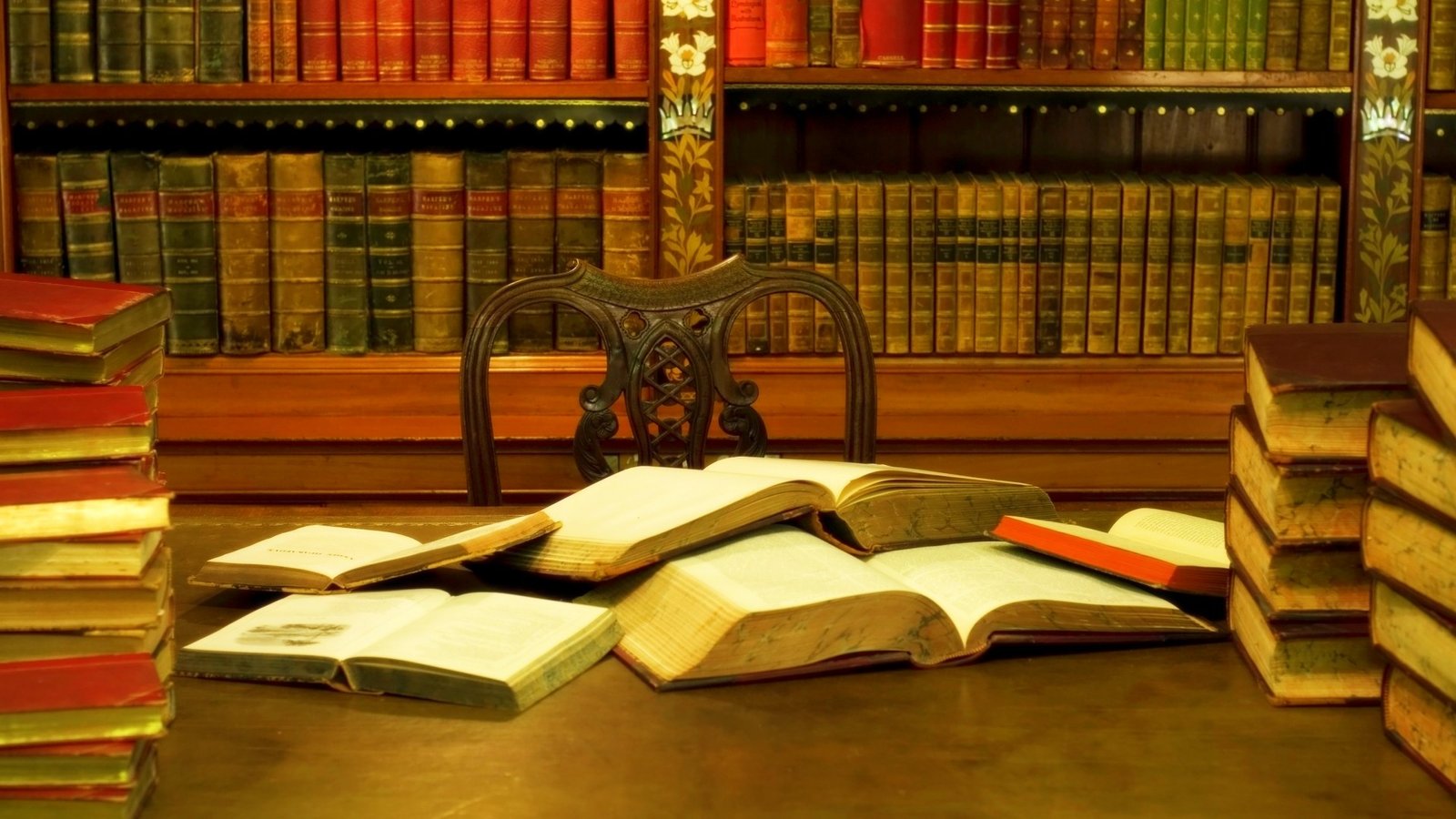
বাংলা উপন্যাস
সংজ্ঞার্থ
সাহিত্যের আঙ্গিকগুলোর মধ্যে উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা দুরূহ কাজ। কেননা, সময় ও সমাজের এতো বিচিত্রমুখী ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও ভাঙা-গড়ার যুগে উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোনো মানদন্ড দিয়ে উপন্যাসের স্বভাবধর্ম নিরূপন করা সম্ভব নয়। উপন্যাসের উদ্ভবের সঙ্গে সমাজবিন্যাস, আর্থ-উৎপাদন কাঠামো, মানুষের মনোজাগতিক সূক্ষ্মতা এবং অস্তিত্বজিজ্ঞাসার জটিল ক্রমবিকাশের প্রশ্ন জড়িত।
রেনেসাঁ বা নবজাগরণ- পরবর্তী মানুষের নতুন জীবন – ভাবনা, বাণিজ্যপুঁজির আশ্রয়ে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপুল বিস্তার এবং শিল্পবিপ্লব- উত্তর নাগরিক সভ্যতার দ্বন্দ্বসংঘাতপূর্ণ, জটিল, বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল জীবনের শিল্প আঙ্গিক হিসেবে ইউরোপে উপন্যাসের উদ্ভব। সুতরাং উপন্যাস তার জন্মলগ্নেই সমাজ ও জীবনের বাস্তবতার অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। এই বাস্তবতার চরিত্র সমাজ ও ব্যক্তিভেদে বিচিত্র।
উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে, তার বিষয় ও আঙ্গিকের স্বরূপ নির্ধারণে আলোচনার শেষ নেই। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমালোচকগণ দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক ও বিশেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু কোনো মীমাংসিত সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হতে পারেন নি। তবুও স্বভাবলক্ষণ এবং বিষয় ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য বিচার করে উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করা সম্ভব। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় ও বিষয়-আঙ্গিক বিচার সময় ও সমাজের চরিত্র ও রুচি অনুসারী।
যেমন আয়তন, , চরিত্র এবং ঘটনা-বৈশিষ্ট্য বিচারে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘ওল্ডম্যান এন্ড দ্য সী’ এবং লিউ তলস্তয়ের ওয়ার এন্ড পীস’ দুই ভিন্ন স্বভাবের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। হারমান মেলাভিলের ‘মবিডিক’ এবং জেমস্ জয়েসের ‘ইউলিসিস’, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুন্ডলা’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’, সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্র ‘চাঁদের অমাবস্যা’, এবং শহীদুলা কায়সারের
‘সংশপ্তক’ আয়তন, চরিত্রায়ন এবং বিষয়বিচারে ভিন্নধর্মী সৃষ্টি। কিন্তু সবগুলোই উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত ও বিশেষিত। তবুও উক্ত গ্রন্থগুলোতে মৌৗলিক কিছু লক্ষণ বিদ্যমান, যার ভিত্তিতে ঐসব গ্রন্থ উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। উপর্যুক্ত ধারণার আলোকে উপন্যাসের একটি সাধারণ সংজ্ঞার্থ আমরা নির্ণয় করতে পারি। তাহলো, যে বর্ণনাত্মক রচনায় মানুষের বাস্তব জীবনকথা লেখকের জীবনসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অভিব্যক্ত হয়, তাকেই উপন্যাস বলে।
ঘটনামূলক ও বর্ণনাধর্মী হওয়ায় গদ্যভাষাই উপন্যাসের প্রকাশবাহন। মানুষের জীবন জটিল, সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র। জীবনবৈশিষ্ট্যের বহুমুখী রূপের প্রতিফলন ঘটায় প্রতিটি উপন্যাসের আয়তন ভিন্নধর্মী। রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ এবং ‘শেষের কবিতা’ বিচার করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, উপন্যাস কেবল কাহিনী কিংবা ঘটনামাত্র নয়। মানুষের জীবনে অসংখ্য ঘটনা ঘটে।
কোনো ঘটনা যৌক্তিক শৃঙ্খলাযুক্ত আবার কোনোটার মধ্যে তা থাকেনা। এজন্যেই উপন্যাসবিধৃত ঘটনাংশের মধ্যে যৌক্তিক শৃঙ্খলা থাকতে হবে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র ও ঘটনার সমন্বয়ে একটি উপন্যাস হয়ে উঠবে যথার্থ ।
উপন্যাসের উপাদান ও গঠনকৌশল
উপন্যাসের উপাদানের সংখ্যা ৭। এর মধ্যে শরীরী উপাদানের (Concrete elements) সংখ্যা ৬। যেমন, প্লট (plot), চরিত্র (Character), দৃষ্টিকোণ ( Point of view), পশ্চাৎপট (Back ground ), সময় (Time), এবং ভাষা (Language)। উপন্যাস বিশেষণে অশরীরী উপাদান ( Abstruct elements) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে লেখকের জীবন সম্পর্কিত দর্শনকে।
প্লট
ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে গ্রীক সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক অ্যারিস্টটলের প্লটসম্পর্কিত ধারণার প্রভাবই ছিলো সর্বাধিক। অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থে প্লটের আলোচনায় বলেছেন – একটি মাত্র কর্মের সমগ্র রূপ অনুকৃত হয় প্লটে। বিভিন্ন অংশের মধ্যে গঠনগত ঐক্য এমনভাবে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়, যার ফলে একটি অংশকে তার ভেতর থেকে স্থানান্তরিত করলে প্লটের সমগ্র গঠনটিই ভেঙে পড়বে
(So the plot being an imitation of an action, must imitate one action and that a whole, the structural vision of the parts being such that, if any one of them in displaced or removed, the whole will be disjoined and disturbed)।
অ্যারিস্টটলের মতে প্লট একটি সমগ্র ও সম্পর্ক ‘কর্ম’ (Action), অন্যত্র তিনি বলেছেন, প্লট হচ্ছে ঘটনাবলীর বিন্যাস (Arrangement of incidents) এবং এই ঘটনাবিন্যাসে আদি, মধ্য এবং অন্তের মধ্যে থাকবে ঐক্য। তিনি প্লটকে সরল (Simple) ও জটিল (Complex) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। তাঁর জটিল প্লটের ধারণা প্লটভাবনার পরবর্তী রূপান্তরের সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করেছিলো।
চরিত্র
উপন্যাসের শরীরী উপাদানসমূহের মধ্যে চরিত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা, উপন্যাস মানুষের সৃষ্টি এবং অন্তর-বাহির সমেত মানব-মানবীর সমগ্র জীবনের রূপায়ণের প্রয়োজনবোধই উপন্যাসের জন্মকে সম্ভব করে তুলেছিলো। অ্যারিস্টটল চরিত্র অপেক্ষা প্লটকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ট্র্যাজেডির গঠনবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ছয়টি অংশ প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন, প্লট, চরিত্র, ভাষা, ভাবনা ( Thought), দৃশ্য এবং সঙ্গীত।
প্রথমে তিনি প্লটের আলোচনা করেছেন। অতঃপর চরিত্রের । কিন্তু পট যে জীবনের কাজের অনুকরণ, তা নিঃসন্দেহে মানুষের। অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টান্তের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটল চরিত্রের প্রকৃত ক্ষেত্রটি নির্দেশ করতে পেরেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকরা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ বর্ণনাকে (Narration) অধিক গুরুত্ব দিতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অনেক উপন্যাসেও বর্ণনাবাহুল্য চোখে পড়ে।
কিন্তু বর্ণনার মধ্য দিয়ে চরিত্রের বাইরের অবয়ব, গতিবিধি, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলিই উপস্থাপন করা যায়। চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের জন্যে বর্ণনার অতিরিক্ত আরো কিছু প্রয়োজন। জর্জ মেরিডিথ এই ভাবনা থেকেই সম্ভবত বলেছিলেন: ‘কেবল চোখের পাতায় রঙ দিলেই চলবে না, চোখের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিও ফোটাতে হবে।’ ফরাসি বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবোত্তর কালে মানুষের ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসেও চরিত্রের অবস্থান দৃঢ়তর হতে থাকে।
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রের রূপায়ণ মূলত বর্ণনাধর্মী। চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা সমাজ, উপন্যাসবিধৃত ঘটনা এবং ঔপন্যাসিকের আদর্শবোধের কাছে দায়বদ্ধ। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসে আয়েষা চরিত্র সম্পর্কে লেখকের উক্তি: ‘যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েষা।’ অর্থাৎ পুরো উপন্যাসে আয়েষা ঘটনার প্রয়োজনে উপস্থাপিত। আপন ব্যক্তিত্ত্ব ও কর্মধারায় সে স্বাবলম্বী নয়।

উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ (Point of view)
বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য উপন্যাসতাত্ত্বিকদের মতে দৃষ্টিকোণই হলো উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপাদান। ঘটনাংশ, চরিত্র কিংবা অন্যান্য উপাদানের উপস্থাপন কৌশল নির্ভর করে দৃষ্টিকোণের ওপর। ঔপন্যাসিকের জীবনকে দেখা এবং দেখানোর পদ্ধতি দৃষ্টিকোণই নির্ধারণ করে দেয়।
উপন্যাস রচনার প্রথম পর্যায়ে ঘটনার যে বর্ণনাত্মক (Narrative) উপস্থাপন লক্ষ করি, সেখানে সমস্ত ঘটনা, চরিত্রের গতিপ্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ লেখক স্বয়ং বিধৃত করতেন। অতঃপর উপন্যাসে মানবচরিত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর প্রধানত কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ ঘটতে থাকে। স্মৃতিমূলক কিংবা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে মুখ্য চরিত্র নিজেই নিজের কথা বিধৃত করে।
সমগ্র ঘটনার ওপর লেখকের দৃষ্টির একক নিয়ন্ত্রণ কিংবা মুখ্য চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও তৃতীয় কোন চরিত্রও ঘটনা বর্ণনা করতে পারে উপন্যাসে। উপন্যাসবিধৃত ঘটনা যখন লেখক নিরাসক্তভাবে প্রত্যক্ষ করে বিবৃত করেন, তখন বলা হয় লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ (Author’s Omnscient point of view)।
মুখ্য চরিত্র কিংবা নায়কের জবানিতে যখন ঘটনা বিবৃত হয়, তখন তাকে অভিহিত করা হয় উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ হিসেবে (First person’s point of view)। ঘটনার প্রান্তে অবস্থানকারী কোনো চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলে বলা হয়, প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ( Peripherid character)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন প্রখ্যাত উপন্যাসতত্ত্ববিদ পার্সি লুবক তাঁর Craft of Fiction (১৯২১) গ্রন্থে দৃষ্টিকোণের অনিবার্যতা প্রথম সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন।
পশ্চাৎপট (Background )
উপন্যাসবিধৃত প্রতিটি ঘটনা এবং চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি স্থান বা পটভূমিগত ভিত্তি থাকে। কোনো ঘটনা কিংবা কাজ নিরবলম্ব বা শূন্য থেকে ঘটে না। এজন্যেই ঘটনা বা বিষয়ের একটি পশ্চাৎপট অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উইলিয়াম থ্যাকারে, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট পশ্চাৎপটকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করলেন। ডিকেন্স চরিত্র ও ঘটনার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থান বা পশ্চাৎপটের বর্ণনা দিয়েছেন।
জর্জ এলিয়টের কাছে পশ্চাৎপটের উপস্থিতি চরিত্র অঙ্কনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বিংশ শতাব্দীতে এই ধারণাটির ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কেউ কেউ পশ্চাৎপটকে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য দিতে চেয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের অন্য সব উপাদানের সঙ্গে সমন্বিত হয়েই পশ্চাৎপট বা স্থানের সার্থকতা। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের স্থান বা পশ্চাৎপট নাগরিক কোলাহল থেকে দূরবর্তী।
উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলোর অন্তর্জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপনে শিলং পাহাড়ের নির্জন পরিবেশের ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।
সময়
অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় যে ত্রি-ঐক্যনীতির কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে কালের বা সময়ের ঐক্যের কথাও ছিলো। তবে তাঁর কাছে ক্রিয়াগত ঐক্যই (Unity of action) সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিলো। তার পরে এসেছে স্থান (Unity of place) ও কালগত ঐক্যের (Unity of time) প্রসঙ্গ। উপন্যাস রচনার প্রথম যুগ থেকেই সময়ের তাৎপর্য লেখকের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে।
স্যামুয়েল রিচার্ডসন ‘ক্লারিসা’ উপন্যাসে পত্রলিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে সময়ের ক্রমধারাকে সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। হেনরি ফিল্ডিং-এর ‘টম জোনস’ উপন্যাসেও সময়ের ক্রম অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এঁরা সময়কে উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করেননি। ঘটনাক্রম রক্ষার ক্ষেত্রে সময়কে অনুসরণ করেছেন মাত্র।
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধব্যাপী উপন্যাসে সময়ের তাৎপর্য সচেতনভাবে স্বীকৃত হয়নি। হেনরি জেমসই প্রথম সময়কে উপন্যাসের গঠনগত ঐক্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন। বালজাকের উপন্যাস আলোচনায় তিনি সময় রহস্যের স্বরূপ সন্ধান করেছেন।
উপন্যাসের ভাষা ও পরিচর্যারীতি
জন্মলগ্ন থেকেই যে উপাদানের কারণে উপন্যাস অন্যান্য সাহিত্যরূপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠলো, সে হলো তার ভাষা। কাহিনী, গল্প, চরিত্র প্রভৃতি উপাদানগুলো ট্র্যাজেডি কিংবা মহাকাব্যের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু জীবনের বাস্তবমুখী, কৃত্রিম, জটিল ও বহুকৌণিক রূপ অঙ্কনের প্রয়োজনে গদ্যভাষা হলো উপন্যাসের প্রকাশমাধ্যম। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবনসৃষ্টির সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
উপন্যাসের বর্ণনা (Narration), পরিচর্যা (Treatment), স্থান বা পশ্চাৎপট উপস্থাপন, চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ে অনিবার্য ভাষারীতির প্রয়োগ যে কোনো ঔপন্যাসিকের কাম্য। উপন্যাসবিধৃত বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমেই কোনো উপন্যাস যথার্থ ও সমগ্র হয়ে ওঠে। এই ভাষাই একটি উপন্যাস থেকে আরেকটি উপন্যাসকে, একজন লেখক থেকে আরেকজন লেখককে পৃথক করে দেয়।
অন্তর্ময় জীবনধর্মে পরিপুষ্ট কবিপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ এবং বুদ্ধদেব বসুই যে উপন্যাস-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ কথক তা বলা যাবেনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্র রুক্ষ কঠোর গদ্যও উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা। এই ভাষা ব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গতিশীলতার প্রমাণ বিচিত্র পরিচর্যারীতির উদ্ভাবন।
উপন্যাসের বিষয়, চরিত্র ও স্থান ও সময়স্বভাবকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন বোধ থেকেই বিচিত্র পরিচর্যারীতির উদ্ভাবন হয়েছে। এই সব পরিচর্যাকে বর্ণনাত্মক ( Narrative), কাব্যানুগ (Poetic), নাট্যিক ( Dramatic), চিত্রময় (Pictorial), প্রতীকী (Symbolic), বিশেষণাত্মক (Analytical) প্রভৃতি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে।
জীবনদর্শন, জীবনার্থ বা জীবনধারণা
উপন্যাসের অশরীরী উপাদান (Abstract Elements) হিসেবে জীবনদর্শনের তাৎপর্য বিশেষণ করলে অন্য সব শরীরী উপাদানকেও তা ছাড়িয়ে যায়। লেখকের ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তি অনুভূতি এবং জীবন, সময় ও সমাজসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির অন্তঃসারকে আত্মস্থ করে গড়ে ওঠে লেখকের জীবনদর্শন বা জীবনার্থ।
ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন তিনি যে কেবল সাধারণভাবে একটি আদর্শ নৈর্ব্যক্তিক মানুষ রচনা করেন তা নয়, তিনি আপন সত্তারই একটি ভাষ্য (Implied Version) রচনা করেন। সত্তার অন্তর্নিহিত এই ভাষ্য অন্য সাহিত্যরূপ গুলোতে থাকলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তার মূল্য স্বতন্ত্র। ঔপন্যাসিকের অন্তর্নিহিত এই লেখকসত্তাকে ‘দ্বিতীয় সত্তা’ হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে।
একজন লেখকের প্রতিটি উপন্যাসে এই লেখক-সত্তার প্রকাশ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পায়। শরীরী উপাদানগুলোর যৌথ ব্যবহারের অনিবার্যতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মূলত তাঁর জীবনসম্পর্কিত তত্ত্ব বা দর্শনকেই প্রকাশ করেন। উপন্যাস রচনার প্রথমযুগে বর্ণনার ( Narration) প্রতি অতি মনোযোগের ফলে অন্যান্য শরীরী উপাদানের মতো জীবনদর্শনের প্রশ্নটিও অনুচ্ছারিত থেকে যেত।
কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পৃথিবীর সব ভাষার উপন্যাসে লেখকের জীবনদর্শনের প্রকাশ তীব্রতর হতে থাকে। কেউ ইতিহাস, কেউ সমকালীন সময় ও সমাজ, আবার কেউ কেউ ব্যক্তির কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে এই দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় উপন্যাসেই জীবনসম্পর্কিত একটা বক্তব্য আছে। কিন্তু দু-একটি উপন্যাস বাদে অন্য সব উপাদানের সমন্বয়ে তা যথার্থ হয়ে ওঠে নি।
রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসের বিশ্বজনীনতার তত্ত্বটি আমাদের জানা। এ উপন্যাসে ঘটনা, অপরাপর চরিত্র এবং সমাজজীবনের বিস্তৃত পরিসরকে কেন্দ্র করে গোরা চরিত্রের মানসবৈচিত্র্য ও উত্তরণ দেখানো হয়েছে। গোরার উত্তরণ বা মীমাংসায় উন্নীত হওয়ার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনসম্পর্কিত দর্শন প্রকাশ করেছেন।
‘শেষের কবিতা’ রীতির দিক থেকে কাব্যধর্মী হলেও প্রেমের চিরন্তনতার যে তত্ত্ব এ-উপন্যাসের শেষে উচ্চারিত হয়েছে, তা আসলে রবীন্দ্রনাথেরই জীবনদর্শন । এ-ভাবেই আধুনিক উপন্যাসে জীবনদর্শনের অনিবার্যতা স্বীকৃত হয়েছে।
বস্তুসংক্ষেপ:
যে বর্ণনাত্মক রচনায় মানুষের বাস্তব জীবনকথা লেখকের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অভিব্যক্ত হয়, তাকেই উপন্যাস বলে। ঘটনামূলক ও বর্ণনাধর্মী হওয়ায় গদ্যভাষাই উপন্যাসের প্রকাশবাহন। মানুষের জীবন জটিল, সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র। জীবন বৈশিষ্ট্যের বহুমুখী রূপের প্রতিফলন ঘটার জন্য প্রতিটি উপন্যাসের আয়তন ভিন্নধর্মী । জন্মলগ্ন থেকেই যে উপাদানের কারণে উপন্যাস অন্যান্য সহিত্যরূপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, তা হল তার ভাষা।
কাহিনী, চরিত্র প্রভৃতি উপাদানগুলো ট্রাজেডি কিংবা মহাকাব্যের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জীবনের বাস্তবমুখী, কৃত্রিম, জটিল ও বহুকৌণিক রূপ অঙ্কনের প্রয়োজনে গদ্যভাষা হল উপন্যাসের প্রকাশমাধ্যম। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবন সৃষ্টির ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
উপন্যাসের বর্ণনা, পরিচর্যা, স্থান বা পশ্চাৎপট উপস্থাপন, চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ে অনিবার্য ভাষারীতির প্রয়োগ যে কোন ঔপন্যাসিকের কাম্য। উপন্যাসবিধৃত বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমেই কোন উপন্যাস যথার্থ ও সমগ্র হয়ে ওঠে।
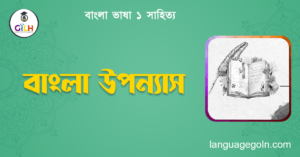
পাঠোত্তর মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করুন।
২. উপন্যাসের অশরীরী উপাদানের স্বরূপ নির্দেশ করুন।
৩. উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করুন এবং প্রধান প্রধান শ্রেণীর পরিচয় দিন।
৪. উপন্যাসের প্লট কাকে বলে।
রচনামূলক প্রশ্ন
১. উপন্যাসের শ্রেণীকরণ সম্পর্কে যা জানেন বিস্তারিত লিখুন ।
২. উপন্যাসের প্লট ও চরিত্র বিষয়ে যা জানেন নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।