আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সহিত্যের শ্রেণীবিভাগ
সহিত্যের শ্রেণীবিভাগ
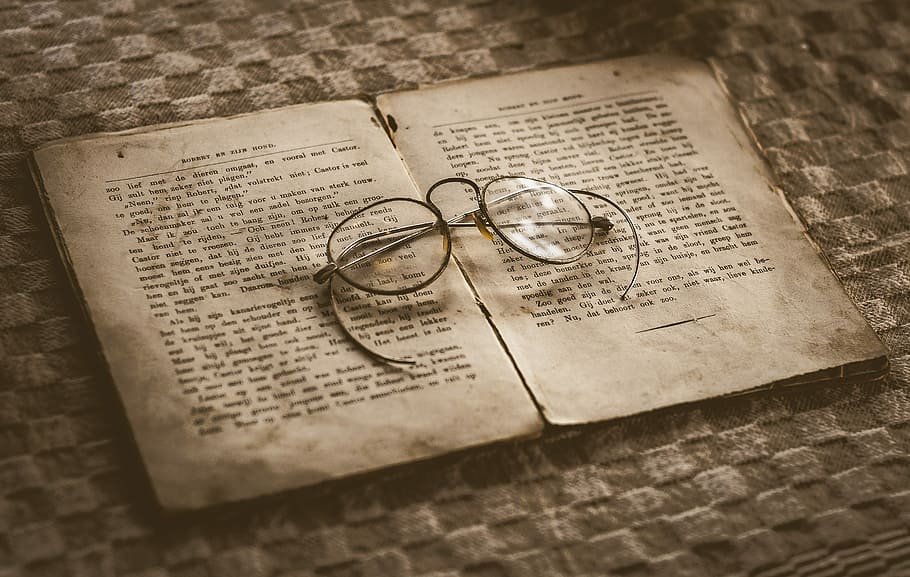
সহিত্যের শ্রেণীবিভাগ
সংজ্ঞার্থ
ইংরেজি Literature-এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা সাহিত্য শব্দটির ব্যবহার করে থাকি। ভাষার সৌন্দর্য ও আবেগের ক্রিয়াশীলতা যখন শব্দের আশ্রয়ে রূপ লাভ করে তখনই প্রকৃত সাহিত্যের জন্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার লেখকরা সাহিত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা একটি বিষয়ে অভিন্ন; তাহলো, সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট শিল্প।
মানবজীবনে সংঘটিত বিচিত্র ঘটনা এবং বস্তুজগতের উপকরণ সাহিত্যের অবলম্বন হলেও দৈনন্দিনতা ও স্থূলতাকে অতিক্রম করে চিরন্তন হয়ে ওঠে। যেমন ইতিহাসে মানবজীবনের ঘটনার সমাবেশ আছে, কিন্তু তা ঘটনার ব্যঞ্জনা বা সত্য অপেক্ষা বিবরণকেই প্রাধান্য দেয়। বস্তুগত উপকরণ দিয়ে আমরা তৈরি করি অট্টালিকা, যানবাহন, গৃহের আসবাবপত্র প্রভৃতি। ঘটনার বিবরণ তৈরি বা গড়ে তোলায় স্রষ্টার কোনো কৃতিত্ব নেই।
কিন্তু সাহিত্যে এ-সব বিষয়ই লেখকের কল্পনা, সৃজনশীলতা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা প্রভৃতির আশ্রয়ে সৃষ্ট হয়, যা একই পাঠককে বার বার তৃপ্ত করতে সক্ষম। কিন্তু ঘটনার বিবরণ ও বস্তুগত প্রয়োজনে মানুষের গভীরতম আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয় না । সাহিত্য হয়ে ওঠা সম্পদ- — তার গ্রহনযোগ্যতা শিল্পগত (Art) সৌন্দর্যের ওপর নির্ভরশীল। সাহিত্য ব্যাপক ও বিচিত্র একটি ধারণা। রূপের বহুমুখিতা এর বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।
প্রতিটি মানুষ মাথা গণনায়ই কেবল স্বতন্ত্র নয়, অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিচারেও পৃথক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। সাহিত্যস্রষ্টাও একজন মানুষ। অনুভূতি, সংবেদন, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাচারিতায় সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। এজন্যে সাহিত্যিকদের বলা হয়, সমাজের অগ্রসর চেতনার প্রতিভূ। অতীত স্মৃতি, অধীত জ্ঞান, বাস্তব-অভিজ্ঞতা এবং সমকালীন জীবন থেকে উপকরণ আহৃত হলেও একজন সাহিত্যিকের লক্ষ্য ভবিষ্যতকে স্পর্শ করা।
আত্মপ্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা মানুষের মৌলিক প্রবণতাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই প্রবণতা মানুষকে সামাজিক হতে সহায়তা করে। একজন সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকেই সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। কবি তাঁর অনুভূতি, আবেগ ও কল্পনাকে অনিবার্য শব্দসমবায়ে উপস্থাপন করেন কবিতায়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য শব্দের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করি।
অভিধানের ভেতরেও ঘরে ঘরে সাজানো থাকে অজস্র শব্দের কংকাল। কবির কল্পনা ও সৃজনীশক্তি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দের মধ্য থেকে বেছে নেয় অনিবার্য কিছু শব্দ। আর অভিধানের মৃত শব্দের স্তূপ থেকে কবিতার শরীরে স্থাপন করে শব্দের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন একজন কবি। এভাবেই মানুষের বস্তুময় জীবনের অন্তরালে মন ও কল্পনার এক ভাবময় জগৎ সৃষ্টি করেন কবি।
কবিতায় কবি এবং পাঠকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কিছু অনিবার্য, প্রাণময় শব্দ । নাটকের উপাদানের পরিসর কবিতার তুলনায় ব্যাপক। নাট্যকার, চরিত্র বা অভিনেতা, মঞ্চ এবং দর্শক বা শ্রোতার সমবায়ে নাটকের সৃষ্টি। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকের উপাদানও জীবন থেকে গৃহীত হয়। মানুষের জীবন, তার স্বভাব, পরিপার্শ্ব, সমাজ এমনকি রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাটকের উপাদান কিংবা নাটকীয়তা বিদ্যমান ।
নাট্যকার সে-সব ক্ষেত্র থেকেই আহরণ করেন নাটকের উপাদান। কিন্তু মনে রাখতে হবে নাটকীয় উপাদান কোনো নাটকের সার্থকতার মানদন্ড নয়। নাটকের আঙ্গিক বা রীতির অনুশাসন সাহিত্যের অন্যান্য রূপ বা আঙ্গিক অপেক্ষা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণপ্রবণ। গল্প, কবিতা, কিংবা উপন্যাস মানুষ একা কিংবা সম্মিলিতভাবে পাঠ ও উপভোগ করতে পারে। কিন্তু নাটক উপভোগের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, সময় এবং সমষ্টিগত উপস্থিতির প্রয়োজন।
এ-কারণে নাটকের গঠনকৌশল সুনিরূপিত, কঠোর ও সতর্ক। নাটক নিয়মের অনুসারী – যার সঙ্গে রয়েছে মঞ্চ এবং অভিনয়ের সম্পর্ক। Performing Art বা প্রয়োগ-সাপেক্ষ শিল্প হিসেবে নাটক একটা স্বতন্ত্র রূপ ও রীতির অনুসারী। বর্তমান কালে সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় আঙ্গিক হলো উপন্যাস। এর কারণ কেবল উপন্যাসের গঠন বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত নয়, সাহিত্যের অন্য সব শাখার কোনো-না-কোনো বৈশিষ্ট্যের একত্র মিলনও এ-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
গল্পের বর্ণনাধর্মিতা যেমন উপন্যাসে বিদ্যমান, তেমনি রয়েছে কবিতার অন্তর্ময়তা। নাটকের আকস্মিকতা, সংলাপ, জীবনের আকর্ষণীয় মুহূর্তের নাটকীয় উপস্থাপনও উপন্যাসের শিল্পস্বভাবের অংশ। আবার মননশীল প্রবন্ধের বিশেষণ-ধর্মিতা ও জটিল মানব-অস্তিত্বও তার স্বরূপ উন্মোচনের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বাস্তব পৃথিবীর ঘটনা, চরিত্র, জীবনের বিচিত্র রূপের বিন্যাস ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রূপায়িত হয় উপন্যাসে।
উপন্যাসের উদ্ভব আধুনিক নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক জীবনের জটিল, দ্বন্দ্বময় ও বহুমুখী সত্য রূপদানের প্রয়োজনচেতনা থেকে উপন্যাসের সৃষ্টি। যে কারণে উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয় যথেষ্ট কঠিন। প্রতিটি উপন্যাসই বিষয়বস্তু ও শিল্পস্বাতন্ত্র্যে অন্য উপন্যাস থেকে পৃথক। তবুও ঘটনাংশ বা plot নির্বাচন, চরিত্রসৃষ্টির কৌশল, ঔপন্যাসিকের জীবন দৃষ্টির মৌলিকত্ব, জীবন সম্পর্কে একটি দর্শন সন্ধানের ঐকান্তিক আগ্রহ উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে।
গল্প বলা এবং শোনা মানুষের চিরকালীন প্রবণতা হওয়া সত্ত্বেও ছোটগল্পের সৃষ্টি সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা বেশ পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাসে আমরা জীবনের যে বিস্তৃত রূপের প্রতিফলন দেখি, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই ছোটগল্পে তা সম্ভব নয়। জীবনের বহুমুখী সত্য উপন্যাসের উপজীব্য। আর ছোটগল্পে বিধৃত হয় জীবনের একান্ত গভীর কোনো একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ছোটগল্পের জীবন খন্ডিত, অপূর্ণ।
উপন্যাসকে আমরা তুলনা করতে পারি মানুষের সমগ্র জীবনের সাথে, যেখানে অসংখ্য ঘটনা, অভিজ্ঞতা, সংঘাত ও সংগ্রামের সমাবেশ। আর ছোটগল্প সেই বিশাল জীবনের একটি অংশ যারও পূর্ণতা আছে, যার মধ্যদিয়েও জীবনের কোনো একটি সত্যের সমগ্রতা অনুধাবন করা যায়। এজন্যেই বলা হয়, উপন্যাসে আমরা সন্ধান করি জীবনের সম্পূর্ণতা (Entirety) আর ছোটগল্পে সমগ্রতা (Totality)।
প্রবন্ধ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কোনো সংক্ষিপ্ত গদ্য-রচনা, যা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকে। কখনো কখনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে আবার কখনো-বা বিষয়ের অন্তর্গত বক্তব্য বিশেষণের মাধ্যমে পাঠককে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। কবিতা, নাটক, গল্প, কিংবা উপন্যাসকে বলা হয় সৃজনশীল সাহিত্যরূপ। আর প্রবন্ধের উপকরণ ও প্রকরণের বৈশিষ্ট্য সৃজনশীলতার স্বভাবধর্ম থেকে দূরবর্তী।
প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি কিংবা রাজনীতি। ইংরেজিতে যাকে আমরা Essay বলি প্রবন্ধ অনেকটা তার সমধর্মী। প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভবের যুগে মননশীল গদ্যকার এক ধরনের ব্যাখ্যানমূলক, বিতর্কমূলক ও বর্ণনামূলক রচনার সূত্রপাত করেন, যাকে বলা হতো ‘প্রস্তাব’। রামমোহন রায়, , বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষী তাঁদের ‘প্রস্তাব’ সমূহে সমাজজীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।
ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-বিশেষণও রামগতি ন্যায়রত্ন ‘প্রস্তাব’-এর রূপ বা Form কেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রবন্ধকার আলোচ্য বিষয়ের ওপর নিরাসক্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যুক্তিশৃঙ্খলায় বিষয় বিশেষণ করেন। ফলে, আধুনিক চিন্তাশীল বিশ্বে প্রবন্ধের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবন্ধকার সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকে যেমন বিশেষণ করেন, তেমনি শিল্প ও জীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বিশেষণ করেন।
উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট। তা হলো সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিকেরই বিষয়বস্তু মানুষের বহুধা-বিস্তৃত জীবন। কিন্তু প্রকরণের ধর্ম সেই মানবজীবন-সত্যকেই স্বতন্ত্র রূপাঙ্গিকে বিন্যস্ত করে। কবিতা মূলত অন্তর্ময় মানুষের আবেগ-কল্পনা-অনুভূতির সূক্ষ্মতর বিন্যাস তার অন্বিষ্ট। নাটকে দেখবো নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ ও দর্শক একটা সামবায়িক শিল্পক্ষেত্র রচনা করেছে।
গল্প এবং উপন্যাস সাহিত্যের সকল আঙ্গিকের স্বভাব আত্মস্থ করে জীবনের ব্যাপক ও গভীর রূপের উন্মোচন-প্রয়াসী। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ এবং বি.এস.এস. প্রোগ্রামের বাংলা ভাষা (সাধারণ শিক্ষা কোর্স) পাঠক্রমে সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকের রচিত কালজয়ী কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের নির্বাচিত পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ধারণা দেওয়াই এই পাঠক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্য। স্বশিক্ষণে-আগ্রহী শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত মূলপাঠ, তার উদ্দেশ্য, পাঠোত্তর মূল্যায়ন, চূড়ান্ত মূল্যায়ন, প্রশ্নোত্তরের নমুনা, টীকা প্রভৃতি থেকে প্রতিটি সাহিত্যশাখা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবনের দিকনির্দেশনা পাবেন ।

সাহিত্যের যে কোনো রূপ বা আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দুটি মানদন্ড ধরে অগ্রসর হই:
এক : বিষয়বস্তু
দুই : শিল্পরূপ বা প্রকরণ
প্রসঙ্গ দুটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হলেও এ দুয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিল্পী বা সাহিত্যিক জীবনের বিচিত্র উৎস থেকে তাঁর অন্বিষ্ট সাহিত্যরূপের (Literary form) উপকরণ আহরণ করেন। ব্যক্তির অস্তিত্বগত অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার বহুকৌণিক সত্যকেই মূলত লেখকের অবলম্বিত সাহিত্যরূপে স্থান দেওয়া হয়। এ- ক্ষেত্রে লেখক জীবনকে কিভাবে দেখেন এবং উপস্থাপন করেন সেটাই প্রধান বিবেচ্য।
অভিন্ন উপকরণ নিয়ে একাধিক লেখক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু বিষয়চেতনা ও শিল্পরূপের ভিন্নতা প্রত্যেক লেখকের সৃষ্টিকেই স্বতন্ত্র করে তোলে। যেমন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে আমাদের সাহিত্যিকরা অসংখ্য কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উপকরণ অভিন্ন হলেও লেখকের চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, উপস্থাপনরীতি প্রত্যেক সৃষ্টিকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।
ভাষা আন্দোলনের রজাত অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত হাসান হাফিজুর রহমানের ‘অমর একুশে’ (বর্তমান পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত) এ-বিষয়ক অসংখ্য কবিতার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কবির দেশপ্রেম, ভাষা-শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, তৎকালীন স্বৈরশাসকের প্রতি তীব্র ঘৃণা কবিতাটির বিষয়বস্তুকে অসাধারনত্ব দান করেছে। কবিতাটির ভাষা, শব্দব্যবহার ও চিত্ররচনায় বিষয়বস্তু প্রকাশের উপযোগী অনিবার্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে।
যেখানে ক্রোধ ও সংগ্রামী চেতনা প্রকাশিত সেখানকার ভাষা নিরাবেগ, তৎসম শব্দবহুল এবং তীক্ষ্ম। আবার স্বজন হারানোর বেদনাময় ভারাক্রান্ত, অশ্রুসিক্ত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে সরল-সহজ শব্দসমবায়ে, মাতৃ-মমতার উপযোগী সহজাত ভাষার বিন্যাসে। মুনীর চৌধুরী রচিত ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ নাটকের উপাদান বা উপকরণ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। এই ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে একাধিক রচনা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।
কিন্তু মুনীর চৌধুরীর নাটকটির অভিনবত্ব এর বিষয়চেতনা। যুদ্ধের ঘটনাকে নাট্যকার মানবীয় প্রেম ও যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী আকাঙ্ক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’র উপকরণ নর-নারীর প্রেমসম্পর্ক। উপন্যাসে বহুল ব্যবহৃত এই সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ মানব প্রেমের এক চিরন্তন বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। যে প্রেম প্রাপ্তির সীমায় বন্দি, তা ক্ষণিক ও ভঙ্গুর সংকীর্ণ চাওয়া-পাওয়ার সীমাযুক্ত প্রেম মানবিক চেতনাকে করে তোলে অনন্তমুখী।
সময়ের চলমানতায় সে-প্রেম চিরকালের মানব-মানবীর। সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে বিধৃত বিষয়বস্তুকে অনিবার্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে লেখককে সন্ধান করতে হয় যথার্থ প্রকরণ বা শিল্পরূপ । তা না হলে সাহিত্য কেবল বিষয়ের বর্ণনায় পরিণত হবে। ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনা-প্রধান বলেই তার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী হয় না । ‘ অমর একুশে কবিতা হয়ে ওঠার কারণ ইতিহাসের ঘটনার অন্তঃসারকে কবি অনিবার্য শিল্পপ্রকরণে উন্নীত করেছেন। ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ নাটকের ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য।
সাহিত্যের বিষয়বস্তু (Content) ও আঙ্গিক (Form) অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। যে কারণে বিষয়বস্তু প্রকাশ-উপযোগী আঙ্গিক সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে সে-সাহিত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়না। রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ কবিতায় যে চলমান জীবনসত্যের বিন্যাস ঘটেছে, এর শব্দব্যবহার ও ছন্দে সেই গতি বা প্রবহমানতাকেই অনিবার্যতা দান করা হয়েছে । মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় বিষয়বস্তু ভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেম।
কিন্তু সনেটের আঙ্গিক সৃষ্টিতে কবির সামগ্রিক সফলতা কবিতাটির আবেদনকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। এজন্যেই বলা যায়, বিষয়বস্তু যত গভীর ও ব্যাপক হোক না কেন আঙ্গিক, প্রকরণ বা শিল্পরূপের সম্পন্নতা ছাড়া কোনো সাহিত্য সৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।
বস্তুসংক্ষেপ
সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট শিল্প। সাহিত্য ব্যাপক ও বিচিত্র একটি ধারণা। সাহিত্যের যে কোন রূপ বা আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রে সাধারণত বিষয়বস্তু এবং শিল্পরূপ বা প্রকরণ— এ দুটি মানন্ড বিবেচ্য। সাহিত্যের বিষয়বস্তু (Content) ও আঙ্গিক (Form) অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে বিষয়বস্তু প্রকাশে উপযোগী আঙ্গিক সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে সে সাহিত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিকেরই বিষয়বস্তু মানুষের বহুধাবিস্তৃত জীবন।
কিন্তু প্রকরণের ধর্ম সেই মানবজীবন-সত্যকেই স্বতন্ত্র রূপাঙ্গিকে বিন্যস্ত করে। যেমন, কবিতায় মানুষের আবেগ-কল্পনা-অনুভূতির সূক্ষ্মতর বিন্যাস নিহিত থাকে। নাটকে দেখা যায়, নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চ ও দর্শক একটা সামবায়িক শিল্পক্ষেত্র রচনা করেছে। গল্প এবং উপন্যাস সাহিত্যের সকল অঙ্গিকের স্বভাব আত্মস্থ করে জীবনের ব্যাপক ও গভীররূপের উন্মোচন প্রয়াসী।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. সাহিত্য বলতে আমরা কি বুঝি?
২. সাহিত্যরূপ শব্দবন্ধটি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?
৩. সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে উপকরণ, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে আমরা কেন স্বতন্ত্র করে দেখি?
৪. সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর রূপগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৫. সাহিত্যের বিষয়বস্তু (Content) কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যা জানেন নিজের ভাষায় লিখুন।
২ নং সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের নমুনা উত্তর
বিষয়বস্তু ও গঠন-বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়েছে। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের একেকটি রূপ বা Form । এই রূপ বা গঠনগত স্বাতন্ত্র্যের কারণেই প্রতিটি সাহিত্য-আঙ্গিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। যেমন কবিতার রূপ গড়ে ওঠে তার ভাবনিষ্ট অন্তর্ময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে। প্রবন্ধের অবস্থান তার বিপরীত মেরুতে। প্রবন্ধ বস্তুনিষ্ট ও বিশেষণধর্মী।
