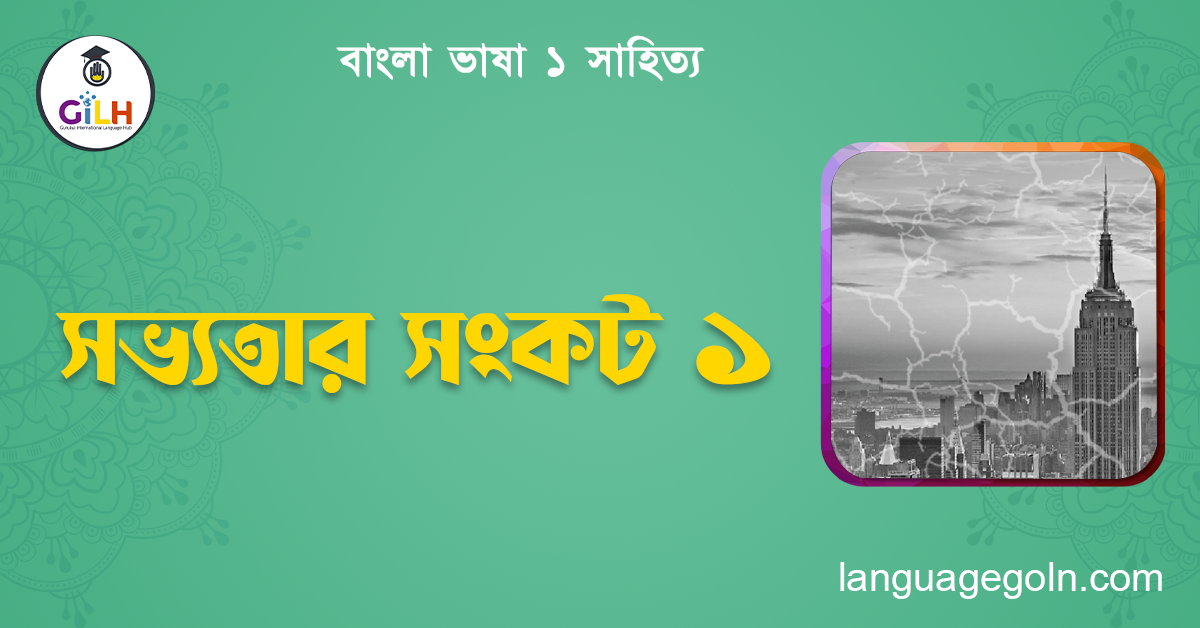রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ প্রবন্ধ রচনা ‘সভ্যতার সংকট’। এখানে প্রবন্ধকার নিজের গোটা জীবন-পরিসরের উপর আলোক প্রক্ষেপণ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র তুলে ধরেছেন। জীবনের অন্তিমকালে এসে প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ এমন মত ব্যক্ত করেছেন, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত, প্রতীচ্য সভ্যতায় আস্থা পুনর্ঘোষিত। তবে মানুষের উপরই তার অন্তিম নির্ভরতা স্থাপন। কারণ, তিনি মনে করেন, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’।
সভ্যতার সংকট
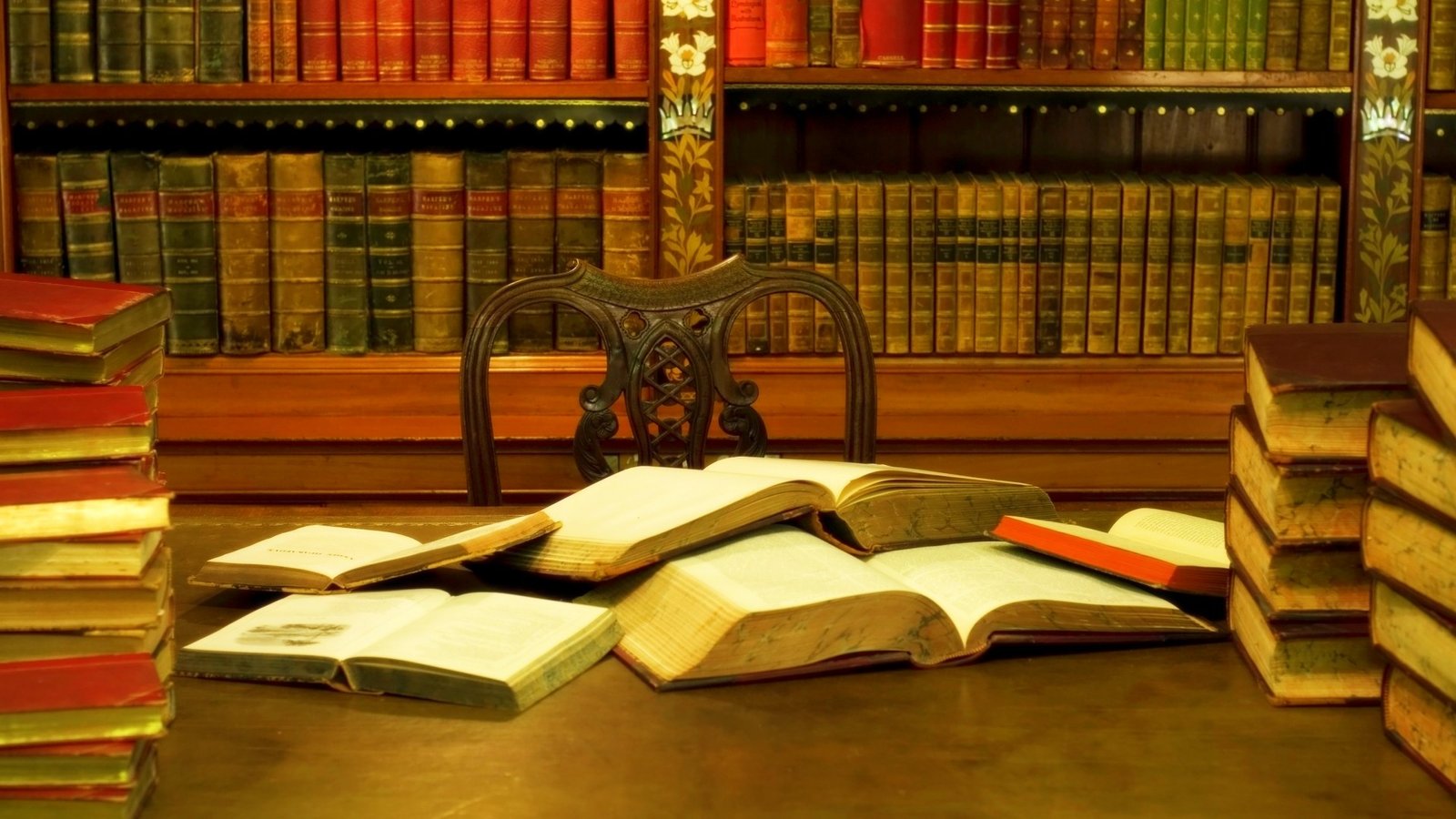
লেখক পরিচিতি
আপনারা ইতোপূর্বে ইউনিট-২-এর বলাকা শীর্ষক পাঠে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জেনেছেন। রবীন্দ্র-জীবনী সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে কবির স্বপ্রণীত-জীবনীগ্রন্থ ‘আমার ছেলেবেলা’ ও ‘জীবনস্মৃতি’ নামক গ্রন্থ দুটি পাঠ করতে পারেন ।
পাঠ পরিচিতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ। ওই বছরই তাঁর একাশিতম জন্মদিনে প্রবন্ধটি পঠিত হয়। রবীন্দ্র – জীবনীকারদের ভাষ্য মতে, এটিই তাঁর রচিত সর্বশেষ প্রবন্ধ। পরে ‘কালান্তর গ্রন্থে প্রবন্ধটি স্থান পায়। সর্বমোট দশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা প্রায় আঠারো শত।
এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ইংরেজদের লালিত ও প্রচারিত সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার কথা তুলে ধরে প্রাচ্যের নিজস্ব কৃষ্টির উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। জীবনের প্রান্তিকে রচিত বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে, এ সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনোপলব্ধিজাত ।
‘সভ্যতার সংকটে’র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর আশি বছর পূর্ণ হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর জীবনের ও দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। এতে দুঃখবোধের কারণ আছে। প্রবন্ধকার বলেছেন, তাঁর দেশ বা উপমহাদেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদিতে যে ব্যাপক অগ্রসরতার সূচনা হয়েছিলো তা মূলত ইংরেজদের কল্যাণে। আর এ জন্যে ওই সময় বাঙালিরা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলো যে, ইংরেজদের ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যেই বুঝি ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হবে।
অবশ্য তখনো ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত-স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, তরুণ বয়সে ইংল্যান্ড গমন করে তাদের সম্পর্কে জেনে, বিশেষ করে পার্লামেন্টারিয়ান জন ব্রাইটের বক্তব্য শুনে তিনি ইংরেজদের হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও জাতিগত অসংকীর্ণতা আবিষ্কার করে মোহাবিষ্ট হন। ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নও তাঁকে জ্ঞানসম্পদবান করে তোলে।
প্রবন্ধকার এখানে ‘সভ্যতা’ বলতে ইংরেজি ‘সিভিলিজেশন’-এর অযথার্থ বঙ্গানুবাদের কথা উলেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর শৈশবে শিক্ষিত সমাজে বাহ্য আচরণ বিরোধী একটা মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এতে ইংরেজদের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিএগুলেও এর প্রভাব পড়ে। অথচ, প্রাচীন ভারতে এই ‘সভ্যতা’-কেই বলা হতো ‘সদাচার’।
প্রবন্ধের পঞ্চম অনুচ্ছেদ থেকে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের বোধজগতে কালক্রমে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার উল্লেখ আছে। নিরন্ন, হীনস্বাস্থ্য ভারতবাসীকে শাসক ইংরেজদের শোষণ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে তিনি ব্যথিত হন। আবিষ্কার করেন, ইংরেজগণ বিশ্বজুড়ে যে আধিপত্য বিস্তার করেছে তা নৈতিক শক্তিরমারা নয়, যন্ত্রশক্তি দিয়ে।
রবীন্দ্রনাথ এখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইংল্যান্ডের তুলনা করে বলেছেন যে, বহুজাতিক সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড তা করেনি। বরং ভারতে বহুজাতি ও ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ ও সন্দেহ সৃষ্টি করে দেশ শাসন করছে। তিনি ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনায় কঠোর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যে, একদিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইংরেজরা যেতে বাধ্য হবে।
তবে তখন হয়তো তারা ভারতকে শোষণ-বঞ্চনায় নিঃস্ব করে ফেলবে। জীবনের প্রথম দিকে ইউরোপের অন্তরের সম্পদ সম্পর্কে তাঁর যে উচ্চধারণা ছিলো এখানে তা তিনি পরিত্যাগ করেছেন। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো মানুষের কাছেই ফিরে গেছেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তবে সে মানুষ আর ইংল্যান্ড বা পাশ্চাত্যবাসী নয়, সে মানুষের বাস ‘পূর্ব দিগন্তে’ অর্থাৎ তারা প্রাচ্যের অধিবাসী।
মূলপাঠ
আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে- সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে। বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে।
আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে, অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই।
তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গ-ভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস।
সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যেরত্নারাই প্রশস্ত হবে। কেননা এক সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম।
তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি। আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলন্ডে গিয়েছিলেম। সেই সময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং বহুজাতিক রাষ্ট্র তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে।
এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শাখার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের বহুজাতিক রাষ্ট্র যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভান্ডারের সম্পদ নয়।
তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শৃখ আমার মনে মন্ত্রিত হয়েছে। সিভিলিজেশন, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন।
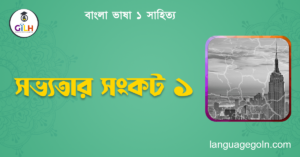
সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীন কালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখন্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে বহুজাতিক রাষ্ট্র এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত – – তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল।
সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে।
এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ – – তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে।
প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে। নিভৃতে সাহিত্যের বহুজাতিক রাষ্ট্র রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক।
অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন- চাালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে।
যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য। যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত।
অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম, জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বোতভাবে কী রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি বহুজাতিক রাষ্ট্র সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্যশাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে।
এই সভ্যতা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।
বহুসংখ্যক পরজাতির উপর প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে – এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির – আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর।
সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এই রকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়।
দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে বহুজাতিক রাষ্ট্র প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুসূট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে।
তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণকামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যচি এখনো ঘটেনি, কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ – – সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারেনি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

শব্দার্থ ও টীকা
বার্ক — জন্ম ১৭২৯, মৃত্যু ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। আইরিশ দার্শনিক ও বাগ্মী বার্ক এডমন্ড ছিলেন মূলত মানবতাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। ‘A Philosophyical Inquiry into the Sublime and Beautiful’ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।
মেকলে— জন্ম ১৮০০, মৃত্যু ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। টমাস ব্যারিংটন মেকলে একজন খ্যাতি সম্পন্ন ঐতিহাসিক ছিলেন। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের সদস্যও ছিলেন তিনি। তিনি ভারতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা ও চিন্তাকে তাঁর মতবাদ দিয়ে প্রভাবিত
করেন ব্যাপকভাবে। ‘Macaulay’s History of England’ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ।
শেপিয়র— উইলিয়াম শেপিয়রের জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইংল্যান্ডের মহাপ্রতিভাশালী কবি ও নাট্যকার। বিশ্বসাহিত্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কিং লিয়ার, মার্চেন্ট অব্ ভেনিস, ম্যাকবেথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।
বায়রন— ইংরেজ কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর কাব্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা প্রবল। ‘Child Harold’s Pilgrimage’ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ । যখন সাম্রাজ্যের বিস্তার করে, তখন সেই বিস্তারকে এবং তার সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকেই সাম্রাজ্যমদমত্ততা বলে।
সাম্রাজ্যমদমত্ততা— সাম্রাজ্য লাভ করার উগ্রতা। এই নীতিকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদীনীতি। সাধারণত শক্তিশালী রাষ্ট্র রাশিয়ার ভ.ই. লেনিন ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘Imperialism, The Highest Stage of Capitalism’ গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের সুনিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
জন্ ব্রাইট— ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তৎকালীন সদস্য।
শ্রীভ্ৰষ্ট— সৌন্দর্যহানি বা সৌন্দর্য-বিচ্যুতি।
সিভিলিজেশন— ইংরেজি শব্দ Civilization-এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘সভ্যতা’। বর্বর জীবন থেকে উন্নত হওয়া; মার্জিত রুচিবোধে পরিশীলিত হওয়া।
মুন— পৌরাণিক মনু ব্রহ্মারপুত্র; মানবজাতির আদিপুরুষ। মনু ১৪ জন। মানবের এই ১৪ জন জন্মদাতা এক-এক মতান্তরের অধিপতি। মনুগণ প্রত্যেকেই ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা।
সরস্বতী ও দৃশদ্বতী— হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দুই নদী। ব্রহ্মাবর্ত মহাভারত অনুসারে কুরুক্ষেত্রের নিকটে এবং সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন দেশ।
রাজনারায়ণবাবু — প্রকৃতনাম রাজনারায়ণ বসু। তিনি রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তবে তাঁর বড় পরিচয় একজন জাতীয়তাবাদী ও উনিশ শতকের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশের আন্দোলনের নেতা হিসেবে বেশি। তিনি হিন্দুমেলার উদ্বোধক ছিলেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে ‘আত্মচরিত’, ‘সায়েন্স অব রিলিজিয়ন’, ‘সেকাল আর একাল’ উল্লেখযোগ্য।
বস্তুসংক্ষেপ
আশি বছর অতিক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন পরিসরের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বোধ প্রকাশ করেছেন ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে। এই সুদীর্ঘ সময়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অনুভব আর মনোবৃত্তিগত খন্ডতায় তিনি দুঃখিত হয়েছেন। বাঙালি তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ মানব বিশ্বের বৃহত্তর আঙ্গিনার সঙ্গে পরিচিত হয় ইংরেজদের কল্যাণে। বার্ক, মেকলে, শেকস্পীয়র, বায়রন প্রমুখের রচনা ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এদেশীয় মানুষ প্রভূত লাভবান হয়।
ইতোপূর্বে জ্ঞানার্জনের বিচিত্রপথ কিংবা বিজ্ঞানের রহস্য ভারতবাসীর অজানাই ছিলো । বাঙালিদের একটা অংশ তখন বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন ইংরেজদের জ্ঞানস্পৃহা ও ঔদার্যে। তাঁরা মনে করতেন ভারতের স্বাধীনতাও ইংরেজ-দাক্ষিণ্যেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাল্যকালে ইংল্যান্ডে গিয়েছেন এবং ব্যাপক পরিমাণে ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করেছেন।
এসব ছাড়াও ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে রাজনীতিকদের বক্তব্য শুনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ইংরেজদের হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও জাতিগত অসংকীর্ণ চিন্তায় মোহাবিষ্ট হন। তাঁর শৈশব কালে বাঙালি শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ-অনুসৃত সভ্যতার চর্চা হিসেবে প্রথাগত আচার-বিরোধিতা দেখা দেয়। এতেও ইংরেজদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিলো প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক অবস্থান ছিলো এই নতুন মূল্যবোধের অনুকূলে।
এসবের প্রভাব ও সাহিত্যানুরাগের ফলে ইংরেজদের উচ্চাসন দান করা হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের কল্পনারাজ্যের বাইরে রবীন্দ্রনাথ যখন তাকালেন বাস্তবে, দেশের জনসাধারণের দিকে, তাঁর তখনই ইংরেজদের প্রতি মোহ ভঙ্গ হতে শুরু করে। মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্যহীন রেখে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শাসনের নামে যে কেবল শোষণই করছে এই সত্য সেসময় তিনি অনুধাবন করতে পারেন।
রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন যে, ইংরেজরা দেশ শাসন করার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এখন যন্ত্র শক্তি দিয়ে কেবল শোষণ করছে। বহুজাতিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে জাত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে মনুষ্যত্বকে গুরুত্ব দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উন্নতির নজির স্থাপন করেছে, ইংরেজরা সেখানে অন্যের সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি জিইয়ে রেখে দেশ শাসন করছে।
পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশেও সহাবস্থানের অনন্য নজির স্থাপিত।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন
১. ইংরেজ শাসনামলে কতিপয় বাঙালি ইংরেজদের ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যেরশারাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব এই মতে কেন বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন?
২. রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ কি কারণে ইংরেজদের উপর আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলো?
৩. রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত ইংরেজদের বিশ্বকর্তৃত্ব অর্জনের কারণটি চিহ্নিত করুন।
৪. বহুজাতিক রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসকদের পার্থক্য কোথায়?
২ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তর:
ভারতের শাসনভার ইংরেজরা গ্রহণ করার কারণে এই দেশবাসীর সঙ্গে ইংরেজদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতিগত সম্প্রসারণের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। ইতোপূর্বে জ্ঞানার্জনের বিচিত্র পন্থা এদেশের লোকের অজ্ঞাত হয়। প্রকৃতির রহস্যজানা বিজ্ঞানীর সংখ্যাও ছিলো না। বার্ক, মেকলে, শেকস্পীয়র, বায়রন প্রমুখের রচনা ও ইংরেজদের রাজনৈতিক ঔদার্যের সঙ্গে এ সময় বাঙালি শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটে। সর্ব মানবের বিজয় ঘোষণার রাজনৈতিক ঐতিহ্য ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়। এ-সব কারণে এক সময় বাঙালি শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ ইংরেজদের উপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তারা এমনও ভাবতে থাকে যে, ভারতের স্বাধীনতাও ইংরেজদের ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যেরত্নারাই অর্জিত হবে। রবীন্দ্রনাথ তখন বয়সে তরুণ। তিনি ওই বয়সেই ইংল্যান্ড গমন করেন এবং ইংরেজদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নীতিবোধের সঙ্গে পরিচিত হন। সে সময় তিনিও ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন।
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন
১. তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস ।
২. অবশেষে দেখেছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।
৩. এই সভ্যতা জাত বিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। ৪. এই রকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না ।
২ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তর:
ব্যাখ্যেয় অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ প্রবন্ধ ‘সভ্যতার সংকট’ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বাস্তব থেকে অর্জিত ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা প্রাবন্ধিকের মনোজগতে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো- – এখানে তা-ই ব্যক্ত। ইংরেজদের আগমন ও শাসন পরিচালনার কারণে ভারতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্রমপ্রসার ঘটে। বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে উন্নত জীবনবোধের পরিচয়ও এ সময় ভারতীয়রা লাভ করে।
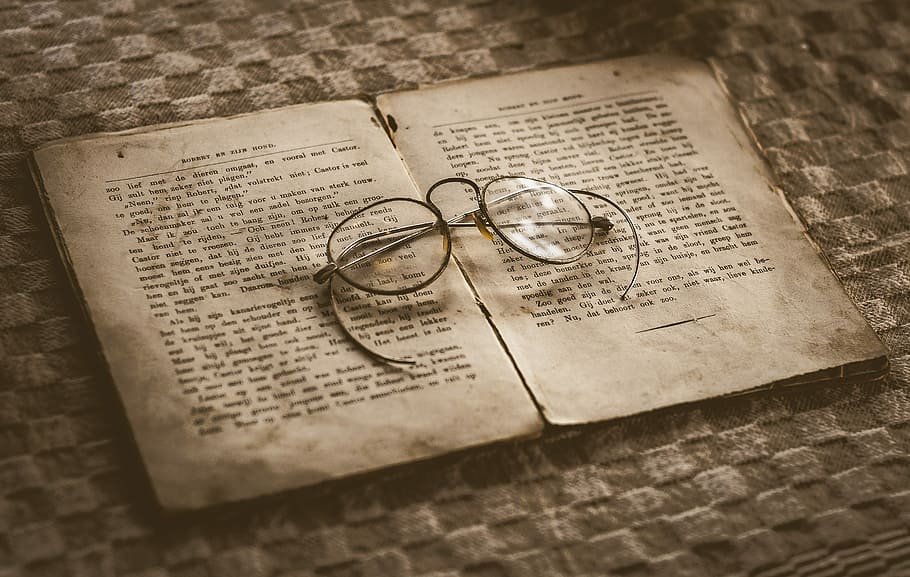
ইংরেজ কথিত ‘সিভিলিজেশন’ অনুসরণের নামে এদেশীয় শিক্ষিতদের জীবনাচরণেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ইংরেজরা পূজনীয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মনেও ইংরেজদের সম্পর্কে বাল্যকালে একটা মোহ জন্মে। কারণ ওই সময় তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন, তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পরিবেশও তাঁকে প্রভাবিত করে। কিন্তু যৌবনে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার সাহিত্য পরিত্যাগ করে যখন বাস্তবধর্মী সৃষ্টিতে মন দেন তখন তাঁর মোহভঙ্গ হতে থাকে।
জমিদারির কাজে গিয়ে পলীগ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করার পর তিনি অনুভব করেন শাসক ইংরেজদের সভ্যতা বা মানবতার বুলির আড়ালে মানুষ শোষণের কুচিন্তা ক্রিয়াশীল। উলিখিত বাক্যে সভ্যতাদর্শী ইংরেজদের এই হীন মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।
মূলপাঠ
ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে।
এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম, উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলন্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলায় ইংলন্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, এক দল ইংরেজ সেই বিপদ্গ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন।
যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয়নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানব হিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল।
সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্ত-শাসনচালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে।
কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়েরত্নারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না।
ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই – ইংরেজশাসনেরমারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দন্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র।
পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা- অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে।
এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এন্ড্রুজের নাম করতে পারি; তার মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃষ্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তার নির্ভীক মহত্ত্ব আরো জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে।
তার কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষ বয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তার স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে।
আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকল প্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না ।
এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি?
ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনেরমারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে।
আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি – পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ!
কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়-যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহত্মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।
শব্দার্থ ও টীকা
জগদ্দল— পৃথিবী দলন করে এমন; এমন গুরুভার যে নড়ানো যায় না।
অহিফেন বিষে — আফিমের বিষে।
এন্ড্রুজ – প্রকৃতনাম চার্লজ ফ্রিজার এন্ড্রুজ। জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ। ইংরজ মিশনারী, অধ্যাপক, মানবদরদী এন্ড্রুজ ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আসেন। কিছুদিন দিলির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আশ্রমবিদ্যালয়ে যোগদান করেন।
নীরন্ধ্র— রন্ধ্র বা ছিদ্র নেই এমন, ফাঁকহীন, চারিদিক রুদ্ধ এমন। অকিঞ্চনতা— নিঃস্ব অবস্থা, সামান্যতা।
পূর্বদিগন্ত— ‘পূর্বদিগন্ত’ বলতে পাশ্চাত্যের বিপরীত অর্থাৎ প্রাচ্য দেশকে বুঝানো হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে সাধারণত পশ্চিমের দেশ বলা হয় । অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
অর্থ: অধমেরপারা যে বিস্তৃত হয়, এক সময়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। সে ভদ্রবেশ ধারণ করে এবং তার প্রতিপক্ষকে জয় করে নেয়। তারপর সে সমূলে ধ্বংস হয়।
বস্তুসংক্ষেপ
রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা করেছেন। ইংরেজদের শাসন ভারতবাসীর উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে বলে প্রবন্ধকার মন্তব্য করেছেন। চীন দেশের মানুষকে নির্জীব করে রাখা, জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন জাপানকে প্রশ্রয় প্রদান ইত্যাদি ইংরেজের পক্ষপাতমূলক সাম্রাজ্যবাদী নীতি রবীন্দ্রনাথকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।
তারা ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়ে শাসন কার্য পরিচালনায় ব্যস্ত। এই আত্মবিচ্ছেদ মূলত সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি। যদিও ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষকে প্রায় নিঃস্ব করেছে নির্দয় শোষণের মাধ্যমে, তবুও দু-একজন ইংরেজ আছেন ব্যক্তি হিসেবে যাঁদের শ্রদ্ধা করতেই হয়। এঁরা শিক্ষা বিস্তার ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রুজ এদের একজন।
রবীন্দ্রনাথের কাছে এদের মহত্ত্বের মূল্য অপরিসীম। ব্যক্তি-ইংরেজদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কারণে তিনি জীবনের প্রান্তিকে ইংরেজদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। কেননা, পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্থি-মজ্জায় তিনি আবিষ্কার করেছেন মানবপীড়নের মহামারী। তবে এই মানবপীড়ক ইংরেজদের একদিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতেই হবে। কিন্তু তারা ভারতকে হয়তো হীনবীর্য করেই যাবে।
জীবনের সূচনাকালে যে ইংরেজদের উদারতা, জ্ঞান ও মানবতাবোধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অগাধ আস্থা জন্মেছিলো, শেষ জীবনে ওই বিশ্বাস তিনি স্থাপন করলেন প্রাচ্যের মানুষের উপর। মানুষই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়স্থল এবং তাই তাঁর উক্তি: ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।’

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. ইংরেজদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শৈশবে গড়ে ওঠা শ্রদ্ধাবোধ তাঁর শেষ জীবনে কোন কারণে বিপর্যন্ত হয়ে পড়ে তা লিখুন।
২. ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তা উলেখ করুন।
৩. জীবনের প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত কোথায় স্থাপন করেছিলেন তা লিখুন।
৩ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তর
আশি বছর বেঁচেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মৃত্যুর বছর (১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে) রচিত ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে সুদীর্ঘ জীবৎকালে অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যে বিশ্বাস পরিবর্তন করেছেন তার উলেখ আছে। প্রথম জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। ইংল্যান্ড সফর ও ইংরেজি শিক্ষার কারণেও এই মোহ গাঢ়তর হয়।
ইংরেজ জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি অনুরাগ এবং তাদের উদার মানবতাবাদী বক্তব্যের জন্যেই মূলত এই মোহের সৃষ্টি। কিন্তু বহির্বিশ্বে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিগ্রহণ এবং ভারতে ‘ল এন্ড অর্ডার’ রক্ষার নামে ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ কার্যকর করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই অবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি।
তবে এ মানুষ পশ্চিমের ইংরেজ শাসকেরা নয়, এরা পূর্বদিগন্তের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষ। প্রাচ্যের এই মানুষই সভ্যতার সংকটকালে পরিত্রাণকর্তার ভূমিকায় কুটির থেকে এগিয়ে আসবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। এ কারণে প্রথম জীবনের মোহ পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে ‘পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের’ প্রত্যাশায় প্রাচ্যের মানুষের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন
১. ইংরেজকে একদা মানব হিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি।
২. পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।
৩. মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।
১ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তর:
আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ ‘সভ্যতার সংকট’ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম জীবনে ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার কারণে এখানে প্রবন্ধকারের উত্তর-জীবনের খেদোক্তি প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিশ্বব্যাপী এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলে তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি এই জাতির অনুরাগ দেখেছেন।
বাল্যকালে লেখাপড়া করার জন্যে ইংল্যান্ড গিয়ে তিনি ইংরেজদের মানবতাবাদী বক্তব্য শ্রবণ করেন। ইংরেজি সাহিত্য পাঠের ফলেও তিনি মুগ্ধ হন। এ সব কারণে তিনি ইংরেজ জাতির প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর একটি অংশ এটাও বিশ্বাস করতো যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভ ইংরেজদের ইচ্ছা বা আনুকূল্য ছাড়া সম্ভব নয়। ‘সভ্যতার সঙ্কট’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সব বিবৃত করে এর অষ্টম অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত খেদোক্তিটি প্রকাশ করেছেন।
কারণ জীবন অতিবাহিত করে সময় অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ করেন পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক ইংরেজদের সভ্যতা বিনাশী ও মনুষ্যত্বের পরিপন্থী ভূমিকা। ভারতেও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার ইংরেজদের ঘৃণ্য রীতি অনুসরণ করতে দেখে উদ্ধৃত বক্তব্যটি প্রদান করেন।
রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন
১। ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি মূলত রবীন্দ্রনাথের আত্মসমালোচনার দলিল’- – আলোচনা করুন।
২। ‘ইংরেজ জাতি ও তার ঔদার্যের প্রতি জীবনের প্রান্তিকে এসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছিলেন। ‘ — ‘সভ্যতার – সংকট’ প্রবন্ধ অবলম্বনে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. ‘মানুষই ছিলো রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়স্থল।’ — আলোচনা করুন।
৪. ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্যবোধের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।
২ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তর
‘সভ্যতার সংকট’ রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রান্তিকে লিখিত শেষ রচনাগুলোর অন্যতম। এখানে তাঁর আত্ম-উন্মোচনের এক করুণ আলেখ্য রচিত হয়েছে। শৈশব থেকে গড়ে ওঠা কিছু বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে ভেঙ্গে ফেলেছেন বলেই এই আত্ম-উন্মোচন খানিকটা করুণ ও মর্মস্পর্শী। তবে তা কোনভাবেই দ্বন্দ্ব-পীড়িত নয়। এই প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ফ্যাসিবাদী ইউরোপের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে সময় ও সমকালীন ঘটনাবলীর অভিঘাণ ছিলো বড় নির্মম। সেই নির্মমতা দীর্ঘদিনে গড়ে তোলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভিত, তার ঐতিহ্যবাহী মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহ বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সদর্প পদক্ষেপে এগিয়ে আসছিলো। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত আঘাত তাতে বিস্ফোরক মাত্রা সংযোজন করে। এ সময় ইংল্যান্ড বা ইংরেজদের ভূমিকা ছিলো আগ্রাসী শক্তির পক্ষে।
রবীন্দ্রনাথ এতে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ, এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ তার ব্যক্তিজীবনের যে পূর্বাপর আলেখ্য তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যায়, শৈশবে তিনি ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট ছিলেন। এর সঙ্গত কারণ এই যে, ইংরেজ শাসিত ভারত সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারায় অতিদ্রুত আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যায়।
তিনি বলেছেন, ইংরেজ জাতির সম্প্রসারণের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালি তথা উপমহাদেশীয় জীবনের বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কিত। একটি মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয় ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে। বার্কের বাগ্মিতা, মেকলের বৈদগ্ধ্য, শেকস্পীয়ারের নাট্যদক্ষতা, বায়রনের স্বাধীনতাপ্রিয়তা সর্বোপরি ইংরেজদের রাজনৈতিক ঔদার্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটে।
এ-সময় অনেক বাঙালির গভীর বিশ্বাস গড়ে উঠেছিলো যে, ইংরেজদের ঔদার্যে অথবা দাক্ষিণ্যে বিজিত জাতি স্বাধীনতা অর্জন করবে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এর অনুকূলবর্তী। তরুণ বয়সে ইংল্যান্ড গিয়ে পার্লামেন্টারিয়ান জন্ ব্রাইটের বক্তব্য শ্রবণ করে তিনি ইংরেজদের হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও জাতিগত অসংকীর্ণতা দেখে মোহাবিষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথ যে পারিবারিক পরিএণ্ডলে মানুষ হয়েছিলেন, সেখানেও ইংরেজদের উচ্চাসন দান করা হয়েছিলো।
ঠাকুর পরিবারে ওই কালের পরিবর্তিত ধর্মমত, লোকব্যবহার ও ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসন অনুসৃত হয়। এই বাস্তব প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠা এবং ইংরেজদের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি। তখনো তিনি সাহিত্যরচনায় অনেকটা কল্পনাবিলাসী। জমিদারী দেখাশোনার কাজে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশেষভাবে লক্ষ করেন ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিদারুণ হৃদয়বিদারক দারিদ্র্য।
ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানহীন জনগণের পশুর ন্যায় বেঁচে থাকা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করে। তিনি আবিষ্কার করেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে ‘বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।’ আর তখনই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সভ্যতা বা ঔদার্যেরত্নারা নয়, যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ তার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে চলেছে।
জাপান যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা করে উন্নত হতে পারে, ইংরেজরা সেই বিজ্ঞানের যথাযথ বিস্তার ভারতবর্ষে ঘটায়নি। বহুজাতিক রাশিয়াতে জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মৌলিকচাহিদা পূরণ করা হয়। অথচ, ইংরেজ বহুজাতিক ভারতে ‘ল এন্ড অর্ডার’ রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ও জাতি-বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছে। এটা মূলত ইংরেজদের ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ নীতির অংশ। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের
ঔপনিবেশিক নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। কারণ —

১.ইংরেজের কথিত সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর ভারতবর্ষের বুকে চাপিয়ে দেয়া, যে-কারণে ভারত নিশ্চল।
২. চৈনিকদের মতো প্রাচীন সভ্য জাতিকে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা।
৩. জাপানের চীন আক্রমণকালে ওই দস্যুবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়া।
৪. স্পেনের গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানো।
এইসব ঘটনার ফলে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজের সভ্যশাসনের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ শৈশবে গড়ে উঠোলো তা বিপর্যন্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের এই সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকটের কারণ সন্ধান ও শনাক্ত করেন। বর্তমান বিশ্বে সাম্রজ্যবাদের চরিত্রের খানিকটা রকমফের হলেও মৌল পরিবর্তন ঘটেনি।