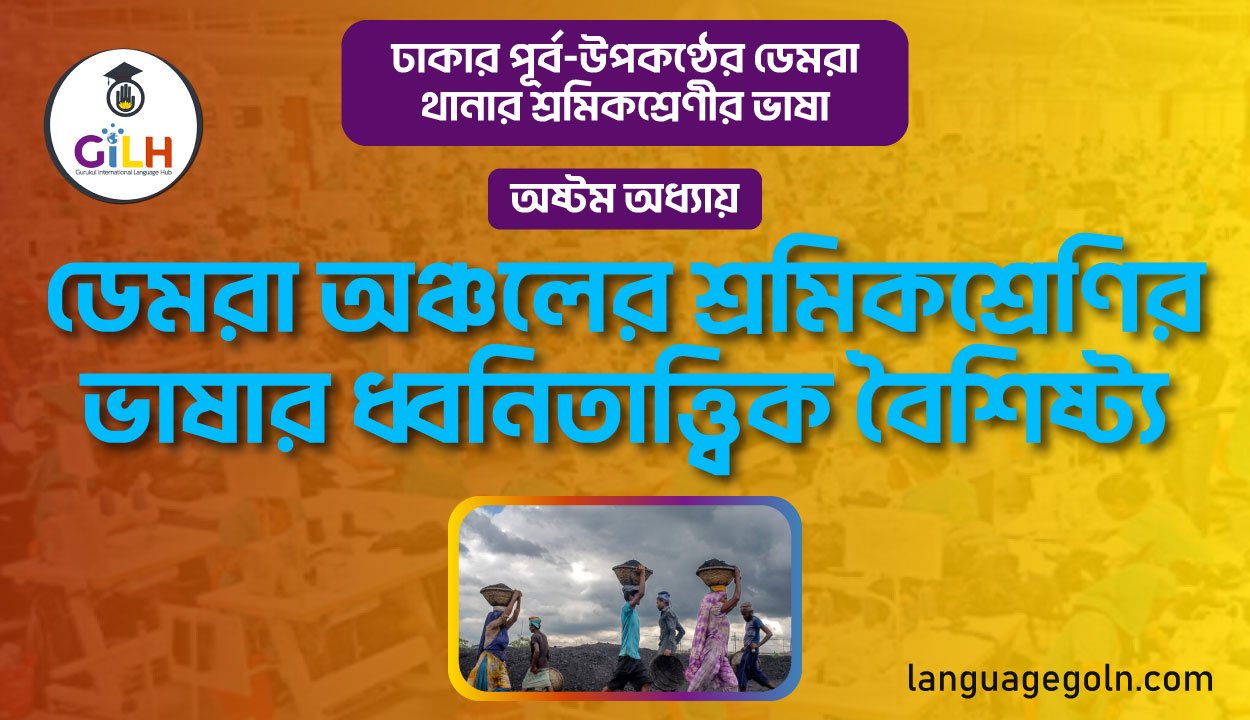আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণির ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
ডেমরা অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণির ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
স্বরধ্বনি : প্রমিত বাংলার ন্যায় ডেমরার আঞ্চলিক ভাষায়ও সাতটি স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়। ই=i, এ=e, এ্যা=ঙ্ক, আ=a, অ=1, ও=0, উ=u|
উচ্চ মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি / এ / /e/ ডেমরা অঞ্চলের ভাষায় নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি / এ্যা//c/ রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন: খেল>খ্যান khel khel, cr
প্রমিত বাংলার স্বরধ্বনির আনুনাসিকতা এ অঞ্চলের ভাষায় দেখা যায় না। কখনো কখনো নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিও লোপ হয় না।
যেমন: পাঁচ> পাছ (pach)
চাঁদ চান (can)
কাঁধ কান্দ (kanda)

ডেমরা অঞ্চলে বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা এলাকার শ্রমিক বেশি। তাই এ অঞ্চলের ভাষায় কখনো কখনো স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঐ এলাকার ধ্বনির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ দেখা যায়।
প্রমিত
আঞ্চলিক
যেমন আলপিন
আলফিইন (alphiin)
‘ফি’ উচ্চারণে ই স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ হয়েছে। রূপমূলের আদা অবস্থানের ‘আল’ স্বরের উচ্চারণ হ্রস্বতম কিন্তু
পরবর্তী ধ্বনি থেকে
উচ্চারণ দীর্ঘ হয়েছে।
আম
আআম (lam)
/আ/ উচ্চারণ দীর্ঘ হয়েছে।
Q. বাংলা ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জন সংযুক্ত আদি নিম্ন অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি /অ/ // এ অঞ্চলের ভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত
/ও/// কারান্ত উচ্চারিত হয়।
শব্দের আদ্যক্ষরে নিম্ন অর্থ বিবৃত /অ/ ধ্বনি পরবর্তী উচ্চ সংবৃত /ই/ ধ্বনির প্রভাবে উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংস্কৃত /ও/
ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চ-মধ্য অর্থ সংস্কৃত /ও/ উচ্চারণ করার সময় চোয়ালসহ মুখের হা অর্ধ সংবৃত অবস্থায় থাকে। আর ওষ্ঠদ্বয় প্রায় পুরো গোলাকার রূপ ধারণ করে।
যেমন করে >কোইরা অ>ও (kore koira
উদাহরণে উচ্চ সংবৃত /ই/ স্বরের আগম ঘটেছে এবং উচ্চস্বর উচ্চ-মধ্য অর্থ সংবৃত / এ/ নিম্ন বিবৃত / আ / -এ
পরিণত হয়েছে।
করব> কোরমু ক>কো (karb> kormu
ডেমরার ভাষায় নিম্ন অর্ধ বিবৃত্ত /অ/-/-/কারের উচ্চারণ অনেকটা সংবৃত, অর্থাৎ উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত /ও/// কাররূপে উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন-অসুখ ওশুক (ofuk), কদু> কোদু (kadu) অ>ও হয়েছে।
শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের শুরুতে নিম্ন অর্থ বিবৃত /অ/// ধ্বনি কখনো কখনো নিম্ন বিবৃত /আ//a/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন-
नवा> नापा (lomba>lamba), অলস আইলশা (olajailja), অমাবশ্যা> আমাবোশ্যা
(omabofæ amabofæe)

१. শব্দের আদি অক্ষরস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ // ধ্বনি কখনো পশ্চাৎ সংবৃত্ত /উ/ /u/ রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন : আদ্যস্বর নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ ও অন্ত্যস্বর নিম্ন বিবৃত / আ / থাকলে কখনো কখনো আদ্য স্বরধ্বনি উচ্চ সংস্কৃত /উ/ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন ডগা>ভুগা (daga duga) এখানে অটি (১) হয়েছে।
শব্দ মধ্যস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/ // ধ্বনি উচ্চ সংবৃত /উ/ //হতে দেখা যায়।
বাসন> বাসুন (bajan bajan), এমন এমুন ( emon emun)
শব্দের অন্তস্থিত নিম্ন অর্ধ বিবৃত /অ/// অনেক সময় উচ্চ সংস্কৃত // // হয়।
দুঃখ দুকখু (duhkh dukkhu), ছোট>ছুডু (chora chudu)।
b. রূপমূলস্থিত উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত / এ/ /e/ ধ্বনি কখনো নিম্ন অর্ধ বিবৃত্ত /অ/ / /, নিম্ন বিবৃত / আ /a/ নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত এ /e/ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-
এখন অহন (ekhan shon), এতগুলি অতগুলান (etaguli otgulan), এখানে এ> ( 20 ) হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বস্বর /এ/-র পর ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় আদিস্বর / এ / /অ/রূপে উচ্চারিত হয়েছে।
আদ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংস্কৃত / এ / – ধ্বনি হলে এবং পরবর্তীতে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে পূর্ববর্তী মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি / এ / ধ্বনি নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত / এ্যা / ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন:
পেট>প্যাট (pa[>prt()
এ>এ্যা (e> in) হয়েছে।
মেঘ >ম্যাগ (megh>meg)

আদিস্বর মধ্য অর্ধসংবৃত সম্মুখ / এ-ধ্বনি এবং অন্ত্যস্বর উচ্চ পশ্চাৎ গোলাকৃতি উচ্চ সংস্কৃত /উ/- ধ্বনি হলে আদিস্বর নিম্ন বিবৃত /আ/ স্বরধ্বনি হয়। যথা :
খেজুর খাজুর (khejur khajur ) এ> আ হয়েছে।
রূপমূলে ব্যবহৃত আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ সংবৃত / ও / // ধ্বনি কখনো কখনো উচ্চ সংস্কৃত /উ/ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যথা- বোতাম > বুতাম (botambutam), ভোর>বুর (bhor bur), ছোট>ছুডু (choto>chudu), তোমার> তুমার (tomar tumar ), চোর>চুর (cor > cur ), এক্ষেত্রে ও>উ (ou) হয়েছে।
উচ্চ সংবৃত /উ/ /u/-কারের উচ্চারণ অনেকটা বিবৃত্ত উচ্চ-মধ্য অর্থ সংবৃত /ও/ /0/-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন-জুতা>জোতা (juta-jota), বুঝেছ > বোচছত (bujhech bacchat)।
১০. ডেমরা অঞ্চলের উপভাষাতে অপিনিহিতি ব্যবহার দেখা যায়। এ অঞ্চলে ব্যবহৃত অপিনিহিতির বৈশিষ্ট্যগুলো হল:
ক. স্পষ্ট স্বরাগম লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে শব্দের স্বরাগমে দ্বিত্বতার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন খাইট্যা
(khaitta) (খেটে), লাইত্যা (laitta) (লাথি দেওয়া), বাইট্যা (baitte) (ভাগ করে
দেওয়া), গুইট্যা (guittee) (ঘুটে দেওয়া)।
খ. বিভক্তি লোপ পেয়েও অপিনিহিতি হয়ে থাকে। যেমন বাড়িতে > বাইত (bait), গাড়িতে > গারিত (garit)। এখানে / এ / /e/ লোপ পেয়েছে।
গ. নাসিক্যধ্বনির বিকল্পে অপিনিহিতি ব্যবহৃত হয়। যেমন কেঁদে > কাইন্দা, রাঁধা > রাইন্দা।
ঘ. ‘র’ এবং ‘ল’ বাঞ্জন বর্ণ দুটির সঙ্গে ‘আ’ থাকলে এবং ‘র’ এবং ‘ল’এর পূর্বে ‘স্থ’ বসে। যেমন কাল > কাইল, চার > চাইর, চালতা > চাইলতা।
ড. নাম শব্দের বিকৃতিতে অপিনিহিতির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রশিদ > রইশ্যা, মুজিবর >
মইজ্যা, রনি > রইন্যা, তকি > তইক্যা।
চ. অপিনিহিতি শব্দে দ্বৈতস্বরের গঠন নিয়মিত। তবে কিছুকিছু শব্দে দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় এককের স্বর সংকোচন দেখা দেয়, ফলে তার উচ্চারণ একক স্বরের পর্যায়ে পড়ে। যেমন হোউরি > হোরি / hóri/, কইগো > কো’গো /kágo/.
ছ. বাক্য শব্দে অপিনিহিতি দেখা যায়। যেমন কোথা থেকে > কইতো, কি জন্য > কি ল্যাগি। এক্ষেত্রে প্রলম্বিত বা দীর্ঘ / ই / উচ্চারিত হয়।
যেমন-নাচ>লাচ (nac>lac), লম্বাম্বা ( lomba namba), লাল > নাল (lal>nal) (রঙ), পাওনা (larjal >nanal), লেপ> নেপ (lep nep)
শব্দের শুরুতে /র/ /r/-কারের আগম ও লোপ এ অঞ্চলে শিশুদের ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন- রস>অশ (rof>2), রাস্তা> আস্তা (rata afta), রান>লান (ran > lan)