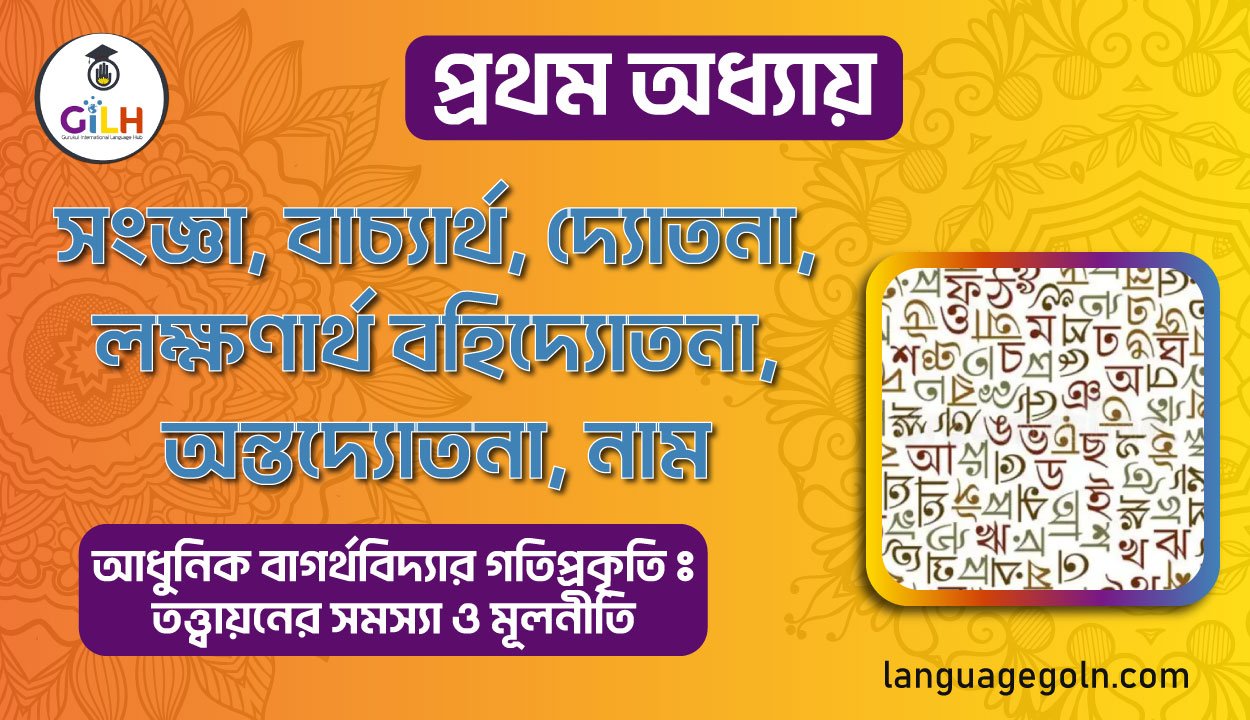আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-সংজ্ঞা, বাচ্যার্থ, দ্যোতনা, লক্ষণার্থ, বহিদ্যোতনা, অন্তদ্যোতনা নাম
সংজ্ঞা, বাচ্যার্থ, দ্যোতনা, লক্ষণার্থ, বহিদ্যোতনা, অন্তদ্যোতনা নাম
সংজ্ঞা, বাচ্যার্থে, দ্যোতনা, লক্ষণার্থ, বহিদ্যোতনা, অন্তদ্যোতনা, নাম এগুলো বাগর্থবিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত পদ । এগুলো অনেক সময় একে অপরকে অধিক্রমন ও অপসারণ করে ব্যবহাত হয় বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে । তাই পদগুলোর সাথে সম্পর্কিত ধারণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । নীচে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ।
সংজ্ঞা : সংজ্ঞার মানে হলো যা দিয়ে চেনা যায় বা জানা যায়। যার সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সংজ্ঞা থেকে আমরা তার পরিচয় পাবো এবং তাকে সনাক্ত করতে পারবো। এজন্য কোন শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণার সংজ্ঞা দিতে হলে শব্দটির সমনাম বা সমঅর্থবিশিষ্ট শব্দসমষ্টি উল্লেখ করতে হয়।

যেমন ত্রিভুজ -এর সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি – তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র বা ত্রিভুজ হলো তিনটি সরলরেখা বেঙ্কিত সমতলক্ষেত্র । লক্ষ্যণীয়, সংজ্ঞা পদটি দ্ব্যর্থক। এটি বাক্যের বিষেয়ও বোঝায় (প্রথম উদাহরণ), আবার সমগ্র বাক্যও বোঝায় (দ্বিতীয় উদাহরণ) ।
এই দ্ব্যর্থকতার নিরসন হতে পারে যদি আমরা প্রথমটিকে সংজ্ঞা ও দ্বিতীয়টিকে সংজ্ঞা বাকা হিসাবে চিহ্নিত করি । সংজ্ঞাবাক্যের তিনটি অংশ উদ্দেশ্য, বিধেয় ও সংযোজক ( definiendum, definiens & copula)। যেমন :
উদ্দেশ্য
সংযোজক
বিধেয়
ত্রিভুজ
triangle
হলো
তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র a three-sided plane figure
যুক্তিবিদ্যার সংযোজককে =Df এই চিহ্ন দ্বারা সূচিত করা হয়। ফলে সংজ্ঞাবাক্যের রূপটি দাঁড়ায় :
ত্রিভুজ = Df তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র
triangle = Df a three-sided plane figure
সংজ্ঞাকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে সংজ্ঞার শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। রমাপ্রসাদ দাস (১৯৯৫ : ১৩৭-১৪৮) নয় ধরনের সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো :
(ক) জাতিবিভেদকটিও সংজ্ঞা: এখানে জাতিধর্ম ও বিভেদক উল্লেখ করা হয়। যথা : মানুষ =Df বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী
(খ) প্রয়োগঘটিত সংজ্ঞা এখানে পদটির প্রয়োগ দেখানো হয়। যেমন অস্তিত্ব -এর সংজ্ঞা :
ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে = Df এমন একটা বস্তু আছে যাতে সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তি, পরমকরুণা, অসীমতা প্রভৃতি বর্তমান।
(গ) কারণিক সংজ্ঞা : এখানে কোন কিছুর কারণ উল্লেখ করা হয়। যথা :
স্বপ্ন হলো অবচেতন মনের চিন্তাভাবনা ।
ঘ) প্রতিবেদক সংজ্ঞা আমরা যেসব সংজ্ঞা সাধারণত উল্লেখ করি সেগুলি প্রতিবেদক সংজ্ঞা । এ সংজ্ঞা সাধারণত অভিধান বা বর্ণনামূলক গ্রন্থ থেকে আমরা সংগ্রহ করি। যেমন আলোচ্য সংজ্ঞাটি আমরা রমাপ্রসাদের বই থেকে সংগ্রহ করেছি। কাজেই এটি প্রতিবেদক সংজ্ঞা ।
(ঙ) প্রবর্তক সংজ্ঞা : কোন পদ কি অর্থে ব্যবহৃত হবে তা যখন প্রস্তাব বা উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে প্রবর্তক সংজ্ঞা বলে । গবেষনামূলক তাত্ত্বিক আলোচনায় হামেশাই এ ধরনের সংজ্ঞার সাক্ষাত মিলে ।
(চ) সার সংজ্ঞা : যে সংজ্ঞার কোন বস্তুর সার ( essence) উল্লেখ করা হয় তাকে বলে সার সংজ্ঞা। যেমন :
মানুষের মন হলো আকাশের রঙের মতো যা ক্ষণে ক্ষণে বদলায় ।
(ছ) বাচ্যার্থঘটিত সংজ্ঞা এখানে পদটির বাচ্যার্থ উল্লেখ করা হয়। যেমন : মানুষ বলতে বোঝায় রাম রহিম, যদু, বদু এরকম পদার্থ ।
(জ) প্রণোদক সংজ্ঞা যখন কোন পদের জ্ঞানীয় অর্থ পরিবর্তন করে নতুনভাবে তার সংজ্ঞা দেয়া হয় তখন তাকে প্রণোদক সংজ্ঞা বলে। যেমন সংস্কৃতি শব্দের মূল অর্থ গান বাজনা ইত্যাদি শিল্পকলা, কিন্তু বর্তমানে এটি মার্জিত আচরণ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এখন সংস্কৃতিবান বললে শিল্পকলার সাথে যুক্ত লোকের গুণকে বোঝায় না, বোঝায় মার্জিত ভদ্রলোকের গুণকে।
(ঝ) দৃষ্টান্ত প্রদর্শক সংজ্ঞা: এক্ষেত্রে নিছক ভাষায় সংজ্ঞায়িত না করে সংজ্ঞেয় প্রত্যয়ের কোন দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি আরর্ষন করা হয়। যেমন, আকাশ-এর সংজ্ঞা দিতে আমি শূন্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারি ।
আনাতোল রাপোপোর্ট (১৯৭৭ : ১৮) আরো এক ধরনের সংজ্ঞার কথা বলেন, তা হলো কার্যমূলক সংজ্ঞা ।

কাৰ্যমূলক সংজ্ঞায় কোন বিষয়ের কার্য বর্ণনা করা হয়। যেমন হিসাবযন্ত্রের সংজ্ঞা দেয়া হয় এভাবে যে যন্ত্র হিসাব করতে পারদর্শী তা-ই হিসাবযন্ত্র। শাস্ত্রজ্ঞরা ধর্মের সংজ্ঞায় বলেন: যা (মানুষকে) ধারণ করে তা-ই ধর্ম (উল্লেখ্য, ধর্ম শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ধাতু থেকে যার অর্থ ধারণ) ।
প্রথাগতভাবে ব্যকরণের যে সংজ্ঞা দেয়া হয় তাও কি কাৰ্যমূলক নয় ? ব্যাকরণের সংজ্ঞায় বলা হয় যে শাস্ত্র আমাদের ভাষার নিয়ম কানুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর সঠিক ব্যবহারের জ্ঞান প্রদান করে তাকে ব্যাকরণ বলে।
এগুলোর সাথে আমরা আরো এক প্রকার সংজ্ঞা যোগ করতে পারি, তা হলো বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। এ সংজ্ঞায় কোন পদনির্দেশিত বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ দেয়া হয় (জ্যাকসন ১৯৮৮ : ৬১)।
যেমন বলা যায় লবন হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড বা
Salt – Df NaCl
তবে এর সীমাবদ্ধতা হলো এভাবে কিছু কিছু মূর্ত বছর সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হলেও কোন বিমূর্ত বার সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয় ।
বাচ্যার্থ : কোন শব্দ যে যে বছর বেলায় প্রযোজ্য তার প্রত্যেকটি হলো শব্দটির বাচ্যার্থ। যেমন মানুষ এর বাচ্যার্থ হলো রিপন, দুলাল, রমা, তমা, পল, পিটার প্রমুখ। দার্শনিক এর বাচ্যার্থ হলো শঙ্কর, রামানুজ, সক্রেটিস, প্লেটো, মিল, হিউম, রাসেল প্রমূখ । আমরা নির্দেশনের আলোচনায় দেখেছি নির্দেশিত হলো নির্দেশী প্রকাশ কর্তৃক চিহ্নিত জাগতিক পদার্থ। কাজেই বাচ্যার্থ নির্দেশিতের সমার্থক। রমাপ্রসাদের মতে, বাচ্যার্থ হলো
ব্যক্তি বা বিশেষ, জাতি বা শ্রেণী নয়। যেমন পার্কির বাচ্যার্থ হতে পারে এই পাখিটি, ঐ পাখিটি বা সেই পাখিটি, কিন্তু কাক, কোকিল, শালিক নয় (কারণ এগুলো পাখির শ্রেণী) । তেমনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বাচ্যার্থ হলো শেখ হাসিনা নামক বিশেষ ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কর্ণধার।
বিনয় বর্মনের বাচ্যার্থ হলো বিনয় বর্মন নামের সেই লোক যে এখন এই অভিসম্পর্কটি লিখছে। সব শব্দের বাচ্যার্থে নেই বা সব শব্দের বাচ্যার্থ স্পষ্ট নয়। যেমন ভূত পরশপাথর, মৃতসঞ্জীবনী এদের বাচ্যার্থ কি হবে তা বোঝা কষ্টকর । বিভিন্ন শব্দের মধ্যে স্বকীয় নাম ও নির্দিষ্ট বর্ণনার বাচ্যার্থ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট।
আমাদের উদাহরণে বিনয় বর্ষন স্বকীয় নাম ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নির্দিষ্ট বর্ণনা । জন লিয়ন্স (1977 206) বাচ্যার্থ বলতে শব্দ ও বস্তুর সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ প্রকাশনকে বুঝিয়েছেন এবং আমরা যাকে বাচ্যার্থ বলছি তিনি তাকে বলেছেন denotatum ( বহুবচন denotata ) ।
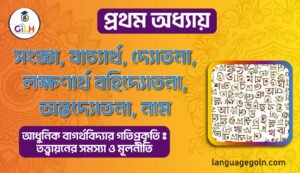
দ্যোতনা :
আমরা অর্থের অর্থ আলোচনায় লীচের সপ্তপ্রকারে দ্যোতিত অর্থের সামান্য আভাস পেয়েছি । এখানে সমস্যাটি আমরা পুনরুস্থাপন করবো। কোন শব্দের দ্যোতনা হলো অনুষঙ্গসূত্রে শব্দটি যেসব ধর্ম বোঝায় সেসব ধর্ম । এটি শব্দটির কেন্দ্রীয় বা মূল অর্থের অতিরিক্ত অংশ।
যেমন রাজাকার ও দালাল শব্দের মূল অর্থ যথাক্রমে স্বেচ্ছাসেবক ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী, কিছু রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তবতায় এগুলো এখন বাংলাদেশে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই কেউ আর রাজাকার বা দালাল হতে চায় না। ম্যাকিয়াভেলি বলেছিলেন, রাজা হবে যুগপৎ শৃগাল ও সিংহ। এখানে শৃগাল এর দ্যোতনা হলো কূটবুদ্ধি ও সিংহ এর দ্যোতনা হলো বিক্রম।
স্পষ্টতই শব্দের দ্যোতনা ব্যক্তিভেদে, গোষ্ঠীভেদে বা সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয়। যেমন গোমাংস শব্দটি শুনলে একজন মুসলমানের জিভে লালা ঝরবে কিন্তু একজন হিন্দু জিভ কাটবে। একইভাবে শুয়োরের মাংস খাওয়ার কথা শুনলে একজন খৃষ্টান হয়তো আবেগাপ্লুত হয়ে বলবে আহা ! অন্যদিকে একজন মুসলমান – ঘৃণাভরে বলবে আসতাকফেরুন্না ! আগুনে যার ঘরবাড়ি পুড়েছে তার কাছে আগুনের দ্যোতনা যেমন, যে – কারো ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে তার কাছে তেমন নয়।
আবার যে আগুন দিয়ে মড়া পোড়ায় তার কাছে এর দ্যোতনা এক রকম, যে আগুনে মাংস পুড়িয়ে কাবাব বানায় তার কাছে এক রকম এবং যে আগুন দিয়ে খেলা দেখায় তার কাছে আরেক রকম। কারো কাছে আগুন উষ্ণতার প্রতীক, আবার কারো কাছে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক ।
সাধারণ ভাষার প্রায় সব শব্দেরই কমবেশি দ্যোতনা আছে। কেবল পারিভাষিক শব্দের দ্যোতনা নেই, কেননা এর তা থাকতে নেই। রমাপ্রসাদ দাস (১৯৯৫: ১০৫-১১৫) শব্দের দ্যোতনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন – চিত্রার্থ কাব্যার্থ ও আবেগার্থ ।
কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টি শ্রোতার মনে যে চিত্র বা ছবি ফুটিয়ে তোলে তাই হলো চিত্রার্থ । যেমন তিতা শব্দটি শুনলে কারো মনে নিমগাছেরর ছবি এবং মিষ্টি শব্দটি শুনলে ময়রার দোকানের ছবি ভেসে উঠতে পারে। কবিতার চিত্রকল্পও চিত্রার্থ। যেমন :
আমার পূর্ব বাংলা এক গুচ্ছ নি অন্ধকারের তমাল অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিরা সন্ধ্যার উন্মেষের মতো কালো কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি
এই কাব্যাংশটি শুনে অন্ধকার, তমাল গাছ, ঘনপাতা, সন্ধ্যা, সরোবর, কালোমেঘ প্রভৃতির সম্মিলনে এক মাধুর্যময় ছবি পাঠকের মনে ভেসে উঠতে পারে ।
কাব্যার্থ হলো কবিতার রসাস্বাদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ। এটি একান্তভাবেই কাব্যগুণ, যেটি কোন কাব্যের বাক্যান্তরিত গদ্য থেকে পাওয়া যায় না। যেমন :
আজিকে প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর কেমনে পশিল প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে গুহার আঁধারে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ। এই পদ্যটিকে যদি আমরা গদ্যে রূপ দেই তাহলে এমন হবে : আজ সকালে সূর্যের আলো কিভাবে প্রাণের ভিতরে পৌঁছালো, সকাল বেলার পাখির গান কিভাবে গুহার অন্ধকারে পৌঁছালো, এতদিন পরে কেন যেন প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ।
কিন্তু এই গদ্যাংশের মধ্যে কি সেই কাব্যের রস পাওয়া গেল ? অপ্রসাদ গুপ্ত তার কাব্য জিজ্ঞাসা গ্রন্থে কাব্যরস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বলেন যে কাব্যের আস্বাদ তখনই হয় যখন ধুনি কাব্যপ্রেমিক চিত্তে আনন্দময় সম্বিতের ধারায় রসে পরিণত হয় ।
কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, “Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility.” বতঃ যার মধ্যে শুভ্রশান্ত সৌম্যকান্ত আবেগের অপার উচ্ছ্বাস নেই কবিই হোক পাঠকই হোক, সে কোনদিন রসের নাগাল পায় না। কাব্যরস তাই সুলভ নয় এবং সেই অর্থে সরস কাব্যও বিরল।
গুপ্ত (১৯৭৩ : ২৭) বলেন, “মনে যতো ভাব উদগত হয়, তাই যদি কাব্য হতো, তবে আজ বাংলাদেশের যে সব হিন্দু মুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানের উপর হিন্দুর ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হতো।”
আবেগার্থ হলো কোন শব্দকে ঘিরে অনুকূল বা প্রতিকূল অনুভবের উদ্ভাসন বা অনুরঞ্জান । এটি আমাদের পূর্বালোচিত আনুভূতিক অর্থের (নীচের সপ্তপ্রকারের চতুর্থটি সমতুল্য। কাউকে যদি বলা হয় তোমার মনে জিলাপীর প্যাঁচ তাহলে মিষ্টান্ন দ্রব্যের উপমা সত্ত্বেও সে নাখোশ হয় কারণ বাক্যটির অর্থ আবেগাত্মকভাবে কুটিলতার সাথে সম্পৃক্ত।
একইভাবে কোন মেয়েকে মাল বললে সে অপমান বোধ করতে পারে কারণ শব্দটি বক্তার মনের অশালীন আবেগ থেকে উদ্ভুত। অনেক সমাজে এরকম রীতিই আছে যে মেয়েদের সাথে কথা বলতে হবে নরম সুরে মিঠাবোলে এমন শব্দ প্রয়োগে যা ইতিবাচক আবেগার্থ প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে জন ই ডনোভ্যানের একটি মজার কবিতা আছে Semantics শিরোনামে ।
Call a woman a kitten, but never a cat
You can call her a mouse, cannot call her a rat Call a woman a chicken, but never a hen
Or you surely will not be her caller again.
You can call her a duck, cannot call her a goose You can call her a deer, but never a moose
You can call her a lamb, but never a sheep economic she lives, but you can’t call her cheap.
You can say she’s a vision, can’t say she’s a sight And no woman is skinny, she’s slender and slight If she should burn you up, say she sets you afire And you’ll always be welcome, you tricky old liar. ”
দ্যোতনা কেবল ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, এটি এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । হায়াকাওয়া (১৯৪৯ : ৩৭- ১৩৮) লক্ষ্য করেন যে দ্যোতনাপূর্ণ ভাষা আবেগসঞ্চারক, তাই এটি সূক্ষ ও শক্তিশালী। যারা এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করেন হায়াকাওয়া তাদের রসিকতা করে বলেন বাকপ্রতারক, কারণ তারা শ্রোতাকে আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে বাস্তববোধ থেকে দুরে সরিয়ে নেন ।
তিনি বলেন, “বাকপ্রতারকের সঙ্গীতময় শুনিতে সাপুড়ের বাঁশির সুরে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো আমরা দুলে উঠি ।” (Like snakes under the influence of a snake charmer’s flute, we are swayed by the musical phrases of the verbal hypnotist.)
লক্ষণার্থ : যে ধর্মসমটি থাকার দরুণ কোন বস্তুতে কোন শব্দ প্রযোজ্য হয় তাকে বলে ঐ শব্দটির লক্ষণার্থ । যেমন মানুষ এর লক্ষণার্থ হল প্রাণিত ও বুদ্ধিবৃত্তি, কারণ এ দুটি গুণ থাকার কারণে কোন কিছুকে আমরা মানুষ বলে গন্য করি । লক্ষণার্থ ও বাচ্যার্থের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে প্রথমটি হলো সংখ্যা পরিমাপ, – দ্বিতীয়টি হলো গুণপরিমাপ।
দুটি শ্রেণীবাচক শব্দ যে শ্রেণী বোঝায় সে শ্রেণী দুটির মধ্যে যদি অন্তর্ভুক্তির সম্বন্ধ থাকে তাহলে শব্দদুটির লক্ষণার্থ ও বাচ্যার্থ তুলনা করে যা পাওয়া যায় তা একটা নিয়মের আকারে ব্যক্ত করা যায় ( রমাপ্রসাদ দাস ১৯৯৫ : ১৫)
যে শব্দটির লক্ষণার্থ অধিকতর তার বাচ্যার্থ অপেক্ষাকৃত কম যে শব্দটির বাচ্যার্থ অধিকতর তার লক্ষণার্থ অপেক্ষকৃত কম যে শব্দটির লক্ষণার্থ অপেক্ষাকৃত কম তার বাচ্যার্থ অধিকতর যে শব্দটির বাচ্যার্থ অপেক্ষাকৃত কম তার লক্ষণার্থ অধিকতর
নীচের উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি পরিস্কার করা যায় :
শব্দ
প্রাণী
মানুষ
সৎ মানুষ
লক্ষণার্থ
প্রাণিত
প্ৰাণিত + বুদ্ধিবৃত্তি
প্ৰাণিত্ব + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা
প্রত্যেক সৎ মানুষ + অসৎ মানুষ + অন্য প্রাণী
প্রত্যেক সৎ মানুষ + অসৎ মানুষ প্রত্যেক সৎ মানুষ
জন লয় (১৯৭৭ : ৫০-৫১) অর্থকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন বর্ণনামূলক, সামাজিক ও প্রকাশমূলক – এবং তিনি বর্ণনামূলক অর্থকে লক্ষ্মণার্থের সাথে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন ।
বহিদ্যোতনা : বহিদ্যোতনা পদটি নির্দেশনাত্মক ও সত্যশর্তমূলক তত্ত্বের প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভূত হয়েছে । বাহ্যিক সংগঠনে এটি সাধারণত বিধেয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। কোন বিধেয়ের বহিদ্যোতনা বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বস্তুর সেটকে যার উপর বিধেয়টি সত্যিকারভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
যেমন ঘর -এর বহিদ্যোতনা হলো পৃথিবীর সমস্ত ঘরের একটি সেট, কুকুর -এর বহিদ্যোতনা হলো প্রথিবীর সমস্ত কুকুরের একটি সেট এবং লাল এর বহিদ্যোতনা হলো পৃথিবীর সমস্ত লাল বস্তুর একটি সেট । কাজেই দেখা যায় আমরা নির্দেশিত ও বাচ্যার্থকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছি তাতে বহিদ্যোতনা তাদের অনুরূপ বলে প্রতিভাত হয়।
তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, বহিদ্যোতনার তাত্ত্বিক গুরুত্ব ভিন্ন। বিষেয়ের বহিদ্যোতনা সময়সাপেক্ষ । যখন আমরা জীবিত -এর বহির্দোতনার কথা বলি তখন আমরা বলার মূহুর্তে যত জীবিত মানুষ আছে তাদের কথা বলি । কাজেই জীবিত শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হলে ভিন্ন ভিন্ন সেটকে বোঝাবে ( Hurdford & Heasley 1993: 81)
অন্তৰ্দ্যোতনা : অন্তদোতনা বহিদ্যোতনার সাথে বৈপরীত্য প্রকাশ করে। জন লিয়ম্স বহিদ্যোতনা ও অন্তদ্যোতনার সংজ্ঞা দেন এভাবে : “একটি পদের বহিদ্যোতনা বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বন্ধকে যার উপর পদটি সঠিকভাবে প্রযোজ্য ।” এবং “একটি পদের অন্তর্দ্যোতনা বলতে বোঝায় সেই সমস্ত আবশ্যিক গুণাবলীর সেটকে যা পদটির প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করে ।”
বিধেয় কলনের সাহায্য নিয়ে (চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা) বলা যায় যে ক যদি কুকুরের সেট হয় এবং খ যদি তার গুণাবলী (কুকুরত্ব) হয় তাহলে :
x ( x = x ∈ ক) “যার মধ্যে কুকুরত্ব আছে তা-ই কুকুর ।”
এটিই হল কুকুরের অন্তর্দ্যোতক সংজ্ঞা । আমরা লক্ষ্য করে থাকবো অন্তর্দ্যোতনা আমাদের পূর্বালোচিত লক্ষণার্থের মতো হলেও এর তাত্ত্বিক গুরুত্ব ভিন্ন। আমরা পরে দেখবো যে ফ্রেজ ও অন্যান্য দার্শনিকগন একটি উক্তির বহিদ্যোতনাকে এর সত্যশর্ত বলে ধরে নিয়েছেন এবং অন্তর্দ্যোতনাকে বলেছেন উক্তিটির অর্থ ।
যে যুক্তিবিদ্যা অন্তৰ্দ্যোতনাকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতর এনে ভাষার অর্থকে রৌপিকভাবে ব্যাখার প্রয়াস পায় তাকে বলে অন্তদ্যোতক যুক্তিবিদ্যা ।
নাম : নাম হলো কোনকিছুকে ডাকার উপায় । ভাষার শব্দসমূহ এক অর্থে কোন না কোন কিছুর নাম । যেমন আবদুল, রমেশ বিশেষ ব্যক্তিসমূহের নাম; গরু, ঘোড়া বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর নাম : দৌড়ানো, সাঁতরানো বিশেষ বিশেষ ধরনের কর্মের নাম ।
ভাষা আয়ত্তকরণের জন্য নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশুরা নামকরণের মাধ্যমে অনেক শব্দ শিখে থাকে। অনেকে মনে করেন যে ভাষার উৎপত্তিই হয়েছে নামকরণের মধ্য দিয়ে । জন লিয়ন্স (১৯৭৭ : ২১৬) মনে করেন নামের রয়েছে দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্য নির্দেশনাত্মক ও সম্বোধনমূলক – । প্রথম ক্ষেত্রে নাম দিয়ে কোন কিছু নির্দেশ করা হয় এবং নামটি বক্তা বা শ্রোতাকে বিশেষ ব্যক্তি বা বর
“By the extension of a term is meant the class of the things to which it is correctly applied.” “The intention of a term is the set of essential properties which determines the applicability of the term “John Lyons (1977), Semantics, pp. 158-159.
অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নাম দিয়ে কাউকে সম্বোধন করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যা ভাষিক যোগাযোগকে ত্বরান্বিত ও সুচারু করে। শুধু ব্যক্তি, বন্ধ বা ধারণা নয়, আমরা নামেরও নামকরণ করতে পারি। যেমন আমরা বিল ক্লিনটন নামটির নাম রাখতে পারি চিনু।
এখন চিনু বললে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন নামক ব্যক্তিকে বোঝাবে না, বোঝাবে বিল ক্লিনটন নামটিকে। স্বকীয় নামের অর্থ আছে কিনা তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। জন লিয়ন্স মনে করেন স্বকীয় নামের কোন অর্থ নেই, তবে তাদের নির্দেশন আছে।
সে হিসাবে জলি, পলি, মলি, কোন অর্থ প্রকাশ করে না, তবে বাস্তব জগতের বিশেষ ব্যক্তি সমূহকে নির্দেশ করে।
শেকসপীয়ার বলেছিলেন, “নামে কিবা আসে যায় ? গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাতে তার গন্ধের তারতম্য হবে না।” বাস্তবে মানুষের কাছে নামের গুরুত্ব সমধিক নাম নিয়ে মানব সমাজে রয়েছে নানা সংস্কার।
ব্যাপারটি বাগর্থবিদ্যার চেয়ে বরং নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয় হলেও এখানে লৌকিক নামকরণ নিয়ে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। অপত্যস্নেহে অন্ধ হয়ে পিতামাতা তাদের কানা ছেলের নাম রাখতে পারেন পদ্মলোচন, কোন অশুভ প্রস্তাব যাতে ছেলেমেয়েকে স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য তারা নাম রাখেন মরণ/মরণী ফালান / ফালানী পড়া ভিতুরাম ইত্যাদি, যাতে আর সন্তান না হয় সেই কামনায়
(বিশেষ করে পূর্বের সমাজে যেখানে কৃত্রিমভাবে জন্মনিরোধের ব্যবস্থা ছিল না কিংবা থাকলেও তাতে জনগনের অনাস্থা ও অবিশ্বাস ছিল) নাম রাখেন আন্নাকালী (আর না কালী মনি, মনি, ইতি ইত্যাদি । কেউ-ই তার সন্তানের দুঃখ চায় না, চায় না কালিমাযুক্ত জীবন। তাই কোন হিন্দু পিতামাতাকে তাদের মেয়ের নাম সীতা ও ছেলের নাম রাবন রাখতে যায় না (এখানে পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্যণীয়)।
সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের কামনায় পিতামাতা তাদের সস্তানের নাম রাখেন রাজা বাদশা সম্রাট। ইতিহাস মানুষকে প্রভাবিত করে। ইতিহাসের কুখ্যাত চরিত্রকে মানুষ এড়িয়ে চলতে চায়, সেজন্য আমাদের দেশের কোন মুসলমান সম্ভবত তার সন্তানের নাম রাখবে না সীমার, মীরজাফর বা এজি। সুন্দর নাম মানুষের মনকে আকর্ষণ করে যেমনভাবে সুন্দর রঙ আকর্ষণ করে মানুষের চোখকে ।
এজন্য সাহিত্যিকরা তাদের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা-নাটকের একটি শিল্পময় সুন্দর নামের জন্য হন্যে হন। একইভাবে চিত্রনির্মাতারা তাদের ছায়াছবির ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাড়িওয়ালারা তাদের ভবনের নামকরণে একটি হৃদয়গ্রাহী শব্দের প্রয়াসী হন।
তবে কিভাবে একটি নাম মনোহারিত্ব অর্জন করে তা এক বিরাট রহস্য। এটিও ভালোভাবে বোঝা যায় না ঠিক ধুনির কোন গুণ থাকার কারণে অথবা ধ্বনিসমূহের কিরকম বিন্যাসে একটি শব্দ শ্রুতিমধুর ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথও এ নিয়ে ভাবিত হয়েছেন এবং মনে হয় কিছুটা বিভ্রান্তও হয়েছেন। নামকে তিনি ইতিহাসের নিরিখে বিচার করতে গিয়ে হয়ে উঠেছেন নষ্টালজি
সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী গিরি নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর । অবন্তী বিদিশা উয়ি ব কৈলাস দেবগিরি, রেবা সিপ্রো বেত্রবতী নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী ।
মেঘদুতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির যথার্থতা বিচার করবেন নামতত্ত্ববিদেরা।